তুজম্বর আলির কবিতা : জসীমউদ্দীনের ১৯৭১
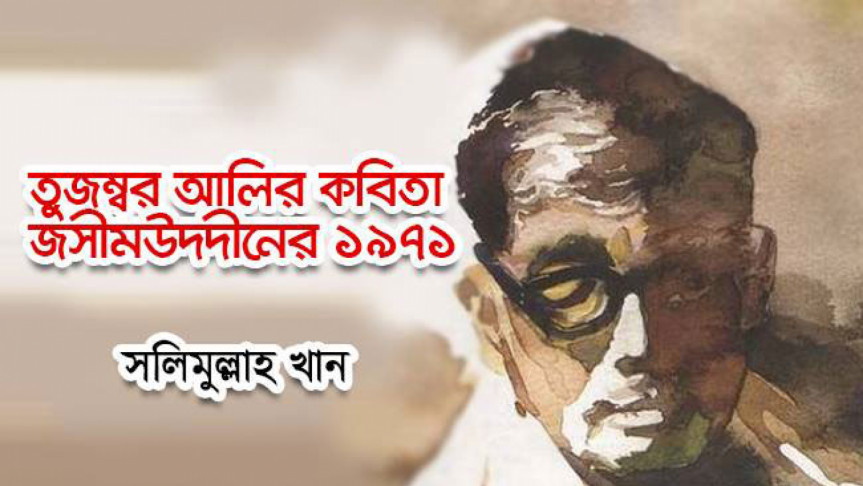
১৯৭১ সালের ছায়া বাংলাদেশের সাহিত্যে কতদূর পর্যন্ত পড়িয়াছে তাহার সঠিক পরিমাপ এখনো পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নাই। তবে একটা জায়গায়—বিশেষ কবিতায়—এই ছায়া না পড়িয়া যায় নাই। উদাহরণস্বরূপ কবি জসীমউদ্দীনের কথা পাড়া যায়। ১৯৭১ সালেও বাঁচিয়া ছিলেন এই মহান কবি। সেই অভিজ্ঞতা সম্বল করিয়া তিনি ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি নাগাদ ‘ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে’ নামধেয় একটি ক্ষীণকায় কবিতা সংকলন ছাপাইয়াছিলেন। সংকলনের গোড়ায়—‘লেখকের কথা’ অংশে—জসীমউদ্দীন জানাইতেছিলেন, ‘তুজম্বর আলি ছদ্মনামে এই কবিতাগুলি রাশিয়া, আমেরিকা ও ভারতে পাঠান হইয়াছিল।’ (উদ্দীন ১৯৭২ : [ছয়])
কবি অধিক জানাইতেছিলেন, ‘আমার মেয়ে হাসনা এর কতকগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া অপর নামে নিউইয়র্কে বিদ্বান সমাজে বেনামিতে পাঠ করাইয়াছে। রাশিয়াতেও কবিতাগুলি সমাদৃত হইয়াছিল। সেখানেও কিছু কিছু লেখা রুশ ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। ভারতে এই লেখাগুলি প্রকাশিত হইলে মুল্করাজ আনন্দ প্রমুখ বহু সাহিত্যক ও কাব্যরসিকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।’ (‘লেখকের কথা’, “ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে,” কবিতাসংগ্রহ ২ : ৩৮৬)
স্বীকার করিতে হইবে, আজও এই কবিতা সংকলনের খবর অনেকেই রাখেন না। যাঁহারা রাখেন তাঁহারাও রাখিতে মনে হয় খানিক বিব্রতই বোধ করেন। জসীমউদ্দীন—বিশারদ অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়কে এই দ্বিতীয়—বিব্রত—দলের দৃষ্টান্তস্বরূপ স্মরণ করা যায়। ১৯৭২ সালে প্রকাশিত এই সংকলন প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন, ‘... উদ্দেশ্যমূলকতার দায় বহন করতে হয়েছে বলে কোথাও কোথাও কবিতার প্রাণশক্তি কিছুটা পীড়িত হয়েছে, তা মানতেই হয়।’ (মুখোপাধ্যায় ২০০৪ : ১৪৪)
সবিনয় নিবেদন করিব, জসীমউদ্দীন -বিশারদের এই নালিশ সর্বাংশে সমর্থন করা যায় না। আমাদের প্রস্তাব, এই ধরনের রায় ঘোষণার আগে জসীমউদ্দীনের ‘কবিতার প্রাণশক্তি’টা কোথায় তাহা নির্দেশ করারও দরকার আছে। এই খণ্ড নিবন্ধে আমরা সেই কোশেসই করিতেছি।
১
১৯৭১ সালের প্রায় তিরিশ বছর আগে—মোতাবেক ১৯৪০ সালে—ভারতবিখ্যাত অধ্যাপক হুমায়ুন কবির দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, কাজী নজরুল ইসলামের মতন জসীমউদ্দীনের সৃজনীপ্রতিভাও অল্পদিনেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। তিনি ধরিয়া লইয়াছিলেন, ‘মানস সংগঠনে’ নজরুল ইসলামের মতন জসীমউদ্দীনেরও কোন রূপান্তর ঘটে নাই। হুমায়ুন কবিরের মতে নজরুল ইসলামের কবিতায় যে বিপ্লবধর্ম তাহা পুরাতন ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন ঘটাইয়াছে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা আর আবেগের নতুন নতুন রাজ্যজয়ে অগ্রসর হইতে পারে নাই।
আর—তাঁহার ধারণা— জসীমউদ্দীনের কাব্যসাধনায় সিদ্ধিটা আসিয়াছিল দেশের ‘গণমানসের অন্তর্নিহিত শক্তি’ হইতে। তবে কিনা তিনিও কল্পনা আর আবেগের নতুন নতুন রাজ্যজয়ে বিশেষ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গের কাজী নজরুল ইসলাম আর পূর্ববাংলার জসীমউদ্দীন—এই দুই বড় কবির কথা মনে করিয়া হুমায়ুন কবির আক্ষেপ করিয়াছিলেন, ‘আজ আত্মকেন্দ্রিক পুনরাবৃত্তির মধ্যেই তাঁদের সাধনা নিবদ্ধ।’ (কবির ১৩৬৫ : ৯১) স্মরণ করা যাইতে পারে হুমায়ুন কবির যখন তাঁহার বহুলপ্রশংসিত ‘বাঙলার কাব্য’ প্রবন্ধটি লিখিতেছিলেন তখনো নজরুল ইসলাম পুরাদস্তুর অসুস্থতার রাহুগ্রাসে পতিত হন নাই।
১৯৪০ সাল হইতে যে দশকের শুরু হয় সেই দশক নাগাদ বাঙ্গালি মুসলমান সমাজের অন্তর্গত কবি ও সাহিত্যসাধকেরা মোটের উপর তিন ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছিলেন। একভাগে ছিলেন সংরক্ষণশীল পক্ষ। সংরক্ষণশীলতার এই দিকপালদের প্রসঙ্গ ধরিয়া হুমায়ুন কবির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ‘তার ঝোঁক অতীতের দিকে, তার ধর্ম্ম প্রচলিত ব্যবস্থার সংরক্ষণ। ইসলামের অন্তর্নিহিত সামাজিক সাম্যকেও তা ব্যাহত করে।’ (কবির ১৩৬৫ : ৯২)
এই পশ্চাৎমুখিতার কারণেই সেদিন বাংলার মুসলমান সমাজ একদিকে যেমন ‘অনিশ্চিত মতি’ অন্যদিকে তেমনি ‘গতিহীন’ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।
দ্বিতীয় ভাগে ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীলরা। এই মাঝি বা দলপতিরা স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড় বাহিয়া পুরাতন বন্দরে ফিরিয়া যাইতে চাহিতেন। আত্মনিবেদন বৃথা জানিয়াও ইঁহারা সমাজমানসের সমস্ত উদ্যম এক অলীক অসম্ভবের পায়ে উৎসর্গ করিয়াছিলেন।
সবশেষে ছিলেন আরেক দল। সংখ্যায় আর শক্তিতে ইঁহারা ছিলেন দুর্বলতম। তবে কিনা একই সঙ্গে ভবিষ্যতের সাধকও ছিলেন ইঁহারাই। সম্ভবত এই দলের কথা মনে রাখিয়াই হুমায়ুন কবির লিখিয়াছিলেন, ‘ভবিষ্যতের অভিযানে আশঙ্কা থাকতে পারে, কিন্তু সম্ভাবনা আরো বেশী, অথচ আজো বাঙালী মুসলমানের যৌবন সে দুঃসাহসিকতায় বিমুখ।’
এই তৃতীয় ভাগের উপরই যতদূর পারেন ইমান আনিয়াছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ হুমায়ুন কবির। তিনি লিখিয়াছিলেন, ‘সমস্ত পৃথিবীতে বর্ত্তমানে যে আলোড়ন, তারও নির্দ্দেশ ভবিষ্যতের দিকে। সেই প্রবাহ যদি বাঙালী মুসলমানকে নূতন সমাজসাধনার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়, তবে মুসলমান সমাজ-সত্তার অন্তর্নিহিত ঐক্য ও উদ্যম দুর্ব্বার হয়ে উঠবে, বাঙলার কাব্যসাধনায়ও নূতন দিগন্ত দেখা দেবে।’
হুমায়ুন কবিরের এই আশা ও আশীর্বাদ সত্য হইতে না হইতে ১৯৭১ সাল আসিয়া গেল। বাংলার কাব্যসাধনায় নতুন দিগন্ত দেখা দিল শামসুর রাহমান ও আল মাহমুদ প্রভৃতি নবীন কবির জন্মের পর।
এই তিন ভাগের মাপে বিচার করিলে দেখা যায় জসীমউদ্দীনের কবিতা একই সাথে দুই ভাগ জুড়িয়া বিরাজ করিতেছিল। আকারের দিক হইতে দেখিলে তাঁহার কবিতাকে সংরক্ষণশীল ভাগে ফেলা যায়। এদিকে বাসনার বিচারে বিভাজন করেন তো তৃতীয় ভাগেও তাঁহাকে গ্রহণ করা চলে।
এই স্ববিরোধ আমলে লইয়াই হুমায়ুন কবির ১৯৪০ সালে লিখিতেছিলেন, ‘... সাম্প্রতিক বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই পশ্চাদমুখী এবং নতুনের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রাচীনপন্থী। সাহিত্যের আঙ্গিক নিয়ে নতুন পরীক্ষা করবার উদ্যম তাঁদের নেই, সমাজব্যবস্থার রূপান্তরে নতুন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভাবনায়ও তাঁদের কল্পনা বিমুখ।’ (কবির ১৩৬৫: ৯১-৯২)
সংক্ষেপে বলিতে কি, ইহাই আমাদের নতুন নাচের ইতিকথা। ইতিকথার পরের কথাও একটা থাকে অবশ্য। যেমন কথায় বলে, মরা হাতির দাম লাখ টাকা। বাংলাদেশের কবিতার পুরাতন আঙ্গিকের চৌহদ্দির মধ্যেও জসীমউদ্দীনের প্রাণশক্তি পুরাপুরি নিঃশেষিত হইয়া যায় নাই। প্রমাণ ১৯৭১ সালের অভিজ্ঞতা লইয়া লেখা এই ক্ষীণকায়—সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় ‘জসীম উদ্দীনের ক্ষুদ্রতম’—কাব্যগ্রন্থেও মিলিতেছে।
২
এই গ্রন্থে ‘বঙ্গ-বন্ধু’ নামে একটি কবিতা আছে, নিচের তারিখ ১৬ মার্চ ১৯৭১। এই কবিতার মাথায় মন্তব্য ঠুকিতে বসিয়া সুনীলবাবু লিখিয়াছেন, ‘এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব এই বঙ্গবন্ধু, যাঁর হুকুমে অচল হয়ে গিয়েছিল শাসকের সকল নিষ্পেষণ যন্ত্র, বাঙালী নরনারী হাসিমুখে বুকে বুলেট পেতে নিয়েছিল শোষক সেনাবাহিনীর।’ কথাটি মোটেও মিথ্যা নহে। খোদ জসীমউদ্দীনের রূপকটা পাওয়া যায় এই ভাষায়:
তোমার হুকুমে তুচ্ছ করিয়া শাসন ত্রাসন ভয়,
আমরা বাঙালী মৃত্যুর পথে চলেছি আনিতে জয়।
(‘বঙ্গ-বন্ধু’, “ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে”, কবিতাসংগ্রহ ২ : ৩৮৮)
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আরো একটি বিজয়ের কথা জসীমউদ্দীন আমাদের শুনাইয়াছেন। ইহা বিশারদ অধ্যাপকদের দৃষ্টিও এড়াইয়া গিয়াছে। যাহা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন করিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু পারেন নাই—কি আশ্চর্য—বঙ্গবন্ধু তাহা পারিয়াছেন। হিন্দু ও মুসলমানকে তিনি ‘প্রেম-বন্ধনে’ মিলাইয়াছেন। মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি জীবনদান করিয়াও যাহা পারেন নাই, তিনি সম্ভব করিয়াছেন তাহা। জসীমউদ্দীন লিখিতেছেন:
এই বাঙলায় শুনেছি আমরা সকল করিয়া ত্যাগ,
সন্ন্যাসী বেশে দেশ-বন্ধুর শান্ত-মধুর ডাক।
শুনেছি আমরা গান্ধীর বাণী—জীবন করিয়া দান,
মিলাতে পারেনি প্রেম-বন্ধনে হিন্দু-মুসলমান
তারা যা পারেনি তুমি তা করেছ, ধর্মে ধর্মে আর,
জাতিতে জাতিতে ভুলিয়াছে ভেদ সন্তান বাঙলার।
(‘বঙ্গ-বন্ধু’, “ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে”, কবিতাসংগ্রহ ২ : ৩৮৮)
১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ তারিখে লিখিত ‘কবির নিবেদন’। তাহার কয়েক পংক্তি এইরকম:
প্লাবনের চেয়ে—মারিভয় চেয়ে শতগুণ ভয়াবহ,
নরঘাতীদের লেলিয়ে দিতেছে ইয়াহিয়া অহরহ
প্রতিদিন এরা নরহত্যার যে কাহিনী এঁকে যায়,
তৈমুরলং নাদির যা দেখে শিহরিত লজ্জায়।
(‘কবির নিবেদন’, ‘ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে’, কবিতাসংগ্রহ ২ : ৩৯০)
পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পোড়ামাটি নীতির একটি গূঢ় প্রতীক ধামরাই রথ আগুন দিয়া ছাই করার কাহিনী। পাকিস্তান রক্ষাকারী সেনাবাহিনীর কীর্তিস্তম্ভস্বরূপ এই ‘ধামরাই রথ’ ভস্মীভূত করিবার কাহিনীটিও লিখিয়া রাখিয়াছেন জসীমউদ্দীন । এই কবিতা হইতে অংশবিশেষ বাছিয়া লওয়া সহজ কর্ম নহে। আমরা ইহার শেষাংশ হইতে মাত্র তিনটি স্তবক উদ্ধার করিব।
বছরে দু-বার বসিত হেথায় রথ-যাত্রার মেলা,
কত যে দোকান পসারী আসিত কত সার্কাস খেলা।
কোথাও গাজীর গানের আসরে খোলের মধুর সুরে,
কত যে বাদশা বাদশাজাদীরা হেথায় যাইত ঘুরে।
শ্রোতাদের মনে জাগায়ে তুলিত কত মহিমার কথা,
কত আদর্শ নীতির ন্যায়ের গাথিয়া সুরের লতা।
পুতুলের মত ছেলেরা মেয়েরা পুতুল লইয়া হাতে,
খুশীর কুসুম ছড়ায়ে চলিত বাপ ভাইদের সাথে।
কোন্ যাদুকর গড়েছিল রথ তুচ্ছ কি কাঠ নিয়া,
কি মায়া তাহাতে মেখে দিয়েছিল নিজ হৃদি নিঙাড়িয়া।
তাহারি মাথায় বছর বছর কোটী কোটী লোক আসি,
রথের সামনে দোলায়ে যাইত প্রীতির প্রদীপ হাসি।
পাকিস্তানের রক্ষাকারীরা পরিয়া নীতির বেশ,
এই রথখানি আগুনে পোড়ায়ে করিল ভস্মশেষ।
শিল্পী হাতের মহা সান্ত¡না যুগের যুগের তরে,
একটি নিমেষে শেষ করে গেল এসে কোন বর্বরে!
(‘ধামরাই রথ’, ‘ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে’, কবিতাসংগ্রহ ২ : ৩৯৭)
কবিতার নিচে তারিখ লেখা আছে ‘ঢাকা, ১৬: মে, ১৯৭১’।
শুদ্ধমাত্র ‘ধামরাই রথ’ নহে—এইরকম গোটা ষোলটি (উৎসর্গপত্র সমেত মোট সতেরটি) কবিতা লইয়া জসীমউদ্দীনের ‘সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে’। ২৭ মার্চ ১৯৭১ তারিখে রচিত ‘কবির নিবেদন’ নামক বিশেষ কবিতাটি মনে হয় ‘ধামরাই রথ’-নামারই সামান্য সংস্করণ।
পদ্মা মেঘনা যমুনা নদীর রূপালী রেখার মাঝে,
আঁকা ছিল ছবি সোনার বাঙলা নানা ফসলের সাজে।
রঙের রেখার বিচিত্র ছবি, দেখে না মিটিত আশ,
ঋতুরা তাহারে নব নব রূপে সাজাইত বার মাস।
যে বাঙলা আজি বক্ষে ধরিয়া দগ্ধ গ্রামের মালা,
রহিয়া রহিয়া শিহরিয়া উঠে উগারি আগুন জ্বালা।
দস্যু সেনারা মারণ-অস্ত্রে বধি ছেলেদের তার,
সোনার বাঙলা বিস্তৃত এক শ্মশান কবরাগার।
(‘কবির নিবেদন’, ‘ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে’, কবিতাসংগ্রহ ২ : ৩৮৯-৩৯০)
১৯৭১ সালে কবি জসীম উদ্দীনের বয়স প্রায় সত্তর ছুঁই ছুঁই। সৃষ্টিক্ষমতাও তাঁহার ততদিনে নিঃসন্দেহে কিছু কমিয়া আসিয়াছে। তবু ধন্য আশা কুহকিনী, দেশ স্বাধীন হইয়াছে আর কবি গাহিতেছেন ভরসার গান।
ঝড়ে যে বা ঘর ভাঙিয়া গিয়াছে আবার গড়িয়া নিব,
ঝড়ের আঁধারে যে দীপ নিভেছে আবার জ্বালায়ে দিব।
ধান কাউনের গমের আখরে মাঠেরে নক্সা করি,
হেলাব দোলাব প্রজাপতি পাখে সাঁঝ উষা রং ধরি।
(‘জাগায়ে তুলির আশা’, “ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে”, কবিতাসংগ্রহ ২ : ৪০৪)
এই সরল পংক্তিনিচয় পড়িবার কত আগেই না হুমায়ুন কবির লিখিয়াছিলেন, ‘আজ আত্মকেন্দ্রিক পুনরাবৃত্তির মধ্যেই তাঁদের সাধনা নিবদ্ধ!’ কাব্যসাধনার প্রকরণে ইহা সত্য হইলেও কাব্যের ‘নিরাকারে’ কোথায় যেন একটা দুর্মর নাদ আছে, যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।
৩
১৯৭০ সালের ১৪ আগস্ট ছিল যুক্ত পাকিস্তানের শেষ স্বাধীনতা দিবস। এই দিনটি উপলক্ষে রচিত মুলতানের উর্দু কবি রিয়াজ আনোয়ারের ‘আজাদির দিনে’ নামক একটি কবিতা তর্জমার ছলে সেদিন জসীমউদ্দীন লিখিয়াছিলেন আপন মনেরই অপ্রকাশিত বেদনা। এই বেদনা পুনরাবৃত্তির অযোগ্য।
আজ আজাদির তেইশ বছর কিবা উন্নতি দেশে
নয়া সড়কের শত তন্তুতে আকাশের কোণ মেশে।
শোষণের আর শাসনের যেন পাতিয়া এই পথ-জাল
অন্তরীক্ষে আছে পাহারায় মহাশয় মহীপাল।
পানটুকু হতে চুনটি খসাবে এমন স্পর্ধা যার,
এই জালে তারে জড়ায়ে পেচায়ে করা হবে সুবিচার।
...
আজি আজাদির এ পুত দিবসে বার বার মনে হয়
এই সুন্দর শ্যাম মনোহরা এ দেশ আমার নয়।
(‘আজাদির দিনে’, “পদ্মানদীর দেশে”, কবিতাসংগ্রহ ২ : ৩০৫-৩০৬)
স্বাধীনতা সংগ্রামের মাহেন্দ্রক্ষণে সংগঠিত ‘লেখক শিবির’ নামের একটি সংগঠন বাংলা একাডেমির সহায়তাক্রমে ‘হে স্বদেশ’ নামে তিন খণ্ড সংকলন প্রকাশ করিয়াছিলেন ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। তাহাদের এক সংকলনে—কবিতা খণ্ডে— জসীমউদ্দীনের কবিতাও দেখা গিয়াছিল একটি। এই ‘একুশের গান’ কবিতাটি ঠিক কখন লেখা হইয়াছিল উল্লেখ করা নাই, তবে অন্তর্গত সাক্ষ্য হইতে অনুমান করি ইহার রচনাকাল ১৯৫২ সালের কাছাকাছি কোন এক সময়েই হইবে। কারণ তখন পাকিস্তানের অন্তঃপাতী পূর্ববঙ্গ প্রদেশের জনসংখ্যা চার কোটি বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। জসীমউদ্দীনও সত্যই লিখিয়াছিলেন: ‘চার কোটী ভাই রক্ত দিয়ে/ পূরাবে এর মনের আশা।’ আমি কবিতাটির দোহাই দিয়া এই নিবন্ধের উপসংহার করিতেছি। ইহার যে রূপক তাহাতেও জসীমউদ্দীনের শক্তি তাজাবোমার মতন বিস্ফোরিত হইতেছে। ‘একুশের গান’ কবিতাটিতে মোট বাইশটি পংক্তি। টুকরা-টাকরা উদ্ধার না করিয়া গোটা কবিতাটিই না হয় এখানে ছাপাইয়া দিই।
আমার এমন মধুর বাঙলা ভাষা
ভায়ের বোনের আদর মাখা
মায়ের বুকের ভালোবাসা।
এই ভাষা রামধনু চড়ে
সোনার স্বপন ছড়ায় ভবে
যুগ যুগান্ত পথটি ধরে
নিত্য তাদের যাওয়া আসা,
পূব বাঙলার নদীর থেকে
এনেছি এর সুর,
শস্য দোলা বাতাস দেছে
কথা সুমধুর,
বজ্র এরে দেছে আলো
ঝাঞ্ঝা এরে দোলদোলালো
পদ্মা হল সর্বনাশা।
বসনে এর রঙ মেখেছি
তাজা বুকের খুনে
বুলেটেরি ধূম্রজালে
ওড়না বিহার বুনে,
এ ভাষারি মান রাখিতে
হয় যদি বা জীবন দিতে
চার কোটী ভাই রক্ত দিয়ে
পূরাবে এর মনের আশা। (জসীমউদ্দিন, হে স্বদেশ ১৯৭২ : ২৫)
বাংলা ভাষার শক্তি সম্বন্ধে জসীম উদ্দীনের রূপক—এক কথায় বলিতে—অতুলনীয়। কবির নির্বন্ধে বাংলা ভাষার সুরটা আসিয়াছে পূর্ব বাংলার নদী হইতে আর এই ভাষার স্বাদটা (‘সুমধুর’ তো স্বাদের কথাই) আসিয়াছে এই দেশের বাতাস হইতে। সে বাতাস শস্যকে দোলা দেয়।
অধিক মন্তব্য করিব না। শুদ্ধ লক্ষ্য করিতে বলিব ‘দেছে’ শব্দের ব্যবহারটি। এ রকম আরো খাঁটি বাংলা শব্দ ছড়াইয়া আছে জসীমউদ্দীনের চরণে চরণে। এহেন শব্দের মধ্যে পাইতেছি আরেকটি—‘এরে’। ভারি দুর্ধর্ষ এক রূপক গড়িয়া উঠিয়াছে ‘ওড়না বিহার’ শব্দের নির্বন্ধে—‘বুলেটেরি ধূম্রজালে ওড়না বিহার বুনে’। এই বাক্যবন্ধটিকে ‘অসাধারণ’ বলিলে খুব কমই বলা হয়। এইরকম আরেকটি রূপক পাইয়াছিলাম ‘ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে’ নাম দেওয়া কবিতা সংকলনের ‘জাগায়ে তুলিব আশা’ কবিতায়।
শোন ক্ষুধাতুর ভাইরা বোনেরা, উড়োজাহাজের সেতু
রচিত হইয়া আসিছে আহার আজি মোদের হেতু।
(কবিতাসংগ্রহ ২/২০১৮ : ৪০৪)
স্বীকার করিব ‘উড়োজাহাজের সেতু’ রূপকটি রসের পরিচয়ে ‘ওড়না বিহার’ বা উড়ন্ত ধর্মাশ্রমকে ছাড়াইয়া যায় নাই। তারপরও তাহাকে কম সুন্দর বলা যায় কি?
৪
সীমান্তের কাছাকাছি গুটিকতক গ্রামের কথা ছাড়িয়া দিলে বলিতে হইবে ১৯৭১ সালের ‘ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে’ গোটা বাংলাদেশই ছিল একটি বৃহৎ বন্দীশিবির। শামসুর রাহমান তখন ঢাকায় ছিলেন। তিনি ঢাকা হইতে কিছু কবিতা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে হাতে কলিকাতা পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাগুলি ফরাশিদেশের কবি পল এলুয়ারের ধরনে লিখিত হইয়াছিল আর ‘মজলুম আদীব’ নামের আড়ালে ছাপা হইয়াছিল কলিকাতা নগরীর মশহুর সাপ্তাহিক ‘দেশ’ পত্রিকায়। আর জসীমউদ্দীনের কবিতাগুলি একই সময়ে পাচার হইয়াছিল ‘তুজম্বর আলি’ ছদ্মনামে। শামসুর রাহমানের রূপক ছিল ‘বন্দী শিবির’ আর জসীমউদ্দীনের লক্ষণার মধ্যে প্রধান ‘গোরস্তান’, ‘শ্মশান’ কিংবা ‘কবরাগার’। আহা, ‘কবরাগার’ শব্দটি যেন খোদ সিগমুন্ড ফ্রয়েডের অভিধান হইতে উঠিয়া আসা! অজ্ঞানের দান। ‘কবর’ ও ‘কারাগার’ কি গাঢ় আলিঙ্গনেই না মিলিয়াছিল ১৯৭১ সালের অবরুদ্ধ বাংলাদেশে! কবরাগারে কবিতার প্রাণশক্তি কোথায় যে থাকে কে জানে! জসীমউদ্দীন লিখিয়াছিলেন:
গোরস্তান যে প্রসারিত হয়ে ঘিরেছে সকল দেশ,
শ্মশান চুল্লি বহ্নি উগারি নাচে উলঙ্গ বেশ।’
(‘কি কহিব আর’, কবিতাসংগ্রহ ২ : ৩৯২)
কিংবা
সারা গাঁওখানি দগ্ধ শ্মশান, দমকা হাওয়ার ঘায়
দীর্ঘ নিশ্বাস আকাশে পাতালে ভস্মে উড়িয়া যায়।
(‘দগ্ধগ্রাম’, কবিতাসংগ্রহ ২ : ৩৯৫)
আর আগেই তো একবার উদ্ধার করিয়াছি:
দস্যু সেনারা মারণ-অস্ত্রে বধি ছেলেদের তার,
সোনার বাঙলা বিস্তৃত এক শ্মশান কবরাগার।
(‘কবির নিবেদন’, ‘ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে’, কবিতাসংগ্রহ ২ : ৩৮৯-৩৯০)
‘ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে’ জসীমউদ্দীন উৎসর্গ করিয়াছিলেন আপনকার পরিচিতজনের একজন অখ্যাত শহিদ মুক্তিযোদ্ধার নামে। ‘শহীদ সামাদ স্মরণে’ নামে প্রণীত উৎসর্গপত্রের কিছুটা পুনরাবৃত্তি করিয়া আমিও আজিকার নিবন্ধের তামাম শোধ করিব।
যাহাদের দুঃখে দিলে প্রাণদান, তাদের কাহিনীগুলি,
কিছু কুড়াইয়া দিলাম আজিকে তোমার হস্তে তুলি।
তোমার সঙ্গে আরো যারা গেছে তাদের স্মরণ পথে
ভাসালেম মোর মানসের ফুল আজিকে কালের স্রোতে।
(‘শহীদ সামাদ স্মরণে’, ‘ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে’, কবিতাসংগ্রহ ২ : ৩৮৪)
দোহাই
১. জসীমউদ্দীন, ভয়াবহ সেই দিনগুলিতে (ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭২); পুনর্মুদ্রণ : জসীমউদ্দীন, কবিতাসংগ্রহ : ২, পুলক চন্দ সম্পাদিত (কলিকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ২০১৮), পৃ. ৩৮৩-৪০২।
২. জসীমউদ্দীন, ‘আজাদির দিনে,’ পদ্মানদীর দেশে, কবিতাসংগ্রহ : ২, ঐ, পৃ. ২৯৩-৩৩৩।
৩. হুমায়ুন কবির, বাঙলার কাব্য, ২য় সংস্করণ (কলিকাতা : চতুরঙ্গ, ১৩৬৫)।
৪. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, জসীমউদ্দীন : কবিমানস ও কাব্যসাধনা, পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪)।
৫. বাংলাদেশ লেখক শিবির সম্পাদিত, হে স্বদেশ : কবিতা (ঢাকা : বাঙলা একাডেমী, ১৯৭২)।






















 সলিমুল্লাহ খান
সলিমুল্লাহ খান


















