আমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্যচর্চার জন্য পড়ালেখায় অমনোযোগ
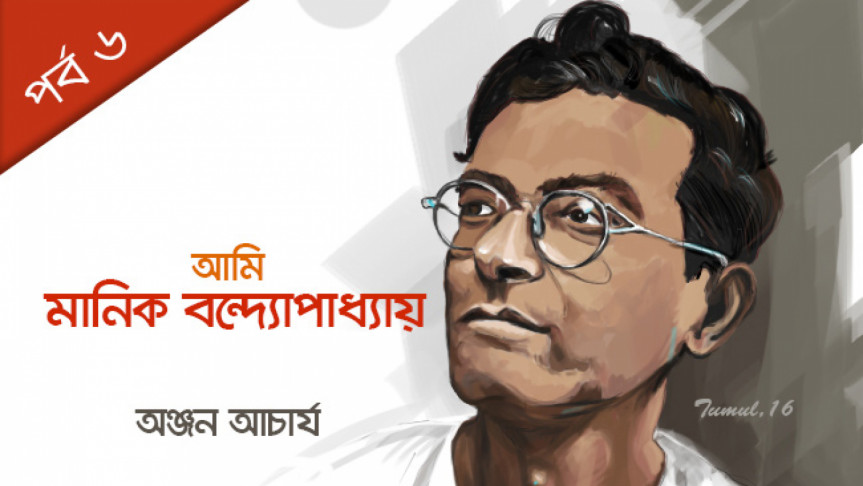
১৩৪৫ বঙ্গাব্দে রমাপতি বসু সম্পাদিত শ্রেষ্ঠ কবিতা নামে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়। সেখানে স্থান পেয়েছিল আমার একটি কবিতা। তবে পাঠকসমাজে আমি তখন গল্প-উপন্যাস লিখে পরিচিতি ও খ্যাতি পেয়ে গেছি ততদিনে। নিজের কবিতার বিষয়ে আমি নিজেও যে খুব বেশি আগ্রহী বা উৎসাহী ছিলাম, তা বলা যায় না। থাকলে, মৃত্যুর পৌনে দুই বছরের মাথায় ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমার পূর্ব-প্রকাশিত ১৬টি প্রবন্ধ জড়ো করে লেখকের কথা নামে যে বইটি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কোনো না কোনো লেখায় কোথাও না কোথাও কবিতার বিষয়ে চিন্তাভাবনা বা অভিজ্ঞতার কথা লেখা থাকত। কিন্তু সে রকম কোনো কিছুর নিদর্শন পাওয়া যায় না।
১৯৭০ সালের মে মাসে (জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ) আমার লেখার একনিষ্ঠ পাঠক কবি যুগান্তর চক্রবর্তী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা শিরোনামে একটি শীর্ণকায় গ্রন্থ প্রকাশ করে। বলে রাখি, একসময় এই যুগান্তরের সঙ্গে বিয়ে হয় আমার ছোট মেয়ে শিপ্রা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। যুগান্তরের ওই বইটিতে ১১ পৃষ্ঠার ‘ভূমিকা’ এবং আট পৃষ্ঠার ‘কবিতা পরিচয়’ সংযোজন করে সেটির সম্পাদনা করে নিজেই। সেই বইটিতে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য প্রকাশ করা হয় আমার : “একটি খাতার ভেতর ১৬ থেকে ২১ বছরের বয়সের মধ্যে রচিত ‘একেবারে তাঁর (মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়) প্রথম জীবনের রচনা’। এই সব কবিতা সমস্ত অর্থেই প্রাথমিক কবিতা’ তা জানতে পারি আমরা। এ খাতার কবিতার সংখ্যা একশর কাছাকাছি এবং লক্ষণীয় বিষয় ছিল যে, এর মধ্য থেকে কোনো কবিতাই মানিক প্রকাশ করেননি। কবিতার আরো দুটি খাতা ছিল মানিকের।”
যুগান্তর জানান, কবিতার খাতার মাত্র চার-পাঁচটি কবিতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবিতকালে প্রকাশিত হয়েছিল; দু-একটি কবিতা তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম প্রকাশিত হয়। জানা যায়, খাতার আর সব কবিতাই এর আগে অপ্রকাশিত।
বইটির ভূমিকা অংশের শুরুতেই যুগান্তর লেখেন, “মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এক যুগেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁর কবিতাগ্রন্থের প্রথম প্রকাশ নিঃসন্দেহেই ঘটনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ঠিক অনুরূপ কোনো ঘটনা এর আগে ঘটেছে বলে মনে পড়ে না। ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু কবিতা তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। এসব কবিতা আমরা এতকাল লক্ষ করিনি। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সম্পর্কে আমাদের এ যাবৎকালের ধারণা, তাঁর কবিতার অপেক্ষা না-রেখেই নির্ণীত হয়েছে। আজ যারা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম পাঠক, তাদের কাছে তাঁর কবিতার প্রথম প্রকাশ তাই প্রায় আবিষ্কারের মতো গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে বাধ্য। এই অর্থে আবিষ্কার যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার পাশ কাটিয়ে আজ তাঁর সাহিত্যের মৌলিক অভিজ্ঞতা পর্যন্ত বুঝে নেওয়া অসম্ভব হবে।”
সেই ভূমিকায় আরো লেখা হয়, মানিকের প্রথম প্রকাশিত কবিতা তাঁর প্রায়-প্রথম গদ্য রচনার সমসাময়িক। রচনাকালের দিক থেকে তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘দিবারাত্রির কাব্য’র তিনটি পৃথক বিভাগের ভূমিকাস্বরূপ মুদ্রিত কবিতা তিনটি, অন্তত প্রকাশকালের দিক থেকে মানিকের প্রথম কবিতার নিদর্শন। এমনকি যুগান্তরের মতে, ‘দিবারাত্রির কাব্য’র এই ভূমিকা-কবিতা প্রমাণ করে যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা তাঁর গদ্যের চেয়েও প্রাচীন; যে অর্থে অনেক লেখক কবিতা লিখে শুরু করেন ঠিক সেই অর্থে নয়, কবিতার মৌলিক অভিজ্ঞতা ছাড়া ‘দিবারাত্রির কাব্য’র মতো প্রথম উপন্যাস লেখা যে কোনো লেখকের পক্ষেই অসম্ভব হতো।
আমার কৈশোর-তারুণ্যের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম খাতার কবিতাগুলো ছাড়া আরো বেশ কিছু কবিতা আমি লিখেছিলাম যার মধ্য থেকে বাছাই করা ৪৫টি কবিতা বইটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাল-তারিখ মিলিয়ে একরকম হিসাব কষে যুগান্তর মোটামুটি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছে যে, ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ কবিতাগুলোর রচনাকাল। যুগান্তর এ কথাও উল্লেখ করে যে, “অন্তর্ভুক্ত লেখাগুলির রচনাকাল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনের শেষ আট-দশ বছর।” তাঁর মূল্যায়ন হলো, “জীবনের শেষ আট-দশ বছরই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতার শ্রেষ্ঠ কাল।” বইটি মোট ৫৮টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে ১৩টি কিশোর জীবনে লেখা, এবং বাকি ৪৫টি পরবর্তী জীবনে রচিত কবিতা। হায়াৎ মামুদ তাঁর ‘মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা : যাপিত জীবন’ প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গটি তুলে ধরেন- “মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখকের কথা, মৃত্যুর পরবর্তী বৎসর ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত, প্রবন্ধসংকলনে লেখা নিয়ে যত কথা বলেছেন সবই গল্প-উপন্যাস নিয়ে। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করি, কবিতা সম্পর্কে- নিজের কাব্যসাধনা বা কবিতাপ্রেম নিয়ে- একটি কথাও বলেননি। অথচ সংখ্যায় যত অল্পই হোক বা রচনাসমূহের মধ্যবর্তী বিরতিকাল যত দূরবর্তীই থাকুক, তিনি আমৃত্যু কবিতা লিখেছেন। যুগান্তর চক্রবর্তী জানিয়েছেন, কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বাসনাও তাঁর ওই তিনটি খাতার পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ আছে। ওই ইচ্ছাটুকু পর্যন্তই; কই, ছাপেননি তো। তিনি যখন খ্যাতির তুঙ্গে, মুদ্রণের কথা ভাবলে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা মোটেই অসম্ভব হতো না। কিন্তু তিনি সে কথা ভাবেননি। বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয় যে, তিনি কবিতা প্রকাশের চিন্তাকে আমল দেননি; যে নিভৃতচারিণী সে নিভৃতেই থাকুক- তাঁর মনের ইচ্ছে যেন এ-রকম। আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি, কবিখ্যাতি তাঁর ইপ্সিত ছিল না।” এ কথাটিকে সমর্থন করতে দেখা যায় যুগান্তরের সেই ভূমিকাতেও- “বিশেষ কোনো লেখকের ভাষাগত অভিজ্ঞতা কেন বিশেষভাবে গদ্য বা কবিতার আশ্রয় নেয়, তা নিশ্চিতভাবে ব্যাখ্যা করা কঠিন। আমরা শুধু সাধারণভাবে বলতে পারি যে, লেখকমাত্রই তাঁর অন্তঃপ্রকৃতির গঠন ও জীবনসম্পর্কিত অভিজ্ঞতার বিশেষ প্রকৃতি অনুযায়ী তাঁর নিজস্ব সাহিত্যভাষা নির্ভুলভাবে খুঁজে নেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নিজের সাহিত্য সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ‘সাধ করলে কবি হয়তো আমি হতেও পারি; কিন্তু ঔপন্যাসিক হওয়াটাই আমার পক্ষে হবে উচিত ও স্বাভাবিক!’ [উপন্যাসের ধারা, লেখকের কথা, ১৯৫৭ সাল] এই উক্তি আমরা বিনাবাক্যে মেনে নিতে বাধ্য, কারণ, একমাত্র মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষেই, তাঁর অমানুষিক আত্মচেতনার প্রমাণস্বরূপ, এমন অব্যর্থ উক্তি সম্ভব, ‘আড়াই বছর বয়স থেকে আমার দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস আমি মোটামুটি জেনেছি।’ [কেন লিখি, ১৯৪৪ সাল; প্রকাশ : লেখকের কথা, ১৯৫৭]
ফিরে আসা যাক আবার ১৯২৯ সালে। সেই বছরের জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ) ‘গল্পগুচ্ছ’ পত্রিকায় ‘শেষ মুহূর্তে’ এবং এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) ‘মানসী ও মর্ম্মবাণী’ পত্রিকায় ‘রকমারি’ নামে দুটি গল্প প্রকাশিত হয় আমার। এদিকে বিচিত্রা পত্রিকার সম্পাদকের তাগিদে আমার গল্প লেখা চলতে থাকে বিরতিহীন। জুন মাসে (আষাঢ় ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) ‘নেকী’ এবং আগস্ট মাসে (ভাদ্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) ‘ব্যথার পূজা’ গল্প দুটি প্রকাশিত হয় বিচিত্রায়। বছরের শেষ দিকে এসে আমি হাত দিই আমার প্রথম উপন্যাস দিবারাত্রির কাব্যের আদি পর্বে। আর এ সময়টায় সাহিত্যচর্চায় মনোযোগী হয়ে পড়ায় স্বাভাবিকভাবে আমার কলেজশিক্ষায় দেখা দেয় অমনোযোগ। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি মাসে (মাঘ ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) বিচিত্রায় ছাপা হয় ‘বৃহত্তর ও মহত্তর’ গল্পের প্রথম কিস্তি। গল্পের বাকি অংশ প্রকাশিত হয় সেই পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় (ফাল্গুন ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। মার্চ মাসে (চৈত্র ১৩৩৬ বঙ্গাব্দ) ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় ছাপা হয় আমার ‘চাপা আগুন’ গল্পটি। এদিকে সাহিত্যচর্চায় বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়ায় কলেজপাঠে দেখা দেয় চরম অনীহা। এ সময় আমার পড়াশোনার খরচ চালাতেন বড়দা সুধাংশুকুমার।
পড়ালেখায় আমার অমনোযোগিতার কথা শুনে চরম রেগে আগুন হয়ে পড়েন তিনি। এমনকি আমার লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ দেওয়াও বন্ধ করে দেন। বড়দার পাঠানো টাকা বন্ধ হয়ে গেলে চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়ি আমি। একপর্যায়ে কলেজ হোস্টেল ছেড়ে গিয়ে উঠি আমহার্স্ট স্ট্রিটের এক মেসে। এভাবেই আর্থিক অসচ্ছলতার মুখোমুখি হই প্রথম। লেখালেখি করে চলার মতো পয়সা রোজগারের লক্ষ্যে তখন আমি পুরোপুরি নিজেকে নিয়োজিত করি সাহিত্যচর্চায়। কেন এমনটা করেছিলাম তার একটি কারণ অবশ্য আছে। আর সেই কারণ আমি প্রকাশ করি বহু বছর পরে আমার এক লেখায়। ১৯৫৭ সালে লেখা আমার ‘উপন্যাসের ধারা’ প্রবন্ধটি শুরু করি এভাবে- “লিখতে শুরু করার আগে শুধু আশা নয়, দৃঢ় প্রতিজ্ঞাও ছিল যে, একদিন আমি লেখক হবো।” এই কথাটির মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি নিতান্ত কোনো ঝোঁকের বশে সাহিত্যজগতে প্রবেশ করিনি আমি। বরং মনের দিক থেকে প্রস্তুতি নিয়েই সাহিত্য চর্চা করতে শুরু করি। এ ছাড়া ১৯৭৬ সালে যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত ‘অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়’ বইটিতেও আমার বেশ কয়েকটি চিঠিপত্র সংকলিত হয়েছে। ২ আগস্ট ১৯৫২ সালে লেখা সেখানকার ২৩ নম্বর চিঠিতে আমি লিখেছিলাম, ‘অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বিএসসি পড়ার সময় আমি সাহিত্য করতে নামি- বাড়ির লোকের সঙ্গে ঝগড়া করে। কারণ, তখন আমি অনুভব করেছিলাম যে সাহিত্যজগতে একটা বড় রকম পরিবর্তন ঘটতে চলেছে, এ রকম সন্ধিক্ষণে সাহিত্য সৃষ্টি করার বদলে অন্য কাজে সময় নষ্ট করা যায় না।’
(চলবে)





















 অঞ্জন আচার্য
অঞ্জন আচার্য

















