আবদুশ শাকুর : জ্ঞানযোগী লেখকের মৃত্যুদিনে
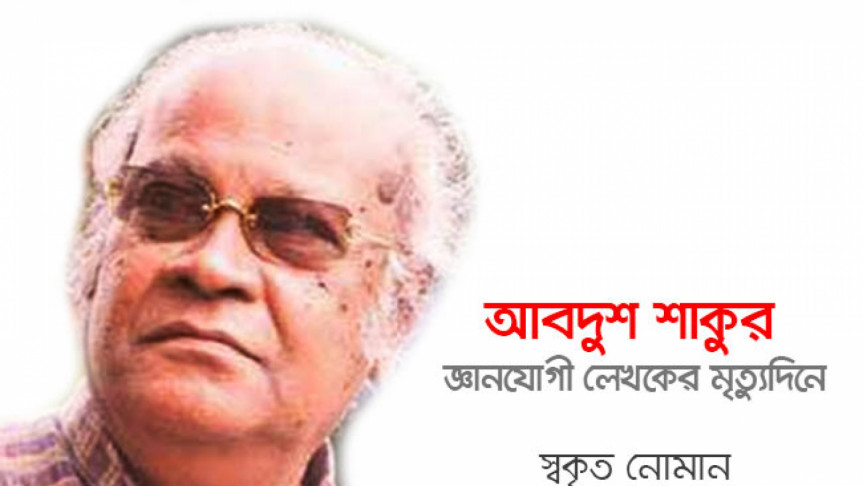
“শোন নোমান, আমার পাঠশালার সহপাঠী ও দীর্ঘজীবনের একান্ত সুহৃদ মাস্টার নোমানের বর্তমান মুমূর্ষু অবস্থার কারণেই বোধ হয় তোমার প্রায় সকল প্রশ্নই আমার কাছে বাল্যবন্ধু নোমানের প্রশ্ন বলেই মনে হয়েছে এবং আমাকে করে তুলেছে একান্তই স্মৃতিবেদনাতুর। বেশি অতীত-আর্ততায় যাপিত জীবনের হাহাকার বেজে উঠতে চায় বেশি―যা সত্যকথনে বিঘ্নও ঘটাতে পারে বেশি। তবে স্মৃতিবেদনা অনেক বিস্মৃতিকেও টেনে আনে। তোমার সঙ্গেকার এই দীর্ঘ গল্পবাজিতে সে উপহারও আমি অনেক পেয়েছি―ফিরে এসেছে আমার চিরতরে হারিয়ে ফেলা অনেক অমূল্য স্মৃতি। ফলে সাক্ষাৎকারটা অনেকাংশেই আমার জীবনের গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে গল্প নেহাত নীরসও নয়। কারণ ক্যারিয়ারটা আমার আগাগোড়াই, যাকে বলে, ‘চেকার্ড’ (chequered)― সাদা বাংলায় নকশিকাঁথা।
জানি আমার কিছু উত্তর রূপ নিয়েছে ভাষ্যের আর অধিকাংশ জবাবই হয়ে উঠেছে বয়ান। তবে বয়ান আমার যাপিত জীবনেরই। ফলে এতে অপ্রাসঙ্গিক কিছুই নেই। তোমার প্রশ্নগুলো ছিল আমার জীবনের স্মৃত ও বিস্মৃত ফাইল এবং ফোল্ডারগুলো খোলার পাসওয়ার্ড বা চাবি। অলস ক্ষণে অন্যমনে নেহাত অহৈতুকী কৌতূহলবশত কেউ আমার মতো অকৃতীর জীবনের গভীর ভিতরটা একনজর দেখতে চাইলে খোলা খাতার এ বয়ানটুকুর বেশি জানার দরকার হবে না তাঁর। আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনের ভেতরমহলটা এভাবে খুলে তুলে ধরার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ জানাই। শুভ নববর্ষ!’
আবদুশ শাকুর
ধানমন্ডি লেকসাইড, ঢাকা, পয়লা জানুয়ারি ২০১২”
গত দশকের শুরুর দিকে সদ্যপ্রয়াত কথাশিল্পী আবদুশ শাকুরের অনবদ্য স্মৃতিকথা ‘কাঁটাতে গোলাপও থাকে’ পাঠের মধ্য দিয়েই মূলত তাঁর লেখার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর রচনার শিল্পগুণ এত বেশি মুগ্ধ করে যে, তাঁকে আরো বেশি করে জানতে সচেষ্ট হই। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর বিচিত্র রচনাবলি পাঠ করতে করতে, তাঁকে জানতে জানতে দশকের শেষের দিকে এসে তাঁর সান্নিধ্য লাভের গৌরব অর্জন করি। প্রস্তাব করি তাঁর একটি আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকার নেওয়ার ব্যাপারে। বেশ কয়েক মাস সময় নিয়ে অবশেষে প্রস্তাবে রাজি হলেন। কাজ শুরু হলো। দীর্ঘদিন ধরে সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ শেষে তিনি আমাকে উপর্যুক্ত পত্রখানা ই-মেইল করে পাঠান। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু এতটাই স্তব্ধ করে দেয়, লেখাটা কী দিয়ে শুরু করব স্থির করতে পারছিলাম না। তাই অবতরণিকা হিসেবে এই পত্রের আশ্রয় নেওয়া।
শক্তিমান কথাশিল্পী আবদুশ শাকুরের আত্মজৈবনিক সাক্ষাৎকারটি যখন নিচ্ছিলাম, সেই সময়ের অভিজ্ঞতার কথা বলি। উর্দু কবি মির্জা গালিবের ‘কাল্লু’ নামে একজন খেদমতগার ছিল। দাস্তান বা গল্প শোনার প্রচণ্ড নেশা ছিল তার। রোজ গল্প না শুনলে রাতে তার ভালো ঘুম হতো না। মির্জা গালিবের কাছ থেকে তো শুনতই, শহরে কোনো দাস্তানগো এলে তাকে ধরে নিয়ে আসতো দাস্তান শোনার জন্য। আবদুশ শাকুরের জীবন-দাস্তান বা জীবনের গল্প শুনতে শুনতে নিজেকে সেই কাল্লুর মতোই মনে হয়েছিল। যে কি না নির্বাক শ্রোতা, গল্প শুনতে শুনতে যে আমুণ্ডু নিমজ্জিত হয়, যে গল্পের ভেতরে জীবন-সঞ্জীবনী খুঁজে পায়।
আবদুশ শাকুর বিষয়ে আমার আগ্রহের প্রধান কারণ তাঁর ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষাশৈলী। তাঁর ভাষার যে ছন্দ, যে স্বাতন্ত্র্য, যে মহাকাব্যিক দ্যোতনা, তা অগ্রসর যেকোনো পাঠককে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করার মতো। এই একটা মাত্র কারণে তাঁর রচনা পাঠে আগ্রহী হয়ে উঠি। এই পাঠের সুবাদেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা। এই ঘনিষ্ঠতা অনেকটা গুরু-শিষ্যের, কিংবা বলা যায় মির্জা গালিব এবং কাল্লুর।
আবদুশ শাকুর ছিলেন প্রজ্ঞানিমগ্ন একজন লেখক। তিনি প্রথমত একজন কথাশিল্পী। গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ও নাটকে শব্দ দিয়ে এমন কারুকাজ করতেন, যা প্রকৃতার্থেই শিল্প হয়ে উঠেছে। স্বস্তা বিনোদনের জন্য, পাঠককে নিছক আনন্দ দেওয়ার জন্য তিনি কখনোই লিখেননি। কথাকে কীভাবে শিল্পে রূপান্তর করা যায়, সেই প্রয়াস ছিল সব সময় তাঁর লেখায়। ভারতের বঙ্গবাসী কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. বিষ্ণু বেরা আবদুশ শাকুর সম্পর্কে তাঁর এক লেখায় লিখেছিলেন : “অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও সূক্ষ্ম রসবোধসম্পন্ন কথাশিল্পী শাকুর তাঁর রচনাসাহিত্যে নিজেকে এবং তাঁর প্রিয় বাংলাদেশ ও পরিবর্তমান বাঙালি সমাজকে বিশশতকের উত্তাল বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে নানা রঙে নানা ভঙ্গিমায় স্থাপন করেছেন। মনন ও অভিজ্ঞতায় এই লেখক প্রকৃত অর্থেই একজন বিশ্বনাগরিক। বাংলাদেশের নাগরিক বৃত্তের উচ্চমহল সম্বন্ধে বিশদ ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তাঁর জীবনপাত্র উছলে উঠে এক স্বতন্ত্র মাধুরীর ছবি ফুটিয়ে তুলেছে তাঁর গল্প-উপন্যাসে, বিশেষত রমণীয় রচনার ছোটগল্পরূপ উপস্থাপনায়। মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা, সংসারের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অসামান্য তাৎপর্যময় করে তোলা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ উপস্থাপনার নির্মোহ দার্শনিকতা তাঁর রচনাকে একান্তই নিজস্ব করে তুলেছে।”
বাংলা ভাষায় বহু শব্দের আবিষ্কারক আবদুশ শাকুর। প্রতিনিয়তই নতুন নতুন শব্দ আবিষ্কার করতেন তিনি। তাঁর লেখায় দেখা যায় অসংখ্য নতুন শব্দের সমারোহ। শব্দ আবিষ্কারের বিস্ময়কর একটা ক্ষমতা ছিল তাঁর। ক্ষমতাটা তৈরি হওয়ার পেছনে নিরন্তর পঠন-পাঠন ও একাধিক ভাষায় দক্ষতার বিষয়টা কাজ করেছে। প্রথম জীবনে তিনি মাদ্রাসায় পড়েছেন বলে আরবি, উর্দু ও পার্সি ভাষাটাকে ভালোভাবে আত্মস্থ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। পরে ইংরেজি সাহিত্যে পড়াশোনা ও অধ্যাপনার সুবাধে এই ভাষাটিকেও রপ্ত করে নেন। পাশাপাশি স্বপ্রচেষ্টায় সংস্কৃত ভাষাটাও কিছুটা আত্মস্থ করতে সক্ষম হন। বহুভাষাবিদ হওয়ার কারণে অনন্য এক সৃজনক্ষমতা তৈরি হয় তাঁর ভেতর। মুখের ভাষার মতো তাঁর গদ্যও বুদ্ধিদীপ্ত, ক্ষিপ্র, কাব্যময়, রঙিন ও ক্ষুরধার হয়ে ওঠে। গদ্যশরীর কতখানি নিখাদ আর শাণিত হতে পারে, তাঁর ভাষা সেটা প্রমাণ করে।
অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ভাষায়, “আজ আমাদের চারপাশে অযত্ন আর অবহেলায় লেখা শিথিল গদ্য ভাষার যে ‘অলীক কুনাট্যরঙ্গ’ মাথা উঁচিয়ে উঠেছে―আবদুশ শাকুরের গদ্য চিরায়ত গদ্যের পক্ষ থেকে তার শক্তিমান প্রতিবাদ... জ্ঞান, মেধা এবং মননের সমবায় তাঁর বৈদগ্ধ্যকে এমন এক পরিশীলিত শ্রী এবং উপভোগ্যতা দিয়েছে যার কাছাকাছি জিনিশ চিরায়ত বাংলাসাহিত্যের ভিতরেই কেবল খুঁজে পাওয়া যাবে।”
ছোটগল্পের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমি ও পশ্চিমবঙ্গের অমিয়ভূষণ―এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার ছোটগল্পের ক্ষেত্রে আবদুশ শাকুরের অবদানকে নির্দেশ করে। তাঁর পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার ‘গল্পসমগ্র’ গ্রন্থটি কীর্তি হিসেবে বাংলা কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার উপাদানে সমৃদ্ধ। ভাষা ও উপজীব্যের দিক দিয়ে অভিনব বলেই তাঁর উপন্যাস ‘ক্রাইসিস’, ‘সংলাপ’ ও ‘উত্তর-দক্ষিণ সংলাপ’ অগ্রসর পাঠকদের কাছে সমাদৃত।
প্রবন্ধসাহিত্যে আবদুশ শাকুর যে সমৃদ্ধি এনেছেন, তা আমাদের প্রবন্ধসাহিত্যের দৈন্যদশাকে অনেকটা ঘুচিয়েছে। প্রবন্ধকে সাধারণত মননশীল সৃষ্টিকর্ম হিসেবে বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তিনি এতটা দক্ষতা ও অভিনবত্বের সঙ্গে লিখেছেন, তাঁর প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধই সৃজনশীলতার পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে বলা চলে। তাঁর প্রবন্ধ মানেই নতুন কিছু, নতুন আস্বাদ, নতুন অভিজ্ঞতা। যে বিষয়টি নিয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেই বিষয়টিকে বিশ্লেষণ করেছেন বৈশ্বিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ একককে বিশ্লেষণ করেছেন সমগ্র দিয়ে। ভাষাগত ঐশ্বর্য, তথ্য, তত্ত্ব ও সৃজনশীলতার গুণে প্রতিটি প্রবন্ধই সুখপাঠ্য হয়ে উঠেছে। জ্ঞানের বিভিন্ন উপাদানকে বিষয়ের সঙ্গে একাঙ্গীকরণে তাঁর দক্ষতা অভিভূত হওয়ার মতো। প্রতিটি প্রবন্ধই বিষয়, ভাষা ও শৈলীর দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মননশীল পাঠকের জন্য যেমন তৃপ্তিদায়ক, তেমনি প্রজ্ঞার উৎকর্ষের সহায়ক। প্রতিটি প্রবন্ধের বিষয়ও অভিনব, বৈচিত্র্যমুখী। তিনি যেসব দুর্লভ ও কঠিন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন, বাংলা সাহিত্যে সেসব দুর্লভই বলা চলে। পাঠেই বোঝা যায়, এমন পরিশ্রমলদ্ধ কাজ একমাত্র জ্ঞানযোগী আবদুশ শাকুরের পক্ষেই সম্ভব।
অন্যদিকে, আবদুশ শাকুর বাংলা ভাষার প্রথম সারির একজন রম্যলেখক। তাঁর পাঁচ শতাধিক পৃষ্ঠার ‘রম্যসমগ্র’ পড়ে উপলব্ধি করা যায়, লেখালেখির এ ধারাটির ক্ষেত্রে কেন তিনি দেশের অগ্রগণ্য লেখক হিসেবে পরিচিত। লেখায় রস সৃষ্টিতে তাঁর যে দক্ষতা, তা তাঁর সমকালীন অন্য কোনো লেখকের ছিল কি না গবেষণার বিষয়। সত্যিকারার্থে আমাদের রম্যসাহিত্য দীর্ঘদিন ধরে একটা তীব্র কাতরতার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। রম্য, অথচ পড়তে গেলে কান্না আসে। কাতরতার এতই তীব্রতা! এই কাতরতার পরিবর্তে তিনি জারিত করলেন শৈল্পিক স্ফুর্তি।
আবদুশ শাকুরের গোলাপবিষয়ক গবেষণামূলক রচনাসমূহ বিশেষত ‘গোলাপসংগ্রহ’ গ্রন্থটি বাংলা ভাষায় একক। শুধু পুষ্পরানী গোলাপ সম্পর্কেই নয়, বইটিতে রয়েছে মৌসুমি, বর্ষজীবী, দ্বিবর্ষজীবী, চিরজীবী ফুলবিষয়ক নানা আলোচনাসহ বাংলাদেশের জাতীয় ফুল ও জাতীয় উদ্ভিদ উদ্যানের ওপর সারগর্ভ পর্যালোচনাও। এ ছাড়া গবেষণামূলক সংগীতলেখক হিসেবে দেশের সংগীত ও সাহিত্যিক সমাজে তিনি অগ্রগণ্য। শুদ্ধসংগীতের স্বর, সুর, কথা, হিন্দুস্তানিসংগীত বনাম কর্ণাটকসংগীত, ধ্বনিমুদ্রণ প্রযুক্তি, ধ্বনিসংস্কৃতি বনাম লিপিসংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে গভীরচারী আলোচনার জন্য তাঁর ‘সংগীত সংগীত’, রাগসংগীতচর্চার সোনালি শতক সম্পর্কিত ‘মহান শ্রোতা’ এবং সার্ধশত বর্ষের দেশাত্মবোধক সংগীত পর্যালোচনা গ্রন্থ ‘বাঙালির মুক্তির গান’ বিশেষজ্ঞমহলে সমাদৃত। এবং তাঁর ‘মহামহিম রবীন্দ্রনাথ’, ‘পরম্পরাহীন রবীন্দ্রনাথ’ এবং ‘রবীন্দ্রনাথকে যতটুকু জানি’ নামক রবীন্দ্র-গবেষণামূলক গ্রন্থগুগুলো বোদ্ধামহলে কবিগুরুর শেষহীন গুরুত্ব অনুধাবনে বিশেষ সহায়ক বলে বিবেচিত।
একজন মানুষ নিরন্তর জ্ঞানচর্চার মধ্য দিয়ে প্রজ্ঞার একটা উচ্চতায় যে পৌঁছতে পারেন, সেই সাক্ষ্য বহন করেছিলেন যশস্বী কথাকার আবদুশ শাকুর। জ্ঞানচর্চার নিবিষ্ট এক ধ্যানী মানুষ ছিলেন তিনি। গতানুগতিকতার জোয়ারে গা না ভাসিয়ে, জনপ্রিয়তার ফাঁদে পা না বাড়িয়ে লেখক হিসেবে একটা স্বতন্ত্র ধারা প্রতিষ্ঠার ঘটনা বাংলাদেশে বিরল। কাজটা বিস্তর কঠিন। আবদুশ শাকুর এমনই এক অনন্য প্রতিভা, যিনি নিজেকে সচেতনভাবে জনপ্রিয়তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখে নিভৃতে সাহিত্যচর্চায় নিরত থেকেছেন নিরলস। ১৯৯৯ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর থেকেই পুরোপুরি লেখালেখিতে মনোনিবেশ করেন। পড়া ও লেখায় তাঁর নিমগ্নতা এতটাই ছিল, প্রতিদিন ১০ ঘণ্টা তো বটেই, কোনো কোনোদিন ১২, এমনকি ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত লেখাপড়ায় মগ্ন থাকতেন। একমাত্র লেখালেখির স্বার্থেই বাসা থেকে তেমন একটা বের হতেন না। প্রতি মঙ্গলবার কেবল মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে যেতেন স্ত্রীর কবর জেয়ারতের উদ্দেশ্যে। তখন প্রায়ই আমাকে ফোন করে বলতেন সেখানে আসতে। বহুদিন স্যারের সঙ্গী হয়েছি। মাঝেমধ্যে বলতেন, ‘চল নোমান, তোমার সঙ্গে আজ সাভার চলে যাই। একটা নৌকা ভাড়া করে বংশী নদীতে ঘুরব।’ বলতেন, কিন্তু যাওয়া হতো না। কবর জিয়ারত শেষে বাসায় ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতেন। প্রতিবারই বলতেন, ‘আজ নয়, আরেকদিন যাব।’ শেষ পর্যন্ত বংশী নদীতে নৌবিহার আর হয়ে উঠল না তাঁর।
সত্যি আবদুশ শাকুর একজন সৌভাগ্যবান লেখক। লেখালেখিতে তিনি সক্রিয় ছিলেন মৃত্যুর আগপর্যন্ত। মৃত্যুর দিন দুপুরেও লেখার জন্য তিনি কম্পিউটারটি ওপেন করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শরীরে কুলাচ্ছিল না বলে বেডরুমে গিয়ে শুয়ে পড়েন। মৃত্যুর দুদিন আগেও তিনি লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনী রচনার কাজটি করছিলেন বেশ কমাস ধরে। বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশের জন্য মোট ছয় খণ্ডে তিনি রবীন্দ্রজীবনী রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। দুই খণ্ড লিখে শেষ করে পাণ্ডুলিপি জমাও দিয়েছেন একাডেমিতে। রবীন্দ্রজীবনের ৩০ বছরের নানা বিষয় এই দুই খণ্ডে আলোচিত হয়েছে। ১৫ জানুয়ারি বইটি বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশের কথা ছিল, হয়ত মুদ্রণবিষয়ক জটিলতার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। স্যারের ইচ্ছে ছিল দুই খণ্ডের জীবনীটি দেখে যাওয়ার। ইচ্ছে পূরণ হলো না। এই কাজে তিনি এতটাই পরিশ্রম করতেন যে ৭৮ বছর বয়সেও কোনো কোনো দিন ১২ কি ১৬ ঘণ্টা লেখার টেবিলে পড়ে থাকতেন। মাঝেমধ্যে মধ্যরাতে ফোন করে জানাতেন, রবীন্দ্রনাথবিষয়ক কোনো নতুন তথ্যটি তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং জীবনীর কোনো অধ্যায়ে সেটা সংযুক্ত করতে চান।
তিন-চার বছর ধরে বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকী, সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ঢাকা ও ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন লিটলম্যাগে প্রচুর লিখছিলেন। মাঝেমধ্যে মৃদু রাগ করে বলতাম, ‘স্যার, এই বয়সে এত লেখার কোনো দরকার আছে? লেখার চেয়ে আপনার বিশ্রাম নেওয়াটা জরুরি।’ স্যার হাসতে হাসতে বলতেন, ‘লেখাটাই তো আমার বিশ্রাম, বাবা! একদিন না লিখলে তো রাতে ঘুম হয় না আমার।’ এই এক আশ্চর্য গুণ তাঁর। লেখালেখির জন্য তাঁর এই পরিমাণ পরিশ্রম ও নিমগ্নতা আমাদের বিস্মিত করে, সেইসঙ্গে অনুপ্রাণিতও করে বৈকি!
শুধু বাংলাদেশে নয়, পশ্চিবঙ্গেও সমান খ্যাতি আবদুশ শাকুরের। কলকাতা থেকে তাঁর বই আগেও বেরিয়েছে। কয়েক বছর ধরে কলকাতার একাধিক প্রকাশনা সংস্থা থেকে তাঁর বিভিন্ন বই প্রকাশিত হচ্ছে। এ বছরও বেশ কিছু বই প্রকাশ হওয়ার কথা রয়েছে। যে বইগুলো বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলোই আবার কলকাতা থেকে প্রকাশিত হতো। এতে স্যারের মধ্যে খানিকটা উচ্ছ্বাস দেখতাম। প্রায়ই বলতেন, ‘বাংলাদেশের পাঠক আমাকে মূল্য দিল না। দেখ, কলকাতার প্রকাশকরা ঠিকই আমার বই গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করছে। ওখানে আমার বইয়ের বিক্রি বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। পশ্চিমঙ্গে আমার বইয়ের বিক্রি বাড়ছে দিন দিন।’
নিজের লেখালেখি সম্পর্কে তিনি এতটাই সতর্ক থাকতেন, প্রতিবছর মেলায় যখন তাঁর বই বের হতো, তখন তিনি প্রুফ দেখানোর জন্য কখনো প্রুফরিডারকে পাণ্ডুলিপি দিতেন না, কষ্ট হলেও নিজেই দেখতেন। পাণ্ডুলিপির সফ্ট কপিও প্রকাশককে হস্তান্তর করতেন না, নিজ দায়িত্বে সরাসরি ট্রেসিং বের করে তারপর প্রকাশকের হাতে তুলে দিতেন। যান্ত্রিক জটিলতার কারণে পাছে কোনো শব্দ ভেঙে যায়, বাক্যের ওলটপালট যদি ঘটে যায়! বইগুলোর মেকআপ দেওয়ার জন্য একজন কম্পিউটার অপারেটরও রেখেছিলেন। আর তাঁর বাসাটি হচ্ছে একটি গ্রন্থাগার। বইগুলো সহজে খুঁজে পেতে নম্বর দিয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার কাজে সহযোগিতা করতেন সঞ্জয় গাইন। এই হচ্ছে আবদুশ শাকুরের বৈশিষ্ট্য।
স্বভাবে কিছুটা অন্তর্মুখী প্রতিভাবান এই লেখক দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে নিয়ে গিয়েছেন। ২০১৩ সালের ১৫ জানুয়ারি সন্ধ্যায় কবি নওশাদ জামিলের ফোনে তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ছুটে যাই তাঁর ধানমণ্ডির বাসায়। স্যার শুয়ে আছেন তাঁর বেডরুমে। কত নিষ্কলুষ তাঁর চেহারা! যেন মৃত্যুকে উপেক্ষা করে গভীর সুসুপ্তিতে নিমগ্ন। তাঁর প্রয়াণে আমাদের শোক অনন্ত, তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি আমাদের অশ্রুত শ্রদ্ধা। বিদায় প্রজ্ঞানিমগ্ন কথাকার আবদুশ শাকুর, বিদায়।





















 স্বকৃত নোমান
স্বকৃত নোমান

















