দহনকথা
তেভাগার শিল্পরূপ
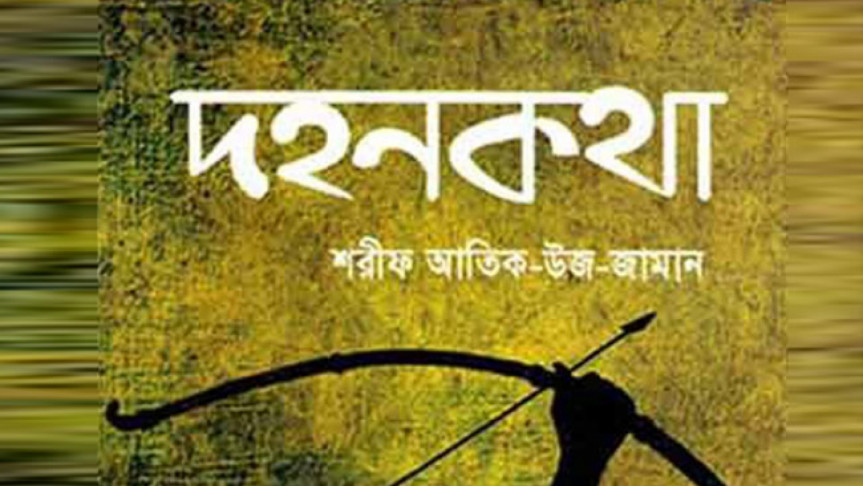
বাংলার কৃষক আন্দোলনের এক উজ্জ্বল অধ্যায়। যেসব এলাকায় তেভাগার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল, নড়াইল জেলা তার মধ্যে অন্যতম। তেভাগা আন্দোলন মোটেও সফল হয়নি, ইতিহাসের কাল বিচারে এ কথা বলা যাবে না। কারণ, ১৯৪৬ সালে শুরু হওয়া এ আন্দোলন যে ইশতেহার রচনা করেছিল, সে কারণে কৃষককে আর শোষণের ওই স্তরে নেওয়া সম্ভব হয়নি। তা ছাড়া তেভাগা, টংক নানকার নাচোলের কৃষক বিদ্রোহ সবই বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের একেকটি সোপান। শরীফ আতিক-উজ-জামান অসম্ভব মেধাবী একজন লেখক, শিল্পী ও ইতিহাসবেত্তা। নড়াইলের মাটিবর্তী এই শিল্প কারিগর তেভাগা নিয়ে মাইলফলক সব কাজ করেছেন।
সম্প্রতি মাটির দায় মেটাতে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের এ শিক্ষক লিখেছেন উপন্যাস ‘দহনকথা’। তেভাগা গণসংগ্রাম নিয়ে এমন উপন্যাস সম্ভবত এটাই প্রথম। ‘চিত্রা নদীর পারে বিশাল হাট। নদীর পার ঘেঁষে রাস্তা। খোয়া উঠে মাঝে মাঝে হাঁ হয়ে আছে। সেই রাস্তার ওপরই হাট। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক, একেবারে ভিক্টোরিয়া কলেজ পর্যন্ত টানা লম্বা রাস্তা। শুরুতেই মেছোহাট, তারপর চাল, মুদি, তরিতরকারি, গুড়, মিষ্টি, জলফক্কর, লুঙ্গি, জামাকাপড়, মাটির বাসন-কোসন, মেয়েদের সস্তা প্রসাধনী, অন্তর্বাস, শোলার তৈরি পুতুল ইত্যাদির বিক্রি চলছে পাশাপাশি পসরা সাজিয়ে। এর মাঝেই বিকট ও বিচিত্র হাঁকডাক করে ফেরিওয়ালারা কেউ দাঁদের মলম, কেউ ইঁদুর-তেলাপোকা মারার বিষ, কেউ যৌন দুর্বলতার ভেষজ ওষুধ, কেউ বা বিছানায় পেচ্ছাব, কিশোরদের স্বপ্ন দোষ ও নানাবিধ জানা-অজানা স্ত্রীরোগ নিরাময়ের তাবিজ কবচ বিক্রি করছে। সব সমস্যার একই তাবিজ। পরিচিতজনের দৃষ্টি এড়িয়ে কেউ কেউ যৌনবর্ধক ওষুধ কিনছে। দ্রুত দাম মিটিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাচ্ছে।’(পৃষ্ঠা-৮)
শরীফ আতিক-উজ-জামানের এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে তেভাগার অঞ্চলগুলো আর্থসামাজিক পরিচয় মেলে। বর্ণনার সারল্য প্রমাণ করে এই অঞ্চলের প্রতিটি বালুকণার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা থেকে কাজটি করেছেন। এই সমাজ কোন সমাজ? মরাচেপড়া এই সমাজের ফাঁকফোকরে জেগে থাকে শুয়োপোকা, শাপ, স্বর্ণবোড়া। রাঘব বোয়াল রাষ্ট্র চায় এ সমাজকে টিকিয়ে রেখে শোষণ করতে। তাদের সহযোগী হয় এসব শুয়োপোকা গোছের মানুষেরা। মেহনতি মানুষের রক্ত শোষণ করে বেঁচে থাকা পুঁজিনির্ভর রাষ্ট্রের পেটোয়া পেটিবুর্জোয়ারা। তাদের সারা বছরের শ্রম শোষণ করে তাদের দাঁদ, প্যাটড়ায় ভরে দেয় সমাজের দেহ। মানুষ বিশ্বাস হারায়। আত্মবিশ্বাস হারানোয় যৌনজীবনে আসে অবিশ্বাস। এমন সমাজসংগ্রাম ছাড়া যে বদলায় না তা তরা জানে না। মাঠে মাঠে সোনালি ধান ঢেউখেলে সেই ধান দেখে কৃষক স্বপ্ন বোনে। ধান উঠলে তার অধিকাংশ চলে যায মহাজনের গোলায়। এর বিরুদ্ধে কথা বরা যাবে না। কারণ এর মালিকরা রাষ্ট্রের পেটোয়া। এই বাস্তবতা যারা বোঝে, তারা তেভাগাকে মুক্তির ইশতেহার হিসেবে মেনে নিয়ে লড়াই-সংগ্রাম শুরু করে।
তেভাগার ডাকে কৃষকরা দলে দলে আসতে থাকে। কৃষকদের অবিসংবাদিত নেতা নূর জালাল সব তদারকি করতে থাকে। ‘আশপাশের সমস্ত গ্রাম দুর্গাপুর, ডুমুরতলা,রতনডাঙ্গা, দলজিৎপুর, বাগবাড়ি, রূপগঞ্জ, বীরগাঁ, বড়েন্দর, গোবরা, মুলিয়া, সীতারামপুর, তুলারামপুর, ইত্যাদি গ্রাম থেকে চাষি কর্মীরা দলে দলে মাঠে জড়ো হতে থাকে। মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বলে দিতে লাগল, এরা যেন একটি ঘোষণার অপেক্ষা করছে।’ (পৃষ্ঠা-২১)। দীর্ঘদিনের শোষণে অতিষ্ঠ কৃষক যে তেভাগার মধ্য দিয়ে মুক্তির ইশতেহার খুঁজেছিল লেখক, তা সুচারুভাবে বর্ণনা করেছেন। এবং এই শান্ত অঞ্চলের শোষিত কৃষক একদিন দধীচির হাড় হয়ে উঠেছিল, ‘হয় ধান নয় প্রাণ’-এর প্রশ্নে কৃষক মেহনতি মানুষ সর্বস্ব নিয়ে মাঠে নেমেছিল। তাদের নেতা নূর জালাল, মোদাচ্ছের, অমল সেনদের নেতৃত্বে। পাকিস্তানি জান্তার অত্যাচারে মাথায় একদিন তারা ধরে ফেলে নূর জালাল অমল সেনদের। ফিরে দাঁড়ায় এক কৃষকের কিশোর ছেলে ছনু, কৃষক ছলেমানের ছেলে সে। সে পাথর ছুড়তে থাকে। এ পাথরকে লেখক যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে মনে হয় একদিকে রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে ছনু পাথর ছুড়তে থাকে। কিন্তু সব রোখা যায় না।
পাকিস্তানি প্রেতাত্মারা পতিত পাথরের ভেতরেই জগদ্দল আকার নেয়। আবার তারা ছোবল মারতে মরিয়া হয়ে ওঠে তবু লেখক হতাশ হন না। তেভাগার নায়ক নূর জালাল যখন পুলিশের গাড়ি থেকেই বলে ওঠেন, ‘কী ভাবিছ? শেষ করে দিবা সব? আমাগের সংগ্রাম, আমাগের লড়াই, সবকিছু? অত সহজ না। তুমরা কিচ্ছু করতি পারবা না। মনে রাখবা মানুষের সংগ্রাম কোনদিন মরে না। তা আগুনির মতো। একবার লাগলি ছড়ায়ে যায়, সব জাগায়। আমাগের সংগ্রামও নেভবে না, ছড়ায়ে যাবে। এক জায়গারতে আরেক জায়গায়, এক পুরুষিরতে আরেক পুরুষি। যাবেই যাবে, কেউ তারে রুখতি পারবে না। মানুষের মুক্তি আসবে, আসবেই।’ (পৃষ্ঠা-১৪৪) ।
তেভাগা যেসব অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল তার একটি লড়াকু অংশ নড়াইল। এ অঞ্চলের সংগ্রামের পটভূমি নিয়ে লেখা উপন্যাসটি তেভাগার শেকড়ের সন্ধানীর যেন ডায়েরি। তেমনি ‘দহনকথা’ নড়াইল অঞ্চলের গণসংগ্রামের শিল্পরূপ বললে অত্যুক্তি হবে না। তবে এটা ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলও। একজন রাজনীতিক গবেষকের কাজটিও তিনি করেছেন সুচারুরূপে। সুপাঠ্য ও বাঙালির গণসংগ্রামের এ দলিল পাঠককে পাঠের আনন্দ দেবে বলে ধারণা করি।
উপন্যাসটিতে দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশ কৃষক আন্দোলন নিয়ে যার উপশিরোনাম ‘নিজ খোলানে ধান তোল’ আর পরের অংশ দেশভাগ সম্পর্কিত যার উপশিরোনাম ‘ভাজ্য-ভাজক-ভাগফল’। এখানে ব্যবহৃত গান-কবিতা-ছড়ার কিছু কিছু সংগৃহীত, কিছু কিছু স্বরচিত। ওই জনপদের মানুষের মাঝে প্রচলিত ও জনপ্রিয় বিষয়গুলো তুলে আনা হয়েছে বস্তুনিষ্ঠতা ও ইতিহাসের খাতিরে। চরিত্ররা বাস্তব, কিন্তু সাহিত্যের প্রয়োজনে কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এখানে পাঠক ইতিহাসের অনেক অজানা বিষয়ের সাথে পরিচিত হবেন নানা চরিত্রের মাঝ দিয়ে। আবার একশ্রেণির মতলববাজ মানুষের নেতিবাচক মনস্তত্ত্ব, আরেক শ্রেণির মানুষের ইতিবাচক সহৃদয়তা, সম্প্রীতি ও বৈচিত্র্য ধারণের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা, অপরাজনীতির বাতাবরণ ভেঙে ফেলে সামনে এগোনোর জন্য সৎ নেতৃত্বের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার, মানুষের কল্যাণ কামনায় নিজস্বার্থ বিসর্জন দেওয়ার পাশাপাশি ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির শৈল্পিক প্রকাশ রয়েছে এই উপন্যাসে। একটি নির্মোহ জায়গা থেকে সবকিছুকে দেখার প্রচেষ্টা রয়েছে এখানে। শরীফ আতিক-উজ-জামানের ‘দহনকথা’ তাকে বাঁচিয়ে রাখবে বলে বিশ্বাস করি।
(বইটির প্রকাশক : ধ্রুবপদ । প্রচ্ছদ : রিও। মূল্য : ১৬৩ টাকা।)






















 দীপংকর গৌতম
দীপংকর গৌতম
















