জন্মদিন
বহুমুখী প্রতিভার এক অনন্য নাম অন্নদাশঙ্কর রায়
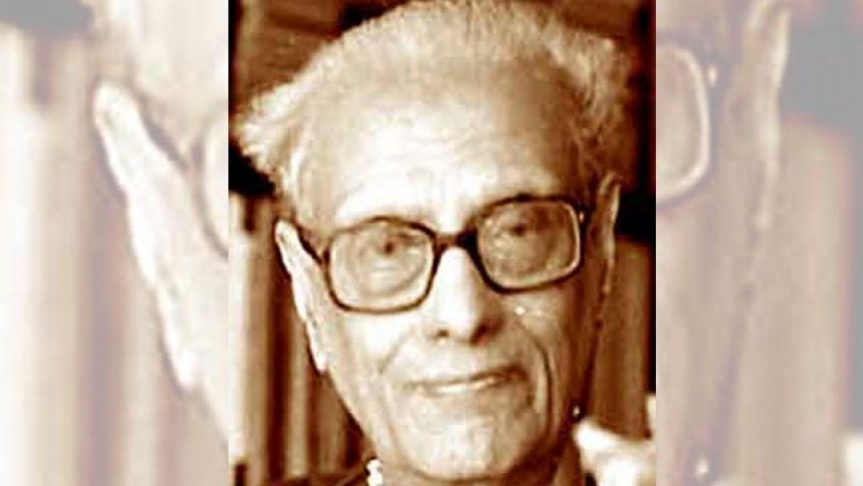
উনিশ শতকের বাঙালি রেনেসাঁ ঐতিহ্যের শেষ বুদ্ধিজীবী হিসেবে যাঁর নাম উচ্চারণ করা হয়, তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়। ওড়িশার দেশীয় রাজ্য ঢেঙ্কানালের এক শাক্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। অন্নদাশঙ্করের পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোতরং গ্রামে। কর্মসূত্রে তাঁরা বসবাস শুরু করেন ওড়িশার ঢেঙ্কানালে। জমিদার হিসেবে তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন প্রজাহিতৈষী, মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী। তাঁদের পরিবারে নিয়মিত চর্চা হতো সাহিত্য-সংস্কৃতির।
পিতামহ শ্রীনাথ রায়, পিতা নিমাইচরণ রায় ও কাকা হরিশচন্দ্র রায়- এঁরা সবাই ছিলেন সাহিত্যরসিক এবং শিল্প-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এমনকি এক বন্ধুর সঙ্গে মিলে ওড়িয়া ভাষায় নিমাইচরণ অনুবাদ করেন ‘শ্রী চৈতন্যচরিতামৃত’। মা হেমনলিনী ছিলেন বৈষ্ণব ভাবাদর্শে বিশ্বাসী এবং কটকের বিখ্যাত পালিত পরিবারের সন্তান। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মিশ্র পরিবেশে কেটেছে অন্নদাশঙ্করের শৈশব।
অন্নদাশঙ্করের শিক্ষাজীবন আরম্ভ হয় ঢেঙ্কানালের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ১৯২১ সালে ঢেঙ্কানাল হাইস্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন এবং ভর্তি হন তৎকালীন পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কটক র্যাভেনশ কলেজে। ১৯২৩ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইএ পরীক্ষায় তিনি অধিকার করেন প্রথম স্থান। ১৯২৫ সালে তিনি পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্সসহ বিএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হন। এমএ (ইংরেজিতে) শ্রেণিতে পড়াকালে ১৯২৭ সালে অন্নদাশঙ্কর রায় আইসিএস পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান ইংল্যান্ডে। সেখানে তিনি লন্ডনের ‘ইউনিভার্সিটি কলেজ’, ‘কিংস কলেজ’, ‘লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস’, ‘লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ’-এ পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
এরই ফাঁকে ঘুরে বেড়ান সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ। ফলে ভ্রমণের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটে তাঁর সাহিত্যে। প্রশিক্ষণ শেষে ফিরে ১৯২৯ সালে অন্নদাশঙ্কর রায় যোগ দেন মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে অ্যাসিসট্যান্ট ম্যাজিস্ট্রেট পদে। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৮ বছরের মধ্যে নয় বছর পশ্চিমবঙ্গে এবং নয় বছর পূর্ববঙ্গে বিভিন্ন পদে নিয়োজিত ছিলেন তিনি। অবিভক্ত বঙ্গের মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া, নদীয়া, ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, হুগলি এবং হাওড়ায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন কখনো শাসন বিভাগে, কখনো বিচার বিভাগে যথাক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ হিসেবে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তিনি উচ্চতর পর্যায়ের ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসের (আইএএস) সদস্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসন ও বিচার বিভাগে কাজ করেন। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বিষয়কে কেন্দ্র করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯৫০ সালে পদত্যাগপত্র দেন এবং ১৯৫১ সালে বিচার বিভাগের সচিব পদ থেকে অব্যাহতি পান তিনি।
চাকরি ছাড়ার পর অন্নদাশঙ্কর বসবাস শুরু করেন শান্তিনিকেতনে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য বাঙালির আত্মদান তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। পরের বছর ১৯৫৩ সালে এক ঐতিহাসিক ‘সাহিত্য মেলা’র আয়োজন করেন তিনি শান্তিনিকেতনে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই সাহিত্য মেলায় যোগ দেন কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, শামসুর রাহমান, কায়সুল হকসহ আরো অনেকে।
অন্নদাশঙ্করের শান্তিনিকেতনের বাড়িতে নিয়মিত ‘সাহিত্য সভা’ হতো এবং সেখানে সমাবেশ ঘটত আশ্রমের সাহিত্য রসিকদের। এ ছাড়া দেশি-বিদেশি বহু পণ্ডিত অতিথি হয়ে আসতেন তাঁর বাড়িতে। নানা দেশের নানা ভাষার মানুষের সমাগমে সেখানে তৈরি হতো এক আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল। শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে অন্নদাশঙ্কর ছিলেন বিশ্বভারতীর কর্মসমিতির সদস্য। ষাট দশকের শেষ দিকে পারিবারিক কারণে বসবাস শুরু করেন কলকাতায় এসে এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে থেকে যান তিনি।
বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্নদাশঙ্কর রায় ওড়িয়া সাহিত্যিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন মাত্র ২০ বছর বয়সেই। তাঁর প্রথম কবিতা রচিত হয়েছে ওড়িয়া ভাষায়। অল্প বয়সেই বের করেন ‘প্রভা’ নামে ওড়িয়া ভাষায় হাতে লেখা একটি পত্রিকা। বাংলা, ইংরেজি, ওড়িয়া, সংস্কৃত, হিন্দি-সব ভাষায় পারদর্শী হলেও বাংলাকেই তিনি সাহিত্যচর্চার মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন। বাড়ির ও কলেজের গ্রন্থাগারে তিনি সুযোগ পান ভারতীয় এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হন। স্কুলে তিনি শিশু, সন্দেশ, মৌচাক, সবুজপত্র, প্রবাসী, মডার্ন রিভিউ প্রভৃতি পত্রিকা পড়ার। মাত্র তেরো বছর বয়সে অক্সফোর্ড থেকে প্রকাশিত পত্রিকার গ্রাহক হন তিনি এবং ওই পত্রিকায় প্রকাশ করেন নিজের লেখা।
প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত ‘সবুজপত্র’ ছিল অন্নদাশঙ্করের লেখক হয়ে ওঠার প্রেরণা। সবুজপত্র পত্রিকার দুই প্রধান লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রমথ চৌধুরীর জীবনদর্শন ও শিল্পাদর্শ তাঁর সাহিত্য-মানস গঠনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে টলস্টয়কেও আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন তিনি। টলস্টয়ের সত্যের প্রতি অনুরাগ এবং রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যপ্রীতি তাঁকে আকৃষ্ট করে। ১৬ বছর বয়সে টলস্টয়ের গল্প ‘তিনটি প্রশ্ন’ বাংলায় অনুবাদ করেন তিনি এবং তা প্রবাসী পত্রিকায় ছাপা হয় ১৯২০ সালে। বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত মৌলিক রচনার বিষয় ছিল নারীর অধিকার ও স্বাধীনতা, যা ভারতী পত্রিকায় ছাপা হয়। এ ধরনের বিষয় নিয়ে তিনি ওড়িয়া ভাষায়ও লেখেন। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ‘রক্তকরবী’ নাটকের ওপর যে প্রবন্ধ লেখেন, তা রবীন্দ্রনাথকেও আলোড়িত করে। অন্নদাশঙ্করের প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ তারুণ্য ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় বিচিত্রা পত্রিকায়। তবে তাঁর ইউরোপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা ‘পথে প্রবাসে’ ভ্রমণকাহিনীর মাধ্যমেই তিনি বাংলা সাহিত্যে নিজের স্থান করে নেন। ১৯২৭ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত দুই বছর উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘পথে প্রবাসে’। একই সময় মৌচাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তাঁর ‘ইউরোপের চিঠি’।
অন্নদাশঙ্কর রায় কোনো গোষ্ঠীভুক্ত লেখক ছিলেন না। তবে সম্পাদকদের অনুরোধে কল্লোল, কালিকলম, পরিচয় প্রভৃতি পত্রিকার জন্য লেখেন বেশ কিছু লেখা। কল্লোল, কালিকলম যুগের সাহিত্যিক এবং বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন ও শিখা গোষ্ঠীর প্রতিভূদের সঙ্গেও তাঁর ছিল অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রায় সত্তর বছর ধরে প্রবন্ধ, উপন্যাস, ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী, ছড়া, কবিতা, নাটক, পত্রসাহিত্য, আত্মজীবনীমূলক রচনা প্রভৃতি লিখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন তিনি। সব মিলিয়ে তাঁর গ্রন্থের সংখ্যা বাংলায় ১২৩টি, ইংরেজিতে ৯টি এবং ওড়িয়া ভাষায় ৩টি। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি বৈচিত্র্যপূর্ণ। গদ্য ও পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই ভূমিকা রেখেছেন তিনি। কেবল আঙ্গিকে নয়, ভাববৈচিত্র্যেও তাঁর রচনা কালোত্তীর্ণ। বহুমুখী ভাবানুভূতি তাঁর রচনার বিশেষত্ব। বিষয়বৈচিত্র্যে তাঁর রচনা সমৃদ্ধ।
ইতিহাস, সাহিত্যতত্ত্ব, দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমকালীন বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ তাঁর গদ্যের বিষয়। প্রবন্ধসাহিত্যে তিনি ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সার্থক উত্তরসূরি। তবে রবীন্দ্রযুগের লেখক হলেও তাঁর স্টাইল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি ছিলেন মুক্তচিন্তা, আদর্শবাদ ও শুভবুদ্ধির প্রতীক। দেশভাগ, দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী ছিল আজীবন সোচ্চার। কল্পনা ও যুক্তি, প্রেম ও বিবেক, স্বদেশ ভাবনা, বিশ্বচিন্তা ও বিজ্ঞানমনস্কতার সমন্বয় তাঁর প্রবন্ধসমূহ।
অন্নদাশঙ্কর রায়ের বাংলা ছড়াসম্ভার বিষয়বৈচিত্র্যে তাৎপর্যপূর্ণ প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ এবং পরে বুদ্ধদেব বসুর অনুরোধে তিনি শুরু করেন ছড়া লেখা। সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় থেকে শুরু করে প্রাণীজগতের ক্ষুদ্র জীবজন্তুও স্থান পেয়েছে তাঁর ছড়ায়। তীব্র শ্লেষে, স্নিগ্ধ পরিহাসে, আবার কখনো নিখাদ কৌতুকে তিনি মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের অসঙ্গতিগুলি তুলে ধরেন ছড়ার মাধ্যমে। একসময়ের ছেলেভুলানো ছড়াকে তিনি উপেক্ষিত স্তর থেকে উন্নীত করেন অভিজাত সাহিত্যের শৈল্পিক স্তরে। তাঁর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছড়া : ‘খোকা ও খুকু’ (১৯৪৭)। এতে সুর দিয়েছেন বিখ্যাত সুরকার সলীল চৌধুরী। দেশবিভাগজনিত বেদনা তীর্যকভাবে প্রকাশ পেয়েছে এই ছড়ায়- ‘তেলের শিশি ভাঙল বলে/খুকুর ’পরে রাগ করো,/তোমরা যে সব বুড়ো খোকা/ভারত ভেঙে ভাগ করো। তার বেলা?’ তাঁর বেশ কিছু ছড়া প্রতিষ্ঠিত সুরকারদের সুরে এভাবে রূপ পেয়েছে জনপ্রিয় গানে।
১৯৩০ সালের ঘটনা। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের বিদুষী তরুণী অ্যালিস ভার্জিনিয়া ওর্নডর্ফ ভারতে আসেন ভারতীয় সঙ্গীত বিষয়ে গবেষণার জন্য। লেখক ভবানী মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে অ্যালিসের সঙ্গে পরিচয় ঘটে অন্নদাশঙ্করের। পরিচয় থেকে প্রণয়, পরে পরিণয়ে আবদ্ধ হন তাঁরা। সেই সময় ‘লীলাময় রায়’ ছদ্মনামে লিখতেন অন্নদাশঙ্কর। রবীন্দ্রনাথ অ্যালিসের নতুন নামকরণ করেন ‘লীলা রায়’। অন্নদাশঙ্করের জীবনে লীলা রায়ের প্রভাব ব্যাপক। বহু ভাষায় পারদর্শী লীলা রায় নিজেও খ্যাতিলাভ করেন সাহিত্যিক এবং অনুবাদক হিসেবে। কর্মসূত্রে পূর্ববঙ্গে অতিবাহিত করার সময় এখানকার সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, ভূমিব্যবস্থা এবং ধর্মীয় সংস্কৃতি বিষয়ে গড়ে ওঠে তাঁর সম্যক ধারণা। বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষী মানুষের প্রতি তাঁর দরদ ও সহমর্মিতা ছিল আজীবন অটুট। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালে এবং ১৯৯৬ সালে অন্নদাশঙ্কর দুইবার এ দেশে আসেন সরকারের অতিথি হিসেবে।
অন্নদাশঙ্কর রায় ছিলেন সাহিত্য একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও ফেলো। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমির জন্মকাল ১৯৮৬ সাল থেকে তিনি ছিলেন এর আজীবন সভাপতি ও পথিকৃৎ। সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি বহু পুরস্কারে ভূষিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে জগত্তারিণী পুরস্কারে ভূষিত করে ১৯৭৯ সালে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করে দেশিকোত্তম সম্মান। বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে প্রদান করে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (১৯৬২), আনন্দ পুরস্কার (দুইবার-১৯৮৩, ১৯৯৪), বিদ্যাসাগর পুরস্কার, শিরোমণি পুরস্কার (১৯৯৫), রবীন্দ্র পুরস্কার, নজরুল পুরস্কার, বাংলাদেশের জেবুন্নিসা পুরস্কার। ২০০২ সালের ২৮ অক্টোবর কলকাতায় অন্তিমশ্বাস ত্যাগ করেন এই বহুমুখী প্রতিভাধর মানুষটি।





















 অঞ্জন আচার্য
অঞ্জন আচার্য















