ঠাকুরের সহিত বিচার
বাংলা বানানে হ্রস্ব ইকার (শেষ কিস্তি)
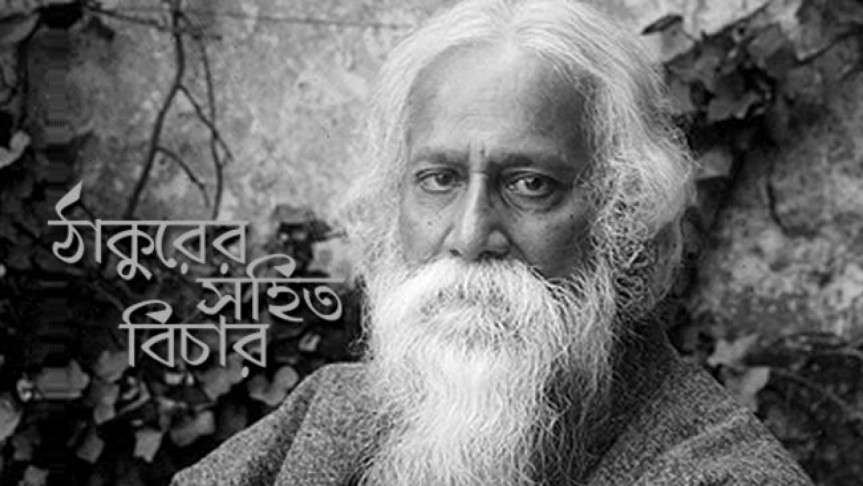
হ্রস্ব ইকারের অধিকার
যেখানে খাস্ বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ সেখানে হ্রস্ব ইকারের অধিকার, সুতরাং দীর্ঘ ঈ’র সেখান হইতে ভাসুরের মতো দূরে চলিয়া যাওয়াই কর্তব্য।’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব , পৃ. ১১২)
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ‘বাঙ্গালা বানান সমস্যা’ নামে এক প্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলেন বাংলা ১৩৩১ সালে। তাহার পরের বছর মাত্র বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বকলম প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ বাহির হয় রবীন্দ্রনাথের আদেশ- বাংলা ‘কি’ শব্দ দুই বানানে লিখিতে হইবে। শহীদুল্লাহর বিষয় ছিল খানিক ভিন্ন। তিনি বলিতেছিলেন বাংলার সকল শব্দই উচ্চারণ অনুযায়ী লিখিতে হইবে। তাঁহার বক্তব্য ছিল, শ্রবণ করা অর্থে বাংলায় ‘শোনা’ শব্দ লেখা হইয়া থাকে। কিন্তু স্বর্ণ অর্থে তাহা কেন ‘শোনা’ লেখা হইবে না? একটা উত্তর- সংস্কৃত স্বর্ণ শব্দে দন্ত্য ‘স’ আছে, তাই ‘সোনা’ লেখাই স্বাভাবিক। তিনি বলিলেন, ‘সোনা’ শব্দের উচ্চারণ তো ‘শোনা’। তাই ‘শোনা’ লেখাই তো উচ্চারণের বিচারে স্বাভাবিক।
তখন আপত্তি উঠিতেছে, ‘স্বর্ণ’ আর ‘শ্রবণ করা’ দুই অর্থ, দুই ভাব। এই ভাবের তফাত বজায় রাখিতে হইলে বানানের তফাত রাখার দরকার আছে। স্বর্ণ অর্থের ব্যঞ্জনা আর ‘শ্রবণ করা’র ব্যঞ্জনা কি এক জিনিস? উভয়ের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক ‘শোনা’শব্দে দুই ভাব প্রকাশ হইবে কি করিয়া? অথবা ‘সোনা’আর ‘শোনা’ দুই বানানই রাখিতে হয়। ইহার জবাবেই মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিলেন : ‘যদি বল এ কি হইল! স্বর্ণ আর শ্রবণ করা দুই-ই যদি শোনা হয়, তবে মানে বুঝিব কেমন করিয়া?’
“আমি বলিব যদি গায়ের তিলে গাছের তিলে কোন গোল না ঠেকে, যদি গানের তালে আর নাচের তালে ঠোকাঠুকি না ঘটে, তবে স্বর্ণ শোনায় আর শ্রবণ শোনায়ও কোন হাঙ্গামা হইবে না। আসল কথা, ভাষায় অক্ষরের মত শব্দ কখন দল ছাড়া হইয়া একেলা আসে না। অক্ষর থাকে শব্দের সঙ্গে জড়াইয়া আর শব্দ থাকে বাক্যের মধ্যে মিশিয়া। কাজেই মানে যদি আলাদা আলাদা হয়, তবে বানান বা উচ্চারণ এক হইলেও বুঝিবার গোলমাল বড় একটা হয় না।” (ভাষা ও সাহিত্য, স. ৩, পৃ. ৮১)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহু জায়গায় কবুল করিয়াছেন তিনি ব্যাকরণে কাঁচা। তাঁহার ভাষায়, ‘কী সংস্কৃত ভাষায় কী ইংরেজিতে আমি ব্যাকরণে কাঁচা’। কিন্তু বাংলায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে প্রমাণ হয় না বাংলা ব্যাকরণ তিনি আর কাঁহারও অপেক্ষা কম জানেন। তবু তাঁহার বিনয়কে অবিশ্বাস করিব না। তিনি জানাইয়াছেন, “ভাষাতত্ত্বে প্রবীণ সুনীতিকুমারের সঙ্গে আমার তফাত এই- তিনি যেন ভাষা সম্বন্ধে ভূগোলবিজ্ঞানী, আর আমি যেন পায়ে-চলা-পথের ভ্রমণকারী।” (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৯) বৈষ্ণব ভাবিয়া বিনয়কে তুচ্ছ করিবেন না।
পায়ে চলা পথের এক জায়গায় শেষ হয়। সে কথা কবির অজানা নয়। পায়ের পথিক ভূগোলে অপটু হইতেই পারেন। তাহাতে দোষ নাই। দোষ অপটুতাকে ধর্মের মর্যাদা দেওয়ায়। ঠাকুর মোটেও নিশ্চিত হইতে পারেন নাই, বাংলা ‘কি’ শব্দটি কি, অর্থাৎ কোন জাতের? তিনি একবার বলিয়াছেন শব্দটি অব্যয়, আর বার বলিয়াছেন সর্বনাম। আগে এই প্রশ্নটির মীমাংসা না করিয়া হাঁটিতে শুরু করা পায়ে চলার কাজ সন্দেহ নাই, ভূগোলবিজ্ঞানীর কাজ এ রকম নহে। কিছুক্ষণের মধ্যেই শব্দটি বিশেষণ হইয়া যায়। আবার আরো বিশেষ করিয়া দেখিলে ইহাকে ‘ক্রিয়া বিশেষণ’ হিসাবেও দেখা যায়। প্রয়োজনে সে বিশেষ্যের ভূমিকাও লইতে পারে। ক্রিয়ার কাজও কখনো বা সে করিলে বিস্ময়ের থাকিবে না।
এই যে বিভিন্ন প্রয়োগ, বিবিধ ব্যবহার তাহার মধ্যে কি কোনই ঐক্য নাই? সেই ঐক্যের নিয়মের সূত্র যতদূর জানি পহিলা রাজা রামমোহন রায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভাবিতে শিহরিয়া উঠি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি সেই আবিষ্কারের খবর লয়েন নাই? না লইবার কোন কারণ তো নাই। তবে আলামত দেখিতেছি। ঠাকুরের লেখায় ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ বলেন :
“প্রশ্নসূচক ‘কি’ শব্দের অনুরূপ আর-একটি ‘কি’ আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম। এ তার প্রকৃত অর্থের প্রয়োজন সেরে মাঝে মাঝে খোঁচা দেবার কাজে লাগে। যেমন : কী তোমার ছিরি, কী যে তোমার বুদ্ধি।” (‘বাংলা ভাষা-পরিচয়’, পৃ. ১১৩)
রামমোহন ভাল করিয়া পড়া থাকিলে রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়া লইতেন, বাংলায় ‘কি’ শব্দ একটাই। কারকভেদে (অথবা রামমোহনের ভাষায় ‘পরিণমন’ বা ‘পরিণাম’ ভেদে) ইহার রূপভেদ হয় মাত্র। যেমন ‘কি’ শব্দ কর্তৃকারকে (রামমোহনের ভাষায় ‘অভিহিত’ পদে) যেমন ‘কি’ কর্মকারকেও তেমনি ‘কি’ই। অধিকরণে ‘কিসে’ অথবা ‘কিসেতে’ আর সম্বন্ধে ‘কিসের’। সবগুলিই ‘কি’ শব্দের আত্মীয়রূপ বৈ নহে। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৮)
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ দেখাইয়াছেন, রামমোহনের ব্যাকরণে একটু অপূর্ণতা আছে। কি, কিসে, কিসেতে, কিসের প্রভৃতি সকল শব্দরূপের গোড়া মাত্র ‘কি’ নহে। ‘কি’ শুদ্ধ সকলেরই গোড়া হইল অন্য একটি রূপ- কাহা (বা কাঁহা)। ইহা ক্লীবলিঙ্গ শব্দ। জাতিতে সর্বনাম। ইহার সহিত তুলনীয়, সহধর্মিণী আরও সর্বনাম শব্দ আছেন, যথা: তাহা, যাহা, ইহা, উহা ইত্যাদি।
তবে কাহা শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া তাহার রূপের খানিক বিশেষত্ব রহিয়াছে। এই শব্দে বিভক্তির একবচন রূপ কর্তা ও কর্ম দুই কারকেই ‘কি’। বহুবচনে ‘কিসের’। তবে শহীদুল্লাহ লিখিয়াছেন, “কাহা শব্দের ক্লীবলিঙ্গের বহুবচনে প্রয়োগ নাই। কখনও কখনও বহুবচন বুঝাইতে দ্বিরুক্তি হয়। যথা- কি কি হইয়াছে? সে কি কি লইয়াছে?” (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, স. মাওলা ব্রাদার্স, মু. ২, পৃ. ৭৮)
মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মোটেও কেমাল পাশা নহেন। তিনিও প্রচলিত ব্যাকরণের মতো বাংলায় ছয় কারকই দেখাইয়াছেন। রামমোহন বলিয়াছেন, বাংলায় দরকারই নাই অত কারকের। তাঁহার বয়ান : “গৌড়ীয় ভাষাতে নামের চারি প্রকার রূপের দ্বারা প্রয়োজনসিদ্ধি হয়, অভিহিত, যেমন রাম, কর্ম্ম, যেমন রামকে; অধিকরণ, যেমন রামে; সম্বন্ধ, যেমন রামের।” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১৩) রামমোহনের কথাই সঠিক বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি। আরো মনে করিতে পারি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয়ও রামমোহনের কথানুসারে অমৃত হইয়াছিল।
‘যাহার দ্বারা ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার বোধের নিমিত্ত ভাষাতে অভিহিত পদের পরে “দিয়া” শব্দের প্রয়োগ করা যায়, যেমন, ছুরি দিয়া কাটিলেন। আর কখন [কখন] সম্বন্ধ পরিণামের পরে “দ্বারা” শব্দ দিয়া ঐ করণকে কহা যায়; যেমন, ছুরির দ্বারা কাটিলেন।’(পৃ. ১৫) আরো পড়া যাইতেছে : ‘কখন বা অধিকরণ বাচক বিভক্তির দ্বারা করণের জ্ঞান হইয়া থাকে, যদি সেই করণ অপ্রাণি হয়; যেমন, ছুড়িতে কাটিলেন। অতএব করণের নিমিত্ত শব্দের পৃথক রূপ করিবার আবশ্যক দেখি নাই।’ (পৃ. ১৫) শহীদুল্লাহ করিয়াছেন, ‘কি দিয়া, কিসের দ্বারা, কিসে।’ দরকার ছিল কি? (বাঙ্গালা ব্যাকরণ, মু. ২, পৃ. ৭৭)
একই কারণে রামমোহন বলিলেন, বাংলায় অপাদান কারকেরও প্রয়োজন নাই। পড়া যাইতেছে :
‘কোন এক ক্রিয়ার বক্তব্য স্থলে যখন অন্য বস্তু হইতে এক বস্তুর নিঃসরণ অথবা ত্যাগ বোধ হয়, তখন তাহার জ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রথম বস্তুর নামের পরে যদি সেই প্রথম বস্তু একবচনান্ত হয় তবে “হইতে” এই শব্দের প্রয়োগ করা যায়। আর যদি বহুবচনান্ত হয় তবে বহুবচনান্ত সম্বন্ধীয় পরিণাম পদের পরে “হইতে” ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে, যেমন গ্রাম হইতে, মন্ত্রিদের হইতে, বেণেদের হইতে, অতএব বঙ্গভাষায় অপাদান কারকের নিমিত্ত শব্দের পৃথক রূপ করিবার আবশ্যক নাই।’ (পৃ. ১৫)
তদ্রূপ “সম্বোধনের নিমিত্তেও শব্দের পৃথক রূপের প্রয়োজনাভাব” বলিয়া রামমোহন তাহার আলাদা প্রকরণ করেন নাই। সম্প্রদান সম্বন্ধেও একই কথা খাটিবে : “ভাষাতে রূপান্তরাভাব, এই হেতুক লিখা গেল না।” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১৪, পাদটীকা ৩)
মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সহিত পণ্ডিত হরনাথ ঘোষ আর সুকুমার সেনের ব্যাকরণও একমত। ঘোষ ও সেনের বইতে ‘কাহা’ শব্দের সম্ভমসূচক একটা রূপও পাওয়া যাইতেছে- কাঁহা বা সংক্ষেপে কাঁ। (বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ, পৃ. ২৭৫)
এই সকল কিছু না দেখিয়াই, না চিন্তিয়াই রবীন্দ্রনাথ বলিলেন, শ্যামাপ্রসাদ, আইন কর। বাংলাভাষার অনেক মহদুপকার রবীন্দ্রনাথ করিয়াছেন। কিন্তু বাংলা তো তাহাকে “কি” শব্দের বানান বদলাইবার অধিকার দেয় নাই। এয়াহুদিপুরানে বলে, সন্তানের গলা কাটিবার অধিকার স্বয়ং ভগবানও এব্রাহিমকে দেন নাই। তিনি তাঁহাকে পরীক্ষা মাত্র করিতেছিলেন। দীপ্তি হউক বলিলেই ভাষায় দীপ্তি হয় না। কোন ভাষাই মাত্র ছয় দিনে তৈরি হয় নাই।
রামমোহনে ফিরিয়া চল
‘কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিশেরও জোর।’ -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৭৯
রাজা রামমোহন রায় দেখাইয়াছেন ভাষার তাবৎ শব্দ প্রথমত দুই প্রকারে বিভক্ত হয় : বিশেষ্য ও বিশেষণ। “যে শব্দের অর্থ প্রাধান্যরূপে জ্ঞানের বিষয় হয় তাহাকে বিশেষ্য কহে; যেমন, রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর, ইত্যাদি স্থলে রামের জ্ঞান প্রাধান্যরূপে হয়, এ নিমিত্তে রাম বিশেষ্য।
“আর যাহার অর্থ অপ্রাধান্য রূপে বুদ্ধির বিষয় হয় তাহাকে বিশেষণ পদ কহে, রাম যাইতেছেন, রাম সুন্দর ইত্যাদি স্থলে যাইতেছেন ও সুন্দর এ দুই শব্দের অর্থ রাম শব্দের অর্থেতে অনুগত হয়, এ কারণ বিশেষণ পদ কহে।” (পৃ. ১১)
রামমোহনের ব্যাকরণে বিশেষ্য নানা প্রকারের হয়। বিশেষ্যকে ‘নাম’ অথবা ‘সংজ্ঞা’ দুইটাই বলিয়াছেন তিনি। এই কাণ্ডজ্ঞান অনুসারে “কাহা” শব্দও একপ্রকার ‘সংজ্ঞা’ বা ‘নাম’ শব্দ। সুতরাং ভাষার প্রথম দুই ভাগ অনুসারে কাহা শব্দের জাতক ‘কি’ শব্দ বিশেষ্য। বিশেষ্য বা সংজ্ঞার মধ্যে ইহা প্রতিসংজ্ঞা বা সর্বনাম জাতীয় হইয়াছে। রামমোহনের সহিত সম্যক পরিচয় থাকিলে ‘বাংলাভাষা-পরিচয়’ বইতে রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করিতে হইত না, “প্রশ্নসূচক ‘কি’শব্দের অনুরূপ আর-একটি ‘কি’আছে, তাকে দীর্ঘস্বর দিয়ে লেখাই কর্তব্য। এ অব্যয় নয়, এ সর্বনাম।” (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ১১৩)
সত্যের অনুরোধে বলিতে হয় কি শব্দ আদিতে সর্বনাম, তবে অব্যয় হিসাবে তাহার প্রয়োগ আছে। অন্য প্রয়োজনেও তাহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। রামমোহন লিখিয়াছেন : “বিশেষ্য পদকে নাম কহি, অর্থাৎ এ রূপ বস্তুর নাম হয় যাহা আমাদের বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর হইয়া থাকে। যেমন রাম, মানুষ, ইত্যাদি। অথবা যাহার উপলব্ধি কেবল অন্তরিন্দ্রিয়-দ্বারা হয় তাহাকেও এইরূপ নাম কহেন, যেমন ভয়, প্রত্যাশা, ক্ষুধা ইত্যাদি।”
‘ঐ নামের মধ্যে কতিপয় নাম বিশেষ ব্যক্তির প্রতি নির্ধারিত হয়, তাহাকে ব্যক্তি সংজ্ঞা কহি, যেমন রামচরণ, রামভদ্র, ইত্যাদি। আর কতিপয় নাম এক জাতীয় সমূহ ব্যক্তিকে কহে, তাহাকে সাধারণ সংজ্ঞা কহি, যেমন মনুষ্য, গরু, আম্র, ইত্যাদি। এবং কতক নাম নানাজাতীয় সমূহকে কহে, যাহার প্রত্যেক জাতি অন্য [অন্য] জাতি হইতে বিশেষ [বিশেষ] ধর্ম্মের দ্বারা বিভিন্ন হয়, তাহাকে সর্ব্বসাধারণ বা সামান্য সংজ্ঞা কহি, যেমন ‘পশু’, মনুষ্য, গরু, হস্তি প্রভৃতি নানাবিধ বিজাতীয় পদার্থ সমূহকে কহে। এবং “বৃক্ষ” নানাবিধ বিজাতীয় আম, জাম, কাঁটাল ইত্যাদিকে প্রতিপন্ন করে’।
‘ঐ নামের মধ্যে কতিপয় শব্দ ব্যক্তি বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত নির্দ্ধারিত হয়, অথচ ঐ সকল শব্দ স্বয়ং স্বতন্ত্র বিশেষ [বিশেষ] ব্যক্তিকে কিম্বা বিশেষ ব্যক্তিসমূহকে নিয়ত অসাধারণরূপে প্রতিপন্ন করে না, ওই সকলকে প্রতিসংজ্ঞা কহি, যেমন আমি, তুমি, সে, ইত্যাদি।’ (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১১-১২, নিম্নরেখা আমরা যোগাইয়াছি)
একইভাবে রামমোহন রায় বিশেষণ শব্দেরও নানান জাতি নির্ণয় করিয়াছেন। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণে যে সকল শব্দকে বিশেষণ বলা হইয়া থাকে, তাহাদের নাম রামমোহন রাখিয়াছেন ‘গুণাত্মক বিশেষণ’। লিখিয়াছেন : ‘বিশেষণ শব্দের মধ্যে যাহারা বস্তুর গুণকে কিম্বা অবস্থাকে কাল সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কহে, সে সকল শব্দকে গুণাত্মক বিশেষণ কহি, যেমন, ভাল, মন্দ, ইত্যাদি।’(গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১২, নিম্নরেখা আমরা যোগ করিয়াছি)
“আর যাহারা কালের সহিত সম্বন্ধপূর্ব্বক বস্তুর অবস্থাকে কহে, তাহাকে ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, আমি মারি, তুমি মারিবে।” প্রচলিত ব্যাকরণে এই পদের নাম ‘ক্রিয়া’মাত্র। ক্রিয়ার অপর নাম ‘আখ্যাত’পদ। ইহা ভাষায় ব্যবহার্যও হইয়াছে। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ৩২)
গুণাত্মক এবং ক্রিয়াত্মক ছাড়াও রাজা রামমোহন রায় আরও পাঁচ জাতের বিশেষণ নির্ণয় করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে, ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ, বিশেষণীয় বিশেষণ, সম্বন্ধীয় বিশেষণ, সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ এবং অন্তর্ভাব বিশেষণ রহিয়াছে। মনোযোগ করিবার বিষয়, অব্যয়ের জন্য তিনি কোন আলাদা প্রকরণ করেন নাই।
সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের তারিফ করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার এই অব্যয় জাতীয় শব্দের আলাদা প্রকরণ না করার কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি শুদ্ধ বিজ্ঞাপন দিয়াছেন: “রামমোহন ‘সর্বনাম’-কে বলেছেন ‘প্রতিসংজ্ঞা’, এর সঙ্গে তুলনীয় পঞ্জাবীতে ব্যবহৃত নাম ‘পড়নাঊঁ’ (= প্রতিনাম)। নামটি সার্থক, ‘সর্বনাম’এই শব্দের মতো এর ব্যাখ্যার আর প্রয়োজন থাকে না। ‘প্রতিনাম’শব্দটির সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার জন্যে আমি ‘সর্বনাম’-এর পাশে ‘প্রতিনাম’ শব্দটিও আমার বাঙলা ব্যাকরণে ব্যবহার করেছি।” (মনীষী স্মরণে, পৃ. ৬)
রামমোহন দেখিয়াছেন ভাষায় অব্যয়ের কাজ বিশেষণেরই কাজ। তিনি কাজ দেখিয়া নাম করিয়াছেন, রূপ দেখিয়া ভোলেন নাই। তাই অব্যয় শব্দের আলাদা প্রকরণ করার “প্রয়োজনাভাব” হইয়াছে। কয়েক গুটি উদাহরণ লইলেই আবিষ্কারটি পরিচ্ছন্ন হইবে। মেঘ কাটিয়া যাইবে।
ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণকে ইংরেজিতে বলে ‘পার্টিসিপ্ল্’। ইহা কি পদার্থ? রামমোহন কহেন, “যাহারা অন্য ক্রিয়াগত কালের সাপেক্ষ হইয়া বস্তুর কাল সংক্রান্ত অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্দকে ক্রিয়াপেক্ষ ক্রিয়াত্মক বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি প্রহার করত বাহিরে গেলেন, ভোজন করিতে [করিতে] কহিয়াছিলেন।” (পৃ. ১২)
আর “যাহারা ক্রিয়া কিংবা গুণাত্মক বিশেষণের অবস্থাকে কহে, সে সকল শব্দকে বিশেষণীয় বিশেষণ কহি; যেমন, তিনি শীঘ্র যান, তিনি অত্যন্ত মৃদু হন।” (পৃ. ১২)
প্রচলিত ব্যাকরণের অব্যয়কেও রামমোহন ‘বিশেষণ’রূপেই আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যথা : “যে সকল শব্দকে পদের পূর্ব্বে কিম্বা পরে নিয়মমতে রাখিলে সেই পদের সহিত অন্য পদের সহিত অন্য শব্দের সম্বন্ধ বুঝায়, সেই শব্দকে সম্বন্ধীয় বিশেষণ কহি; যেমন রামের প্রতি ক্রোধ হইয়াছে।” (পৃ. ১২) ইংরেজিতে এইসব পদকে প্রিপোজিশন কহে।’
‘রামের’পদ বানাইতে রাম শব্দের সহিত যাহা যোগ করা হইয়াছে (এর), তাহাতে বুঝাইত শুদ্ধ ক্রোধের কর্তা রাম। তবে কিনা ‘প্রতি’শব্দটি বসিয়া রামকে ক্রোধের গৌণকর্ম বানাইয়া সারিয়াছে। এই প্রতিশব্দটি বাংলায় ‘অনুসর্গ’ বলিয়াই কথিত হয়। রামমোহন রায়ের লেখা বাংলা ব্যাকরণের ইংরেজি-সংস্করণে এই জাতের পদকেও ‘প্রিপোজিশন’ বলা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছি। (নির্মল দাশ, বাংলা ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ, পৃ. ১৪৭)
বিশেষণের চতুর্থ প্রকারের (অব্যয়ের দ্বিতীয় শ্রেণী) নাম সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ। রামমোহন উল্লেখ করিলেন,
“যাহারা দুই বাক্যের মধ্যে থাকিয়া ঐ দুই বাক্যের অর্থকে পরস্পর সংযোগ কিংবা বিয়োগরূপে বুঝায়, অথবা দুই শব্দের মধ্যে থাকিয়া এক ক্রিয়াতে অন্বয় বোধক হয়, কিন্তু কোন শব্দের বিভক্তির বিপর্য্যয় করে না, সে সকল শব্দকে সমুচ্চয়ার্থ বিশেষণ কহি : যেমন, তিনি আমাকে অশ্ব দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমি লইলাম না; আমি এবং তুমি তথায় যাইব, আমাকে ও তোমাকে দিয়াছেন।”
ইংরেজিতে এইগুলি ‘কনজাংশন নামে চলে’। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১২)
পঞ্চম জাতীয় বিশেষণ (তৃতীয় শ্রেণীর অব্যয়) রামমোহনের বয়ানে এই রকম : “যাহারা অন্য শব্দ সংযোগ বিনাও ঝটিতি উপস্থিত অথবা অন্তকরণের ভাবকে বুঝায় তাহাকে অন্তর্ভাব বিশেষণ কহি; যেমন, হা আমি কি কর্ম্ম করিলাম!” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ১২-১৩)
এতক্ষণ একটু লম্বা শ্বাস টানিয়া রামমোহন পড়িবার কারণ কি? বাংলা ব্যাকরণে ‘কি’ শব্দ প্রতিসংজ্ঞা জাতীয় [অর্থাৎ বিশেষ্য কুলোদ্ভব] হইলেও বিশেষণকুলে হামেশাই তাহার যাতায়াত আছে- এই কথা প্রমাণ করার আবশ্যক দেখি আজিও ফুরাইল না। অথচ তাহার কুল পরিচয় প্রতিসংজ্ঞাতেই পাওয়া যাইবে। চেহারা দেখিয়া লোকে পরিচয় তারপরও ভুলিয়া যায়। এই কথা এখনও সত্য।
বাংলায় “আমি”, “তুমি”, “সে” প্রভৃতি শব্দের যে জাত “যে” শব্দেরও সেই জাতই। আমিকে “ইতর লোকে” “মুই” কহিয়া থাকে। তুচ্ছতা প্রকাশের নিমিত্ত “তুমি” স্থানে “তুই” হইয়া থাকে। “সে শব্দের প্রয়োগ অপ্রত্যক্ষ বস্তু বা ব্যক্তি যাহার জ্ঞান বা উল্লেখ পূর্বে থাকে তাহার স্থলে হয়, যেমন সে চৌকি, সে ব্যক্তি। “যখন সম্মান তাৎপর্য্য হইবেক তখন সে ইহার স্থানে তিনি কিম্বা তেঁহ আদেশ হয়, আর অন্য তাবৎ পরিনামে [কারকে] প্রথম স্বর সানুনাসিক উচ্চারণ হয়, যেমন, তাঁহাকে, তাঁহাদিগকে, তাঁহাদের, ইত্যাদি।” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৬)
“সে” শব্দের আরেক রূপ “এ”। বস্তুর কিম্বা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ-অভিপ্রেত হইলে “এ”শব্দের প্রয়োগ হয়। সম্মান অভিপ্রেত হইলে “এ”স্থানে “ইনি”আদেশ হয় এবং প্রথম স্বরেরও সানুনাসিক উচ্চারণ হয়। “কিয়দন্তর পরোক্ষ অভিপ্রেত হইলে “ও” শব্দের প্রয়োগ হয়, আর তাহার রূপ “এ” শব্দের মতন হইয়া থাকে। কেবল ওকারের স্থানে “উ”হইয়া থাকে। সম্মান অভিপ্রেত হইলে “ও”স্থানে উনি আদেশ হয়, আর প্রথম স্বরের সানুনাসিক উচ্চারণ হয়।”
“যে” শব্দ আসিয়াছে “যাহা” হইতে। এই শব্দ প্রতিসংজ্ঞা বা সর্বনাম। ইহার রূপও ‘সে’শব্দের ন্যায় হয়। অর্থাৎ সে, তাহাকে, তাহাতে, তাহার ইত্যাদির ন্যায় যে, যাহাকে, যাহাতে, যাহার ইত্যাদি হয়। সম্মান অভিপ্রেত হইলে যিনি, যাঁহাকে, যাঁহাতে, যাঁহার ইত্যাদি রূপে পরিণাম হয়।’ (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৭)
এখন ‘কাহা’ শব্দের রূপ। আবারও রামমোহন হইতে সাক্ষাৎ উদ্ধার করিতেছি:
‘জিজ্ঞাসার বিষয় পদার্থ যদি ব্যক্তি হয় তবে কে, আর যদি বস্তু হয় তবে কি, ইহার প্রয়োগ হয় কিন্তু অধ্যাহৃত কিম্বা উক্ত ক্রিয়া যাহার যোজক হইয়াথাকে, যেমন কে কহিয়াছিল? এ স্থলে বাক্যের অর্থ কে কহিয়াছিল উক্ত হইয়াছে; কি? অর্থাৎ কে বসিয়াছে, বা গিয়াছে। এ স্থলে ক্রিয়া উহ্য হইল, এবং কি কহিতেছে? কি? অর্থাৎ কি হয় ইত্যাদি।’ (পৃ. ২৭; নিম্নরেখার যোগান দিয়াছি, নিরেট লিখনরীতি রামমোহন রায়ের)
‘যাহা’শব্দের যে রূপ, কাহা শব্দেরও সেই রূপই হইয়া থাকে। “প্রভেদ এই যে সম্মান অভিপ্রেত হইলেও বিশেষ নাই।” (পৃ. ২৭) অর্থাৎ ‘যিনি’র ন্যায় ‘কিনি’ হয় না।
যদি সময় জিজ্ঞাস্য হয় তবে, “কবে”আর “কখন”শব্দের প্রয়োগ হয়। ইহাদের রূপান্তর নাই। তবে “ওই দুয়ের প্রভেদ এই যে, কবে, ইহার প্রয়োগ দিন জিজ্ঞাস্য [হইলে]; আর, কখন, ইহার প্রয়োগ সময় জিজ্ঞাস্য হইলে প্রায় হইয়া থাকে, যেমন কবে যাইবে? অর্থাৎ কোন্ দিন যাইবে? কখন যাইবে? অর্থাৎ কোন্ সময়ে যাইবে।” (পৃ. ২৮)
একই নিয়মে অন্যান্য প্রতিসংজ্ঞারও প্রয়োগ হয়। “যখন স্থান জিজ্ঞাস্য হয় তখন “কোথা” কিম্বা “কোথায়” ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কোথা যাইবে, কোথায় যাইবে? অবস্থা কিম্বা প্রকার ইহার জিজ্ঞাস্য হইলে-“কেমন” শব্দের প্রয়োগ হয়। যথা কেমন আছেন? ইহার রূপান্তর নাই।” (পৃ. ২৮)
রামমোহনের বিভাজন অনুসারে কি শব্দ অব্যয় নয়, কারণ ইহার ব্যয় বা রূপান্তর আছে। শুদ্ধমাত্র অভিহিত পদ আর কর্মকারকেই ইহা একরূপ থাকে। অন্য পক্ষে “নান্ত কোন্ শব্দ”অব্যয়। কে, কি, কবে, কোথা প্রভৃতি শব্দ নান্ত কোন্ শব্দের প্রতিনিধি হয়। যেমন কে- কোন্ জন? কি- কোন্ বস্তু? কবে- কোন্ দিন, কোথা- কোন্ স্থান ইত্যাদি। কিন্তু খোদ “কোন্”শব্দটি অব্যয় পদবাচ্য। “ইহার রূপান্তর হয় না। আর বিশেষণ পদের ন্যায় ব্যবহার হয়।
“কোন্”শব্দের উচ্চারণ যখন “হলন্ত”বা “নান্ত”না হইয়া অকারান্ত বা ওকারান্ত হয়, তখন কোন জাতিবাচক শব্দের অনির্দ্ধারিত এক ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হয়, কাহাকেও নির্দিষ্ট ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হয় না। অকারান্ত বা ওকারান্ত ‘কোন’শব্দ বিশেষণের ন্যায় প্রয়োগ হইয়া থাকে; যেমন, কোন মনুষ্য ঘরে আছে? অর্থাৎ মনুষ্যের কোন এক ব্যক্তি ঘরে আছে? কোন পুস্তক পেটরাতে আছে? অর্থাৎ পুস্তকের কোন এক খান পেটরাতে আছে?” (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৮)
‘অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি জিজ্ঞাস্য হইলে, কেও [কেউ], কিম্বা কেহ, ইহার প্রয়োগ হয়, যেমন কেও ঘরে আছে, অর্থাৎ কোন্ ব্যক্তি ঘরে আছে? আর কোন শব্দ ও কেহ শব্দ যখন দ্বিরুক্তি হয় তখন প্রশ্ন অভিপ্রেত না হইয়া অনির্দ্ধারিত ব্যক্তি সকলকে বুঝায়, যেমন কোন [কোন] ব্রাহ্মণ, কোন [কোন] রাজা ইত্যাদি।’ (পৃ. ২৮, নিম্নরেখা আমরা যোগাইয়াছি)
রামমোহন তাড়াহুড়া করিয়া লিখিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি দেখাইতে পারিতেন এই প্রণালীতে ‘কেন’এবং ‘কিছু’ শব্দও নিষ্পন্ন হইয়াছে। “কেন”মানে কি কারণে, কি হেতু ইত্যাদি। আর “কিছু”শব্দেরই প্রয়োগ হয় অনির্দ্ধারিত কোন বস্তু জিজ্ঞাসাস্য হইলে, যেমন- ঘরে কিছু খাবার আছে? ইহা “কি”শব্দের রূপান্তর। একই সঙ্গে ইহার প্রয়োগ বিশেষণের ন্যায়ও বটে। বিশেষ্যের ন্যায়ও হইতে পারে, যেমন-‘কিছু হইয়াছে?’ ‘কিছু বলিবে?’ ইত্যাদি।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ১৯৮৬ সনে জন্ম লইবার পর হইতেই সংস্কার কাজে মনোযোগ দিয়া আসিতেছেন। ২০০৫ সালে তাঁহাদের বানানবিধির পঞ্চম সংস্করণ ছাড়া হইয়াছে। তাহাতে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন অর্থগত প্রয়োগ ধরিয়া কি ‘কর্মবাচক সর্বনাম’ কি ‘প্রশ্নমূলক সর্বনাম’, কি ‘বিশেষণের বিশেষণ’-সকল ক্ষেত্রেই ‘কি’বানান ‘কী’লেখা হইবে। একই সঙ্গে তাঁহারা বিধান দিয়াছেন ‘বিকল্পাত্মক বিশেষণ’ [যাহাকে কেহ কেহ ‘সমুচ্চয়ার্থক বিশেষণ’ও বলিতে পারেন] হিসাবেও ‘কী’চলিবে।[১২.১] (আকাদেমি বানান অভিধান, স. ৫, পৃ. ৫৫৪)
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন “‘কী’শব্দের করণ কারকের রূপ : কিসে, কিসে ক’রে, কী দিয়ে, কিসের দ্বারা। অধিকরণের রূপও ‘কিসে’যথা: এ লেখাটা কিসে আছে।” (বাংলাভাষা-পরিচয়, পৃ. ৯৯)
আর পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি লিখিতেছেন : “বিকল্পাত্মক বিশেষণ হিসেবেও কী ব্যবহৃত হবে: কী রাম কী শ্যাম, দুটোই সমান পাজি! এইসঙ্গে সমজাতীয় ব্যাকরণসূত্রে কীসে এবং কীসের দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে লেখা উচিত এবং তার প্রচলন বাড়ছে’।” (বিধি ১২.১)
জানি সব শিয়ালের এক রা। প্রভেদ মধ্যে মধ্যে। প্রভেদের মধ্যে ঢাকার বাংলা একাডেমি ‘বিকল্পাত্মক বিশেষণ’কে এখনও অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়া লিখিবার পক্ষে। প্রমাণ : “অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে। যেমন : তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী।” [.০১] (প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম; ৩য় সংস্করণ) ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, স. ২, পৃ. ১২২১)
প্রভুর ছলের অভাব নাই
“প্রেমনারায়ণ বিরক্ত হইয়া আপন মনের কথা আপনাআপনি বলিতে লাগিলেন-চাক্রি করা ঝক্মারি- চাকরে কুকুরে সমান- হুকুম করিলে দৌড়িতে হয়। মতে, হলা, গদার জ্বালায় চিরকালটা জ্বলে মরেছি- আমাকে খেতে দেয় নাই- শুতে দেয় নাই- আমার নামে গান বাঁধিত- সর্ব্বদা ক্ষুদে পিঁপড়ার কামড়ের মত ঠাট্টা করিত- আমাকে ত্যক্ত করিবার জন্য রাস্তার ছোঁড়াদের টুইয়ে দিত ও মধ্যে [মধ্যে] আপনারাও আমার পেছনে হাততালি দিয়া হো হো করিত। এসব সহিয়া কোন ভাল মানুষ টিকিতে পারে? ইহাতে সহজ মানুষ পাগল হয়। আমি যে কলিকাতা ছেড়ে পলাই নাই এই আমার বাহাদুরি- আমার বড় গুরুবল যে অদ্যাপিও সরকারগিরি কর্ম্মটি বজায় আছে। ছোঁড়াদের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। এখন জেলে পচে মরুক- আর যেন খালাস হয় না- কিন্তু এ কথা কেবল কথার কথা, আমি নিজেই খালাসের তদ্বিরে যাইতেছি। মনিবওয়ারি কর্ম্ম। চারা কি? মানুষকে পেটের জ্বালায় সব করিতে হয়।” -টেকচাঁদ ঠাকুর (আলালের ঘরের দুলাল, পৃ. ২৩)
বাংলা আকাদেমির দ্বিতীয় অবয়বের নাম উচ্চারণে বল প্রয়োগ বা শ্বাসের আঘাতের বিষয় হইতে পাওয়া গিয়াছে। এই যুক্তির বয়ান রাজশেখর বসু সহজেই করিয়াছিলেন।
চলন্তিকা অভিধানে রাজশেখর ‘কী’শব্দের অর্থ দিয়াছিলেন : “বেশী জোর দিতে, যথা- কী সুন্দর! তোমার কী হয়েছে?” মণীন্দ্রকুমার ঘোষ বলিয়াছিলেন, “আরও কোন কোন অভিধানে এইরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু এই ব্যাখ্যা মানিয়া লইতে পারিতেছি না।” (বাংলা বানান, পৃ. ৮০)
সত্য বলিতে উল্লেখ করিবার মত সকল বাংলা অভিধানে ইহাই আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঘোষের অভিধানে লেখেন :
‘মৈথিলী বা উত্তরবিহারী ভাষায় ‘কি’ও ‘কী’র প্রভেদ নাই। (Grierson’s Maithili Dialect, Pt. I., Grammar, 2nd edition, pp. 99-101) তার অনুকরণে প্রাচীন বাংলায়ও ‘কি’ ও ‘কী’নির্ব্বিশেষে প্রচলিত হয়।” জ্ঞানেন্দ্রমোহন আরও জ্ঞান দিয়াছেন, কী শব্দটি ‘মধ্য বাংলা সাহিত্যে অপ্রচলিত। অধুনা কোন কোন লেখক কর্ত্তৃক পুনঃপ্রচলিত।’
সুকুমার সেন প্রণীত ‘বুৎপত্তি-সিদ্ধান্ত বাংলা-কোষ’অভিধানেও ‘কী’শব্দের কোন জায়গা হয় নাই। কিন্তু ‘কি’শব্দের পাঁচ রকম অর্থ দেওয়া হইয়াছে। বলা অপ্রাসঙ্গিক নহে এই অভিধানের ইংরেজি সংস্করণ পহেলা ১৯৭১ সালে বাহির হইয়াছিল। বর্তমান সংস্করণ খোদ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি হইতে বাজারে আসিয়াছে।
‘বুৎপত্তি সিদ্ধান্ত’ অনুসারে, “কি” শব্দ প্রশ্নবাচক, অনির্দেশক সর্বনাম। ইহা শেষ বিচারে সংস্কৃত “কিম্” হইতে আসিয়াছে। বড়ু চণ্ডীদাসের প্রয়োগ এই অর্থেই : ‘কি লআঁ যাইব ঘর’।
“কি” শব্দের দ্বিতীয় প্রয়োগ প্রশ্নবাচক অব্যয়ে আকারে। সুকুমার সেন দুই দুইটি প্রয়োগ দেখাইতেছেন এই অর্থে। দুইই চর্যাপদ হইতে, ‘দুহিল দুধু কি বেন্টে যামায়’ (চর্যা ৩৩) এবং ‘ভাগ তরঙ্গ কি সোসঈ সাঅর’ (চর্যা ৪২)
“কি” শব্দের তৃতীয় প্রয়োগও অব্যয় আকারে। এই প্রয়োগের অর্থে, সুকুমার সেন যাহাকে বলেন ‘দ্বৈধ’সেই ভাবই বুঝাইতেছে। বাংলা আকাদেমির লোকেরা হয়তো বা বলিবেন ‘বিকল্পাত্মক’, কিংবা “সমুচ্চয়বোধক”। এই প্রয়োগও চর্যাপদ হইতে, “জামে কাম কি কামে জাম’। (চর্যা ২২)
কি শব্দের আরো প্রয়োগ “না” শব্দের সহিত যুক্ত হইয়া ঘটে। দুইপদ যুক্ত হইয়া একই সঙ্গে সংশয় ও প্রশ্ন দুইটাই সূচনা করে।
“কি” আরও অর্থে প্রয়োগ করা চলে। সুকুমার সেনের পাঁচ নম্বর অর্থ বুঝাইতে সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী বিভক্তি আকারে ইহার প্রয়োগ হয়। এই অর্থে ইহা সংস্কৃত “কৃত” শব্দের পরিবর্তন হইতে আসিয়াছে। উদাহরণ : ব্রজবুলি হইতে ‘চাঁদ কি চলনা’, হেমচন্দ্র হইতে, ‘অব বাপ্পকি ডুম্মুড়ি’(= বাবার জমিটুকু)।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি উচ্চারণের যুক্তি দেখাইতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা এই বাবদ ধন্যবাদ পাইতেছেন। কিন্তু শ্বাসাঘাতের যে যুক্তি তাহারা দ্বিতীয় অবয়বস্বরূপ হাজির করিয়াছেন তাহাও নিতান্ত খোঁড়া যুক্তি। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ যাহাকে প্রেতের বানান বলিয়াছিলেন তাহার পেছনের যুক্তিই নতুন মুখোশ পরিয়া হাজির হইল মাত্র। কিভাবে, দেখাইতেছি। কথায় বলে দুর্বৃত্তের ছলের অভাব নাই।
‘বাঙলা বানানবিধি’পুঁথিযোগে পরেশচন্দ্র মজুমদার যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে এই মুখোশের সেলাইরেখা দেখা যাইবে। পরেশচন্দ্র দেখাইতেছেন :
“প্রথমেই মনে রাখা দরকার, সংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব/দীর্ঘ ভেদ আছে। বাঙলাতেও আছে। কিন্তু উভয়ের গুণগত পার্থক্য যথেষ্ট। সংস্কৃতে এই গুরু-লঘু ভেদ শব্দের অর্থান্তর ঘটায়, যেমন, দিন : দীন, চির : চীর, কুল : কূল ইত্যাদি। কাজেই সংস্কৃতে হৃস্বদীর্ঘভেদ ধ্বনিমানসূচক (Phonemic)। বাঙলা শব্দের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন অবস্থানমূলক অর্থাৎ স্বরের অবস্থান অনুযায়ী এই ভেদ ঘটে; যেমন, ‘তিন, হিম, চিল’ ইত্যাদি শব্দের ই-কার উচ্চারণে দীর্ঘ, কিন্তু রিপু, ভীষণ’ইত্যাদি শব্দে ই-স্বর হ্রস্ব। লক্ষ করলে দেখা যাবে, ‘প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে স্বর রুদ্ধ (Closed), কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা মুক্ত (Open)। কিন্তু লক্ষণীয়, অবস্থান অনুযায়ী বাঙলা স্বরমাত্রার হ্রস্ব-দীর্ঘভেদ থাকলেও এর বিপর্যয় অর্থান্তর ঘটায় না। কাজই বাংলায় এই ভেদ ধ্বনিমানসূচক (Phonemic) নয়। প্রকৃতপক্ষে বাঙলার যথার্থ প্রবণতা হলো হ্রস্ব মাত্রার উচ্চারণ। উচ্চারণে এবং বানানে সমতা আনা উচিত।” (বাঙ্লা বানানবিধি, পৃ. ২৮)
পশ্চিমবঙ্গে “কি” ও “কী” তফাত উপপাদ্যের পাঁচআনি নেতা পবিত্র সরকার। তিনিও স্বীকার করিয়াছেন : “স্বরচিহ্নের মধ্যে দীর্ঘ ঈকার ও দীর্ঘ ঊকারের উচ্চারণ বাংলায় নেই। অর্থাৎ এই উচ্চারণ ফোনিমিক নয়। এর সহজ অর্থ হল, স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণভেদে অর্থ পাল্টাচ্ছে, এমন শব্দের দৃষ্টান্ত বাঙলায় নেই।” (বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃ. ৪৭) এই কারণেই বাংলা বানানের সংস্কারে মনীন্দ্রকুমার ঘোষ যাহাকে বলেন ‘হ্রস্ব-ইকার প্রবণতা’ তাহার জয় হইতেছে। ইহার কৃতিত্ব বহুলাংশে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই কথা মানিতে হইবে।
পবিত্র সরকারও দেখিয়াছেন সত্য লোকের মধ্যে স্বীকৃতিও পাইতেছে : ‘স্বরের দীর্ঘ উচ্চারণ ফোনিমিক না হওয়ার দরুন আলোচ্য শব্দগুলিকে উচ্চারণ-অনুগ করতে গিয়ে দীর্ঘ ঈকার দীর্ঘ ঊকারের জায়গায় হ্রস্ব ইকার হ্রস্ব উকার লেখা চলছে, এবং এ ধরনের প্রয়োগ ক্রমশ বেশি লোকের কাছে গৃহীত হচ্ছে।’ (বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃ. ৪৭)
এত বাক্য ব্যয় করিবার পরও পায়ে টিকা দিয়া পবিত্র সরকার পুনশ্চ যোগ করিতে ভুলিলেন না, “বাংলা উচ্চারণে ই ও ঈ-র মধ্যে কোনো তফাত নেই।” (বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, পৃ. ১৫১) জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার প্রসিদ্ধ ‘বাংলা ব্যাকরণ’ প্রবন্ধে এই মূলনীতির অবতারণাই করিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ও তীব্র ব্যঙ্গে মিশাইয়া কহিয়াছিলেন, “মাকে মা বলিয়া স্বীকার না করিয়া প্রপিতামহীকেই মা বলিতে যাওয়া দোষের হয়। সেইরূপ বাংলাকে বাংলা না বলিয়া কেবলমাত্র সংস্কৃতকেই যদি বাংলা বলিয়া গণ্য করি, তবে তাহাতে পাণ্ডিত্য প্রকাশ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় থাকে না।” (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ১১২)
পবিত্র সরকার মহাশয়ও রবীন্দ্রনাথের বৃত্তি করিয়া লিখিয়াছেন : “সংসদ বাঙ্গলা অভিধান’-এর সম্পাদক মাঝে মাঝে “বাংলা ঈ” প্রত্যয় জুড়ে শব্দ তৈরি করেছেন, যেমন “অদরকারী”। মনে রাখতে হবে এসব প্রত্যয় তৈরি হয়েছে মুখের ভাষায়, আর মুখের ভাষায় দীর্ঘ ঈ বলে কিছু নেই। সুতরাং ওটা সোজাসুজি ই-প্রত্যয়।” (বাংলা বানান-সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা পৃ. ১৫১)
এতখানি যাঁহার জ্ঞানগরিমা, এতখানি যাঁহার বিচারবুদ্ধি তিনিই পরক্ষণে লিখিতে বসিলেন, ‘তবু “কী” ‘কি’ দুভাবে লেখার জন্য রবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি দিয়েছিলেন তা আমরা সমর্থন করি। ‘কী’ কর্মপদের স্থান নেয়, কিংবা বিশেষণের বিশেষণ (intensifier) হিসাবে কাজ করে। ‘কি’ হ্যাঁ-না প্রশ্নের সূচক। দুটির ভূমিকা ও তাৎপর্য-আলাদা, ধ্বনিগত চরিত্রও আলাদা।’ (পৃ. ১৫১)
এখন আমরা কি করি? কিংকতর্ব্যবিমূঢ় ছাড়া আর কি বা হই!
সারকথা এই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি দুই নম্বর যে অবয়ব দেখাইয়াছেন তাহা আপাদমস্তক স্ববিরোধিতায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্রলোকের জন্য শিক্ষাপ্রদ হইবে না। পবিত্র সরকার মহোদয়কে বাংলা ভাষা আর কে শিখাইবে? শুদ্ধ ইংরেজি হইতে একটি দৃষ্টান্ত দিবার ধৃষ্টতা করি।
সরকার মহাশয় যদি রামমোহন রায়ের গৌড়ীয় ব্যাকরণ ভাল উল্টাইয়া দেখিতেন, খুঁজিয়া পাইতেন ‘কি’শব্দের কর্তৃ (অভিহিত) পদে যে রূপ কর্মপদেও সেই রূপ অপরিবর্তিত থাকে। ইহার রূপ অধিকরণে ‘কিসে’ এবং ‘কিসেতে’, সম্বন্ধপদে ‘কিসের’। রামমোহন রায় বাংলা ভাষায় সম্প্রদান ও অপাদান পরিণাম স্বীকার করেন নাই। (গৌড়ীয় ব্যাকরণ, পৃ. ২৮)
সুতরাং ‘কর্মপদের স্থান নেয়’এই যুক্তি চলে না। বিশেষণের বিশেষণ হইলেও রূপান্তর হইবার কোন কারণ হয় না। যুক্তি একই। যদি না আপনি ঘুরিয়া ফিরিয়া রাজশেখর বসুর প্রস্তাবে- অর্থাৎ বেশি জোর দিতে ফিরিয়া না আসেন। সেই যুক্তি তো অচল। তাহা আপনি মানিয়াছেন আর পরেশচন্দ্র মজুমদারও মানিয়াছেন। মানিয়াছেন দুই জনেই।
এক্ষণে ইংরেজিতে আসিতেছি। ইংরেজিতে অনেক ক্রিয়ার সহিত একটি প্রত্যয়ের যোগসাজশ করিয়া বিশেষ্য বা সংজ্ঞা তৈয়ার হয়। যথা- break হইতে breakage। drainage, leakage প্রভৃতিও এইরূপে গড়া হয়।
কতক আছে যাহাতে মূল ক্রিয়া শব্দে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটাইয়া যোগক্রিয়া সম্পন্ন হয়, যেমন : approval, arrival, refusal। কতকে আবার করিতে হয় না, যেমন : acceptance, appearance, performance, delivery, discovery, recovery, agreement, arrangement, employment, departure, failure। কতকে আবার করিতে হয়, যথা : collision, decision, division, education, organisation, attention, solution, closure ইত্যাদি।
কতক ইংরেজি বিশেষ্য গঠিতে হয় বিশেষণ হইতে, যথা: importance, absence, presence, ability, activity, equality, darkness, happiness, kindness, length, strength, truth ইত্যাদি।
কতক উদাহরণ পাওয়া যায় যাহাতে একই শব্দ উচ্চারণ বা বানান কোনটি না বদলাইয়াই যুগপৎ বিশেষ্যরূপে প্রয়োগ করা যায়। আবার ক্রিয়ার ভাড়ার হইতেও তাঁহাদের বিয়োগ করা চলে না। উদাহরণের তালিকা দীর্ঘ হইবে, আমি কয়েকটি দিতেছি :
aim, answer, cause, change, doubt, dream, end, fall, guess, hope, influence, interest, joke, laugh, lock, move, note, order, plan, play, quarrel, result, smile, stop, talk, trouble, walk, work ইত্যাদি।
আবার কতক শব্দ আছে যাহাদের প্রয়োগ অনুসারে উচ্চারণ বদলায় কিন্তু বানান আদৌ বদলাইবে না। যখন শব্দটি বিশেষ্য ব্যবহার্য হইবে তখন উহার শেষ ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ অঘোষ (voiceless) হইবেক। আর ক্রিয়ায় ব্যবহার্য হইলে একই ব্যঞ্জনের উচ্চারণ সঘোষ (voiced) হইবেক। যথা : abuse শব্দের উচ্চারণ বিশেষ্য অবস্থায় “এবিয়ুস” (abuse/s) আর ক্রিয়া অবস্থায় উচ্চারণ “এবিয়ুজ” (abuse/z)। একই রকম উচ্চারণভেদ হইবে house, excuse, use শব্দে।
কতক শব্দে উচ্চারণভেদে বানানও ভেদ হইয়া থাকে, যেমন advice (বিশেষ্য), advise (ক্রিয়া) ইত্যাদি। কতক শব্দে ইংল্যান্ডের ইংরেজিতে বানানভেদ হইলেও বিশেষ্যে আর ক্রিয়ার উচ্চারণে ভেদ নাই, যেমন practice (বিশেষ্য) practise (ক্রিয়া)। দুই শব্দই শেষ ব্যঞ্জনে অঘোষ থাকে।
পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি উচ্চারণে বল (stress) প্রয়োগের যুক্তি দেখাইয়াছেন। বাংলায় ‘কি’ ও ‘কী’ উচ্চারণের কোন ভেদ নাই। বলের অভিঘাতের আলাদা করার জায়গা নাই। দুইটার ফলই সোজাসুজি ‘ই’। তাঁহারা লিখিয়াছেন, ‘উচ্চারণে হ্যাঁ-না প্রশ্নের “কি”তে বল (stress) নেই। কিন্তু অন্য “কী”তে আছে। তাতেও এ দুটি পৃথক হয়ে যায়।” (বিধি ১২.২) ধরণী দ্বিধা না হইলেও দুঃখ নাই। কি ও কী দ্বিধা হইবেন।
ইংরেজি ভাষায় বিস্তর শব্দ পাওয়া যায় যাহাদের উচ্চারণকালে শ্বাসাঘাত বা বলের স্থান পরিবর্তন হয় কিন্তু বানানের পরিবর্তন হয় না। যদি বল প্রথম দলে (syllable) প্রযুক্ত হয় তখন শব্দটি বিশেষ্য পদবাচ্য হয়। আর বল দ্বিতীয় ভাগে সরিয়া যায় তো শব্দটি ক্রিয়া হইয়া যায়। উদাহরণ : accent (শ্বাসাঘাত)।
শব্দটি যদি বলি ‘The/accent in this noun falls on the first syllable’ (এই বিশেষ্যটির প্রথম ভাগে শ্বাসাঘাত হইবে) তখন শ্বাসাঘাত পড়িতেছে a অক্ষরের আগে, নির্দেশ করা স্থানে। আর যদি ক্রিয়াবিশ্বাসে বলি ‘We ac/cent this verb on the second syllable’ (এই ক্রিয়াটির দ্বিতীয় ভাগে শ্বাসাঘাত পড়িয়া থাকে) তবে শ্বাসাঘাত পড়িবে দ্বিতীয় c অক্ষরটির আগে, নির্দেশ করা জায়গায়।
এই রকম শব্দের তালিকা নাতিদীর্ঘই হইবে। যেমন : abstract, addict, ally, attribute, combine, compress, concert, conduct, conflict, conscript, contest, contract, contrast, converse, convert, convict, decrease, desert, dictate, digest, discount, discourse, entrance, /envelope (বিশেষ্য), en/velop (ক্রিয়া), escort, essay, exploit, export, extract, import, impress, incense, increase, insult, abject, perfume, permit, present, produce, progress, project, prospect, protest, rebel, record, retail, subject, survey, suspect, torment, transfer, transport ইত্যাদি। (R.A. Close, A Reference Grammar, pp. 107-08)
উচ্চারণের যুক্তিবিচার করিয়া বাংলাদেশের বাংলা একাডেমি বা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কেহই প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই “কি” শব্দের বানান ক্ষেত্র (বা প্রয়োগ) বিশেষে “কী” কেন লিখিতে হইবে। তাঁহারা জানেন রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছিলেন, ‘আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিশেরও জোর।’ তাই তাঁহারা উপরওয়ালার দ্বারে দ্বারে দস্তক ও পুরস্কার ভিক্ষা করিয়া বল সংগ্রহের পথ ধরিয়াছেন।
বাংলাদেশে সরকারের বিশেষ পুলিশ বাহিনির হেফাজতে বন্দির পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিলে মন্ত্রণালয় যে যুক্তি সচরাচর দিয়া থাকেন তাহা অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্য।
তুমি কি জাতি?
‘অনধিকার চর্চায় অব্যবসায়ীর যে বিপদ ঘটে আমারও তাই ঘটিয়াছে।’
-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৩২)
‘ভাষার স্বরূপবিচারে একদেশদর্শী সংস্কর্তাদের অভিলাষও যথার্থ দিগ্দর্শনের কাজ করে না। ভাষার সৃষ্টিশীল প্রধান লেখকগণের উৎকৃষ্ট রচনারীতির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেই সেই ভাষা-প্রবাহের মৌল প্রবণতাসমূহ চিহ্নিত করতে হবে, তার ক্রমবিবর্তনের স্বকীয় ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করতে হবে।’
- মুনীর চৌধুরী, (বাংলা গদ্যরীতি, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩)
এই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি কি তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত আদালত পর্যন্ত গড়াইবে? গড়াইলে গড়াইবে। কিন্তু বিচার করেন কে? আমরা কমলাকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়কে বিচারকর্তা মানিতে প্রস্তুত আছি। কারণ বাংলাদেশের উচ্চ-আদালত বাংলা ভাষার সমজদার নহেন। তাঁহারা এই মামলা শুনিবেন না।
খোসনবীস জুনিয়ার প্রণীত বিবরণীতে দেখা যাইতেছে ওই আফিঙ্গখোর কমলাকান্ত মহাশয় এতদিনে আদালতপাড়ায় হাজির আছেন। তিনি ফরিয়াদি নহেন। চুরিও করেন নাই। দোষের মধ্যে এক আফিঙ্গ। তিনি অন্তত সাক্ষী তো হইবেন।
‘এজলাসে, প্রথামত মাচানের উপর হাকিম বিরাজ করিতেছেন। হাকিমটি একজন দেশী ধর্ম্মাবতার- পদে ও গৌরবে ডিপুটি। কমলাকান্ত আসামী নহে- সাক্ষী। মোকদ্দমা গরুচুরি। ফরিয়াদী সেই প্রসন্ন গোয়ালিনী।
কমলাকান্তকে সাক্ষীর কাটারায় পুরিয়া দিল। তখন কমলাকান্ত মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। চাপরাশী ধমকাইল-“হাস কেন?”
কমলাকান্ত যোড়হাত করিয়া বলিল, “বাবা, কার ক্ষেতে ধান খেয়েছি যে, আমাকে এর ভিতর পুরিলে?”
চাপরাশী মহাশয় কথাটা বুঝিলেন না। দাঁড়ি ঘুরাইয়া বলিলেন, “তামাসার জায়গা এ নয়- হলফ পড়।”
কমলাকান্ত বলিল, “পড়াও না বাপু।”
একজন মুহুরি তখন হলফ পড়াইতে আরম্ভ করিল। বলিল, “বল, আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া ...”।
কমলাকান্ত। (সবিস্ময়ে) কি বলিব?
মুহুরি। শুনতে পাও না-“পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে!”
কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে! কি সর্ব্বনাশ!
হাকিম দেখিলেন, সাক্ষীটা কি একটা গণ্ডগোল বাধাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “সর্ব্বনাশ কি?”
কমলা। পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনেছি- এ কথাটা বলতে হবে?”
হাকিম। ক্ষতি কি? হলফের ফারমই এই।
কমলা। হুজুর সুবিচারক বটে। কিন্তু একটা কথা বলি কি, সাক্ষ্য দিতে দিতে দুই একটা ছোট রকম মিথ্যা বলি, না হয় বলিলাম- কিন্তু গোড়াতেই একটা বড় মিথ্যা বলিয়া আরম্ভ করিব, সেটা কি ভাল?
হাকিম। এর আর মিথ্যা কি?
কমলাকান্ত মনে মনে বলিল, “তত বুদ্ধি থাকিলে তোমার কি এ পদবৃদ্ধি হইত?” প্রকাশ্যে বলিল, “ধর্ম্মাবতার, আমার একটু একটু বোধ হইতেছে কি যে, পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। আমার চোখের দোষই হউক আর যাই হউক, কখনও ত এ পর্য্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চশমা নাকে দিয়া তাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন- কিন্তু আমি যখন তাঁহাকে এ ঘরের ভিতর প্রত্যক্ষ পাইতেছি না- তখন কেমন করিয়া বলি- আমি পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ জেনে-”
আমি এক্ষণে কিছু অংশ ছাড়িয়া দিতেছি। উকিল সাহেব চটিলেন বটে তবে হাজার হোক মোয়াক্কেলের স্বার্থ দেখিতে হয়। সাক্ষীকে মনে করাইয়া দিলেন, ‘এখানে আইনের মতে চলিতে মন স্থির করুন।’অর্থাৎ মিথ্যা বলুন। হাকিমের হস্তক্ষেপে খানিক পর আবার জেরা শুরু হইল।
কমলাকান্ত তখন সেলাম করিয়া বলিল, “বহুৎ খুব।” উকীল তখন জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন, “তোমার নাম কি?”
কমলা। শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তী।
উকীল। তোমার বাপের নাম কি?
কমলা। জোবানবন্দীর আভ্যুদয়িক আছে না কি?
উকীল গরম হইলেন, বলিলেন, “হুজুর! এসব Contempt of Court! হুজুর, উকীলের দুর্দ্দশা দেখিয়া নিতান্ত অসন্তুষ্ট নন- বলিলেন, “আপনারই সাক্ষী।” সুতরাং উকীল আবার কমলাকান্তের দিকে ফিরিলেন, বলিলেন, “বল। বলিতে হইবে।”
কমলাকান্ত পিতার নাম বলিল। উকীল তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জাতি?”
কমলা। আমি কি একটা জাতি?
উকীল। তুমি কোন্ জাতীয়।
কমলা। হিন্দু জাতীয়।
উকীল। আঃ! কোন্ বর্ণ?
কমলা। ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ।
উকীল। দূর হোক ছাই। এমন সাক্ষীও আনে! বলি তোমার জাত আছে?
কমলা। মারে কে?
হাকিম দেখিলেন, উকীলের কথায় কাজ হইবে না। বলিলেন, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, হিন্দুর নানা প্রকার জাতি আছে জান ত- তুমি তার কোন্ জাতির ভিতর?
কমলা। ধর্ম্মাবতার! এ উকীলেরই ধৃষ্টতা। দেখিতেছেন, আমার গলায় যজ্ঞোপবীত, নাম বলিয়াছি চক্রবর্ত্তী- ইহাতেও যে উকীল বুঝেন নাই যে, আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমি কি প্রকারে জানিব?
হাকিম লিখিলেন, “জাতি ব্রাহ্মণ।” তখন উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার বয়স কত?”
এজলাসে একটা ক্লক ছিল- তাহার পানে চাহিয়া হিসাব করিয়া কমলাকান্ত বলিল, “আমার বয়স একান্ন বৎসর, দুই মাস তের দিন, চারি ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট-”
আবার উকিল সাহেবের উষ্মা হইল। আমি খানিক লাফ দিয়া সামনে যাইতেছি। জেরা চলিতেছে।
উকীল। এখন আছ কোথা?
কমলা। কেন এই আদালতে।
উকীল। কাল ছিলে কোথা?
কমলা। একখানা দোকানে।
হাকিম বলিলেন, ‘আর বকাবকিতে কাজ নাই- আমি লিখিয়া লইতেছি, নিবাস নাই। তারপর?’
উকীল। তোমার পেশা কি?
কমলা। আমার আবার পেশা কি? আমি কি উকীল না বেশ্যা যে, আমার পেশা আছে?
উকীল। বলি, খাও কি করিয়া?
কমলা। ভাতের সঙ্গে ডাল মাখিয়া, দক্ষিণ হস্তে গ্রাস তুলিয়া, মুখে পুরিয়া গলাধঃকরণ করি। (বঙ্কিম রচনাবলী, খণ্ড ২, পৃ. ৯০-৯২)
বস্তুত শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীকে জেরা করা শামলা গায়ের আমলা উকীলের কর্ম্ম নহে। ভাগ্যের মধ্যে বানান সংস্কর্তা আমলারা কি পূর্বে কি পশ্চিমে কমলার মতো সাক্ষীর পাল্লায় এখনও পড়েন নাই। তাই তাঁহারা ধরাকে সরাই ভাবিতেছেন।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দুই জনকেই উদীয়মান শক্তিরূপে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। হরপ্রসাদের সাক্ষ্য অনুসারে তাঁহারা উভয়েই বঙ্কিমের প্রতিভার অনতিক্রমনীয় প্রভাবের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। ৮০ বছর আগের রবীন্দ্র সংবর্ধনা বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন, “বঙ্কিমচন্দ্রের আশীর্বাদ রবীন্দ্রনাথের উপর গভীর ফলপ্রসূ হইয়াছিল, তাঁহার আবির্ভাব একটি যুগদৃশ্যের অবতারণা করিয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথ আজও ক্রমশঃ উর্দ্ধলোকে আরোহণ করিতেছেন।’ আমরা যোগ করিব, আজও এই আরোহণ অব্যাহতই আছে।
সামান্য ‘কি’ শব্দের বানান লইয়া তিনি যে অসামান্য জিদ করিয়াছিলেন, তাহা অবিস্মরণীয়। ভুলিলে চলিবে না রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই বাংলা বানানে হ্রস্ব ই-কারের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে কর্ণধারের ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তাঁহার মনোঃপূত কর্ণধার সুনীতিকুমার করেন নাই। ‘কি’ বানান দীর্ঘ ঈ-কারযোগে লিখিবার জেদাজেদিতে তাঁহার এই কীর্তি খানিক ম্লান হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবে কীর্তিনাশা হয় নাই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস কালের যাত্রার ধ্বনি এই জেদ ভুলিতে আমাদের সহায় হইবে।
কোন মহান স্রষ্টার কীর্তি তাহার ছোট কিছু জেদের কাছে কিছুতেই ম্লান হইতে পারে না। ঢাকা ও কলিকাতার দুই বাংলা অনুষ্ঠান যাহা করিতেছেন তাহাতে রবীন্দ্রনাথের গৌরব বাড়িতেছে কি?
বাংলা কি শব্দের বানান বদলাইয়া অর্থের তফাত সৃষ্টির চেষ্টা যে চিন্তার উপর দাঁড়াইয়াছে সেই চিন্তা অসার। এই অসারতা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি কিছু পরিমাণে উপলব্ধি করিয়াছেন। ১৯৯৭ সালে প্রথম প্রকাশিত ও পরে পরিমার্জিত সংস্করণের পাঠ অনুযায়ী দেখিতেছি আকাদেমির বানানবিধিতে একটি প্রস্তাব ছিল এই উপলব্ধির সাক্ষী: ‘অতৎসম শব্দে হ্রস্ব-ইকার আর দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে বিশেষ্য বিশেষণরূপের স্বাতন্ত্র্য দেখানোর দরকার নেই। অর্থাৎ আমার খুশি/আমি খুশী তৈরি করা/তৈরী বাড়ি এ রকম কোনো প্রভেদ করা নিষ্প্রয়োজন। এসব ক্ষেত্রে সর্বত্রই হ্রস্ব ই-কারের প্রয়োগ চলুক।” [বানানবিধি ৭.২০; মাহবুবুল হক, বাংলা বানানের নিয়ম, পৃ. ১৭৩-৭৪]
বানানবিধি ৫ম সংস্করণ হইতে ইহা তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। তবে ইহাতে ঐ জাতীয় প্রভেদের অনুমোদন করা হইয়াছে বলিয়া ভুল করিবার সম্ভাবনা নাই। কালের অবধি নাই, পৃথিবীও বিপুলা কম নহেন।
ঢাকার বাংলা একাডেমী এই প্রশ্নে কিছু না লিখিলেও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) গৃহীত বাংলা বানানরীতিতে (১৯৮৮) এই ভুল চিন্তার উৎস কোথায় তাহা আজও দেখা যাইতেছে। বোর্ডের ১০ নং সুপারিশে বলা হইয়াছিল, “অর্থভেদ বোঝাবার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রস্ব ও দীর্ঘ স্বর ব্যবহার করা হবে। যেমন, কি (অব্যয়), কী (সর্বনাম); তৈরি (ক্রিয়া), তৈরী (বিশেষণ); নিচ (নিু অর্থে) নীচ (হীন অর্থে); কুল (বংশ অর্থে), কূল (তীর অর্থে)।” (আনিসুজ্জামান, পাঠ্যপুস্তকের বানান, পৃ. ১০৬; শফিউল আলম, প্রসঙ্গ: ভাষা বানান শিক্ষা, পৃ. ৭৪)
আনিসুজ্জামান, মাহবুবুল হক প্রভৃতি লেখকের বই পড়িয়া মনে হইতেছে ইঁহারা এখনও সেই অর্থভেদ উপপাদ্যের নিচেই মুখ থুবড়াইয়া আছেন। (আনিসুজ্জামান, পাঠ্যপুস্তকের বানান, পৃ. ৩৩-৩৭; মাহবুবুল হক, বাংলা বানানের নিয়ম, পৃ. ১৪৩-১৪৪)
এই অসার যুক্তি বা জেদের প্রকোপে রবীন্দ্রনাথও একদা “নীচ” ও “নিচ” শব্দে ভেদ করিতে তাগাদা দিয়াছিলেন। নীতিশাস্ত্রের বিচারে কেহ মন্দ বিবেচিত হইলে দীর্ঘ ঈকারযোগে “নীচ” আর পদার্থশাস্ত্রের অর্থে কেহ নিম্নে পতিত হইলে “নিচ” হইবেন। ইহাই ছিল ঠাকুরের ধারণা। (বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৯০) এই ধারণার সমাধি বহু আগেই হওয়া উচিত ছিল। বাংলা ভাষায় ইকারের প্রবণতা অনুসারে উভয় অর্থেই শব্দটির বানান “নিচ” হইতে পারে। সংস্কৃত বাদিপক্ষের বিচারে হয়তো উভয় অর্থেই শব্দটি “নীচ”ই ছিল। (মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাংলা বানান, পৃ. ৭৬-৭৮) তাহাতে কিছু আসে যায় না। (দিনেন ভট্টাচার্য, বানানের রবীন্দ্রনাথ, পৃ. ৬০-৬১)
এইখানে আমাদের স্থলাভাব হইয়াছে। তাই মাত্র সংক্ষেপে, ইঙ্গিতে লিখিতেছি। যে বানানেই লিখিবেন না কেন, বাংলায় নীতিশাস্ত্র ও পদার্থশাস্ত্র দুই শাস্ত্রেই এক বানানে “নিচ” কথাটা লেখা যাইবে। কারণ “নিচ” শব্দের যথার্থ অর্থ ভূমিতে “নিম্নস্থল” নৈতিক অর্থে “নিম্নমর্যাদা” তাহার ব্যঞ্জনা মাত্র। দুর্ভাগ্যের মধ্যে, রবীন্দ্রনাথ ইহা ধরিতেই পারেন নাই। তাই তাঁহার জেদাজেদি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বড় কবি সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এক ধরনের বাক্যভ্রংশ বা এফেসিয়া (aphasia) হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইহা কুলসঞ্চারিরোগ কিনা জানি না। (‘যে রোগ পিতামাতা হইতে পুত্রপৌত্রে যায়’ তাহাকে আয়ুর্বেদে “সঞ্চারিরোগ” বলে।’ -বিজয়চন্দ্র মজুমদার।) অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্মৃতিভ্রংশ’ রোগটা ধরনে ছিল রোমান এয়াকবসন কথিত সামঞ্জস্য-বৈকল্য (similarity disorder) বা ব্যঞ্জনালোপ ব্যাধির মতন। ঢাকা ও কলিকাতার সরকারি পণ্ডিতদের মাথায় তাহা কুলসঞ্চারি (hereditary) বিমারস্বরূপ বর্তাইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। (R. Jakobson, ‘Two Aspects,’ pp. 54-82)
ইহাদের উদ্দেশে আমার আজিকার শেষ আবেদন, ভাবিয়া দেখুন। স্বয়ং কবিরই যেখানে চিকিৎসা দরকার সেখানে আপনারা রোগ নির্ণয়ই করেন নাই। উপরন্তু গোটা বাংলা ভাষাকেই রোগদোষে দুষিত করিতেছেন। কবি যদি কোন বিষয় বুঝিতে না পারিয়াও থাকেন আমাদের কি উচিত হইবে তাঁহার এই অগৌরবের দিকে সারাক্ষণ তাক লাগাইয়া চাহিয়া থাকা? কবিকে সম্মান জানাইবার ইহাই কি শ্রেষ্ঠ পন্থা?
যে মানুষের একটি চোখ নষ্ট হইয়াছে তাহাকে কানা বলে কেন? চোখের ব্যবহার সীমারেখায় পৌঁছিলে কানের ব্যবহার বাড়িয়া যায়। এই লোকসংস্কার সত্য হউক আর মিথ্যাই হউক এক চোখা লোককে কানা বলাই তাই রীতি। আপনারাও কি কানা হইলেন না? শুদ্ধ কানকথায় কান দিলেন, চোখের দেখা দেখিলেন না?
পণ্ডিত কৃষ্ণপদ গোস্বামীও দুর্ভাগ্যক্রমে মনে করিতেন অর্থভেদের জন্য “কি” ও “কী” আলাদা করা যাইতে পারে। তবে তিনিও খেয়াল করেন নাই শব্দের ব্যঞ্জনা আসে তাহার বানান হইতে নহে। ব্যবহার হইতে। ব্যবহারই ব্যঞ্জনা নহে, কিন্তু ব্যবহারেই ব্যঞ্জনা।
যদি না হইত তবে গোস্বামী নিজেই কি লিখিতেন এই কথাগুলি? ‘বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস’ গ্রন্থে তিনি লিখিয়াছেন, “অকল্যাণকর বা কুৎসিত অর্থবাচক কোন শব্দকে ভদ্রভাবে প্রকাশ করিবার সময় অনেক সময় সুভাষণ অলঙ্কারের আশ্রয় নেওয়া হয়। চাউল বা ভাত না থাকিলে স্ত্রীলোকেরা ‘চাল বাড়ন্ত’, ‘ভাত বাড়ন্ত’ ইত্যাদি বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকে। উত্তর ভারতে পাচক ব্রাহ্মণকে বলা হয় মহারাজ, বাংলায় বলা হয় ঠাকুর।” (পৃ. ১০৮)
পাচক শব্দের উৎপত্তি অনুসারে জাতি যৌগিক। পচ্ ধাতুর সহিত অক প্রত্যয় লাগাইয়া বাংলায় পাচক হইয়াছে। কিন্তু ‘পচেগা’মানে হিন্দিতে ‘পরিপাক হইবে’ বুঝাইলেও বাংলায় বুঝাইতেছে ‘পচিয়া যাইবে’। এক ধাতু হইতে বহু শব্দ ও বহু অর্থ হয়। ‘অক’প্রত্যয়ের অর্থ কর্তৃত্ব ধরিলে পাচক মানে পচনের উপর যাহার কর্তৃত্ব আছে বোঝায়। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ছাত্র। তিনি লিখিয়াছেন, অনেক সময় বুৎপত্তি ভিন্ন হইলেও ধ্বনি বিচারের দিক দিয়া এক ভাষার কথা অন্য ভাষায় মিলিয়া যাইতেছে দেখা যায়, কোন রূপভেদ হয় না ; ‘কিন্তু ভাষাভেদে অর্থভেদ ঘটে’। (বাংলাভাষা, পৃ. ২৯৪-৯৫)
সংস্কৃতে তীর অর্থ কূল বা পাড়, ফারসিতে তীর অর্থ শর বা বাণ। বানান বদলাইয়া কূল পাইবেন না। বাংলায় দুই তীরই সমান তীরন্দাজ। এক তীর হইতে তীর ছুড়িয়া অন্য তীরে নিতুই যাইতে পারেন।
রবীন্দ্রনাথ প্রাজ্ঞ বয়সে (পৌষ ১৩২৬) একবার স্বীকার করিয়াছিলেন, ‘অনধিকার চর্চায় অব্যসায়ীর যে বিপদ ঘটে আমারও তাই ঘটিয়াছে।’(বাংলা শব্দতত্ত্ব, পৃ. ২৩২)
যাহার বিপদ ঘটে এবং যিনি সেই বিপদ ঘটিয়াছে বলিয়া বয়ান করেন- দুইজন কি একই ব্যক্তি। যদি তাহারা দুইজনই হইয়া থাকেন, তাহাদের কি কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয়?
দোহাই
১. আকাদেমি বানান উপসমিতি (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ) সম্পাদিত, আকাদেমি বানান অভিধান, ৫ম সংস্করণ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৫)।
২. আনিসুজ্জামান, পাঠ্য বইয়ের বানান, সংশোধিত ও পরিমার্জিত (জিয়াউল হাসান) সংস্করণ, (ঢাকা : জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০০৫)।
৩. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর রচনাবলী, ২য় খণ্ড,তীর্থপতি দত্ত সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা : তুলি-কলম, ২০০১)।
৪. কৃষ্ণপদ গোস্বামী, বাংলা ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস, ২য় (পরিবর্ধিত) সংস্করণ, (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০০১)।
৫. চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ : আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ মার্চ ১৯২২-২১ মার্চ ১৯৩২, ১ম খণ্ড (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩)।
৬. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ২য় (পরিবর্ধিত) সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯)।
৭. টেকচাঁদ ঠাকুর, আলালের ঘরের দুলাল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ৮ম (পরিষৎ) সংস্করণ (কলিকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪০৫)।
৮. দিনেন ভট্টাচার্য, বানানের রবীন্দ্রনাথ (কলকাতা : ডি.এম. লাইব্রেরি, ১৪১০)।
৯. নির্মল দাশ, বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও তার ক্রমবিকাশ (কলকাতা : রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭)।
১০. নেপাল মজুমদার সম্পাদিত, বানান বিতর্ক, ৩য় (পরিবর্ধিত, পবিত্র সরকার) সংস্করণ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৭)।
১১. নৃপেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, ভাষাতত্ত্বের ইতিহাস ও অন্যান্য প্রবন্ধ, ২য় (সংশোধিত ও পরিবর্ধিত) সংস্করণ, (কলকাতা : নব চলন্তিকা, ২০০১)।
১২. পবিত্র সরকার, বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা, (কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৮৭)।
১৩. পরেশচন্দ্র মজুমদার, বাঙ্লা বানানবিধি, পরিবর্ধিত সংস্করণ (কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ১৯৯৮)।
১৪. পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য, বাংলাভাষা, ৩য় সংস্করণ (কলকাতা : জিজ্ঞাসা এজেন্সিস, ১৯৯৮)।
১৫. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, ১৪শ মুদ্রণ (কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৪০৯)।
১৬. বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি, ২য় মুদ্রণ (কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৪)।
১৭. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, বাংলা বানান, ৪র্থ (দে’জ) সংস্করণ (কলকাতা : দে’জ পাবলিশিং, ১৪০৯)।
১৮. মাহবুবুল হক, বাংলা বানানের নিয়ম, ৭ম মুদ্রণ (ঢাকা : সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮)।
১৯. মিতালী ভট্টাচার্য, বাংলা বানানচিন্তার বিবর্তন (কলকাতা : পারুল প্রকাশনী, ২০০৭)।
২০. মুনীর চৌধুরী, বাঙ্লা গদ্যরীতি, ২য় সংস্করণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৮৩)।
২১. মুহম্মদ এনামুল হক প্রমুখ সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, পরিমার্জিত সংস্করণ (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৪০৭)।
২২. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, ভাষা ও সাহিত্য, ৩য় (সংশোধিত) সংস্করণ (ঢাকা : প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরি, ১৯৪৯)।
২৩. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা ব্যাকরণ, নতুন সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ (ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৮)।
২৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলাভাষা পরিচয়, পুনর্মুদ্রণ (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৭৫)।
২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলা শব্দতত্ত্ব, ৩য় (স্বতন্ত্র) সংস্করণ (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৩৯১)।
২৬. রমাপ্রসাদ চন্দ, ‘কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম’, বসুমতী, ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্ত্তিক, ১৩৪৪।
২৭. রামমোহন রায়, ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’, রামমোহন গ্রন্থাবলী, ৭ম খণ্ড, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত, ৩য় সংস্করণ (কলিকাতা : বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৮০)।
২৮. সলিমুল্লাহ খান, ‘বাংলা বানানের যম ও নিয়ম’, নতুনধারা, ১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭।
২৯. সুকুমার সেন, বুৎপত্তি-সিদ্ধার্থ বাংলা-কোষ (কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩)।
৩০. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মনীষী স্মরণে, দ্বিতীয় প্রকাশ (কলিকাতা : জিজ্ঞাসা এজেন্সিস, ১৩৯৬)।
৩১. শফিউল আলম, প্রসঙ্গ : ভাষা বানান শিক্ষা (ঢাকা : কাকলী প্রকাশনী, ২০০২)।
৩২. হরনাথ ঘোষ ও সুকুমার সেন, বাঙ্লা ভাষার ব্যাকরণ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ (কলিকাতা : ভিক্টোরিয়া বুক ডিপো, ১৩৫৬)।
৩৩. R.A. Close, A Reference Grammar for Students of English, 15th ed. (Burnt Mill, Harlow: Longman, 1990).
৩৪. G. A. Grierson, Maithili Dialect, Part 1, Grammar, 2nd ed., cited in জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৯)।
৩৫. Roman Jakobson, ‘Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances,’ in R. Jakobson and M. Halle, Fundamentals of Language, pp. 54-82 (Leiden: Mouton, 1956).
প্রথম প্রকাশ : শিল্পসাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা ‘নতুনধারা’, ৮ম সংখ্যা, ১ আষাঢ় ১৪১৭/১৫ জুন ২০১০, সম্পাদক : নাঈমুল ইসলাম খান।






















 সলিমুল্লাহ খান
সলিমুল্লাহ খান















