গল্প
শ্যাওলা
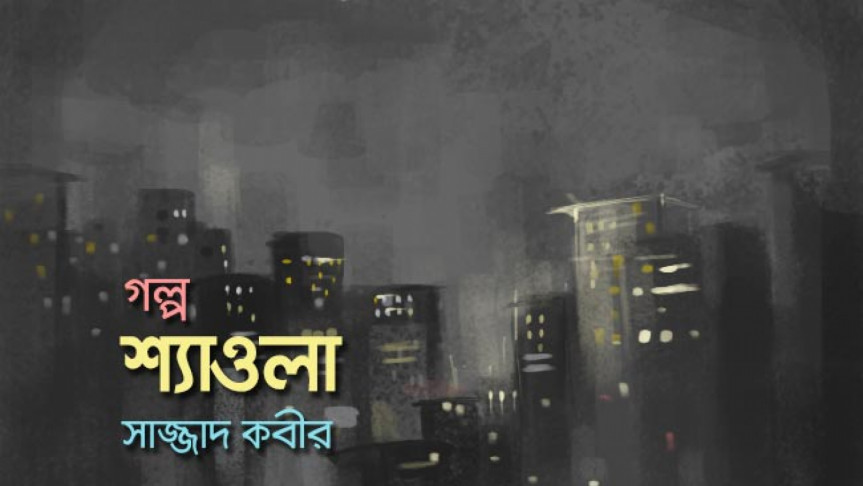
সুউচ্চ কোনো ভবনের মাথায় দাঁড়িয়ে যদি চোখ মেলে দেওয়া যায়, দেখা যাবে বিস্তীর্ণ শহরের কলেবর ছুঁয়েছে দিগন্ত রেখা। দিনের আলোয় বহুদূর চোখ চলে যায়, যেখানটা প্রায় ধোঁয়া ধোঁয়া হয়ে একাকার হয়ে গেছে সেই পর্যন্তও। তারও বাইরে যেখানটা প্রায় দেখা যায় না, সংকুচিত চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির পর্দায় ভেসে ওঠে কয়েকটা ঘরবাড়ি। ঘরবাড়ি খুব ছাড়া ছাড়া সেখানে, একটা থেকে আরেকটা যেন গা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে যারা বাস করে, তারাও কাজ করে এই শহরের কোনো না কোনো জায়গায়। সকালের সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে তারাও বের হয় কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে। সারা দিন চলে কর্মযজ্ঞ, আর ফাঁকে একটু বিশ্রাম।
একসময় আঁধার নামতে থাকে, নামতে থাকে দালানের গা বেয়ে, গাছের পাতা ছুঁয়ে। সমস্ত শহরের অবয়বে, মাটিতে আর ড্রেনের নোংরা জলে। সেইসঙ্গে নেমে আসে শব্দবিহীন সময়ের সারি। ঝুপসি অন্ধকারে ছাওয়া শহরটাকে ঘিরে ফেলে নিঃস্তব্ধতা। রাত নেমে এলে জ্বলে উঠতে থাকে একে একে বাতিগুলো। রাস্তা, পার্ক, উঁচু দালান, দোকান, এমনকি ছোট টং চায়ের দোকানটা পর্যন্ত ঝিকমিকিয়ে ওঠে আলোয়। সন্ধ্যায় ঘরে ফেরে কাকেরা, আর নিত্য অফিস যাত্রী, শ্রমিক, মজুর সবাই। কিন্তু সবাই কি আর ফেরে! ফেরে না। যারা কূলহারা নাবিকের মতো খাবি খাচ্ছে জীবন নদীতে, তারা একটুখানি দিশা পাওয়ার জন্য বাড়তি ঘাম ঝরিয়ে যাচ্ছে তখনো। রাত বাড়তে থাকে, সেইসঙ্গে কমতে থাকে পথচারী। যখন রাত আরো গভীর, তখন একে একে নিভে আসে শহরের বাতি। ঘরগুলোর আলো নিভে যায় আর নিচু হয়ে আসে তার বাসিন্দাদের স্বর।
শনশন, শনশন বাতাসের শব্দ তখন কানে বেজে ওঠে। সেই বাতাস যেটা এখান থেকে ওখানে নিমেষে বয়ে যায়। শহরের কেন্দ্র থেকে যে মুহূর্তে চলে যায় শেষ প্রান্তে। যেখানে একটা ঘরের আলো তখনো নেভেনি। বাইরের কার্নিশের তলায় জ্বলতে থাকা কম পাওয়ারের বাল্বটার চারপাশে পোকারা খেলা করতে থাকে ঘুরে ঘুরে। আর তার ঠিক নিচে জানালার গরাদ ধরে আছে কোমল দুটি হাত। কাচের চুড়ির রিনিঝিনি রিনিঝিনি বেজে ওঠে মাঝেমধ্যে। হাত নড়েচড়ে ওঠে, নড়েচড়ে ওঠে হাতের পেছনে শরীরটা, কিন্তু জানালা ছেড়ে যায় না। সে তার চোখ মেলে দিয়েছে সামনের পায়ে চলা পথটা ধরে বড় রাস্তা পর্যন্ত। যার অপেক্ষায় সে দাঁড়িয়ে আছে, সেও ওই দিশাহারা নাবিকদের একজন। একসময় অপেক্ষার শেষ হয়, সামান্য নুয়ে পড়া শরীরটা দেখা যায়। দ্রুত পায়ে রিনিঝিনি আওয়াজ তুলে ভেতরে ঢুকে যায় ফিরোজা। চুলোটা জ্বালিয়ে তাতে তরকারির হাঁড়িটা বসিয়ে দিয়ে একনজর চোখ বোলায় কলের কাছে বালতিতে পানিটা ঠিকঠাক আছে কি না। একটু আগেই সে চাপকল চেপে চেপে তুলে রেখেছে। ততক্ষণে বাইরের পদশব্দ প্রায় বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছে।
রিনিঝিনি শব্দ এবার ছুটে যায় পাঁচিলের দরজার কাছে। দরজা খুলে দিতে একটু পরে এসে ঢোকে স্ট্রাইপের একটা হাফহাতা শার্ট আর কালো প্যান্ট পরা বত্রিশ-তেত্রিশ বছরের এক পুরুষ। ঢোকার জায়গা করে দিয়ে এক পাশে সরে যায় ফিরোজা, ‘এত দেরি হলো যে?’ ‘আর বলো না, সেই পুরোনো ঝামেলা। মমীনউদ্দিন হাজিরা খাতায় ঝামেলা করে রেখেছে। কোথায় তাড়াতাড়ি বেতন নিয়ে ঘরে ফিরব, তা না।’ ‘শুধু তোমারটাই করেছে?’ ‘না সোবাহান সাহেব, কেরামত সাহেব আরো দু-একজন ছিল আমার সাথে।’ বলতে বলতে ঘরে ঢুকে পড়ে সিরাজুল। তার পর সেখান থেকেই বলে, ‘লুঙ্গিটা কোথায়?’ দ্রুত ঘরে ঢুকে বের করে দেয় ফিরোজা। লুঙ্গি পরতে পরতে পুরোনো কথার খেই ধরে বলে সিরাজুল, ‘অনেকের বেতনই আটকালো, কিন্তু ছাড়া পেয়ে গেল সবাই। একমাত্র সোবাহান সাহেব, সেই যে ময়মনসিংহ বাড়ি, আমার জন্য এতক্ষণ বসে ছিল। বাকিরা যে যার পাওনা আদায় করে বের হয়ে গেছে তাড়াতাড়ি।’ ফিরোজা বের হয়ে যেতে যেতে বলে, ‘সোবহান সাহেব থাকল কী মনে করে?’ ‘ওই আর কী,’ চেঁচিয়ে বলতে থাকে সিরাজুল, ‘থাকে না কিছু লোক ভালো মানুষ গোছের, ওমনই। বলে, আরে ভাই কপাল দোষে বাড়ির জমি-জিরাত সব হারাইছি। তাই বলেই না এখানে বেশি পরিশ্রম করি, একটু বাড়তি সুখের জন্য। আমাদের টাকাপয়সা নিয়ে ঘাপলা করলে মেজাজ ঠিক রাখা যায়? সোবাহান সাহেবরা অনেক কথা বলে, আমি চুপ করে থাকি।’ রান্নাঘর থেকে উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করে ফিরোজা, ‘কেন, কিছু বলো না কেন?’ লুঙ্গিটা পরে প্যান্ট আর শার্টটা হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে বের হয়ে আসে সিরাজুল।
ফিরোজার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যায় কলতলায়। হাত-মুখ ধোয়ার শব্দ শোনা যায়, বালতি থেকে টিনের মগে করে পানি তোলার আওয়াজ, গড়গড়ার আওয়াজ। এর সঙ্গে রান্নাঘর থেকে ভেসে আসা হাঁড়ি বা থালাবাসনের শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। কেউ কোনো কথা বলছে না। বারান্দায় ঝোলানো গামছা নিয়ে হাত-মুখ মুছতে মুছতে সিরাজুল জিজ্ঞেস করে, ‘অপু কখন ঘুমাল?’ ‘কী জানি, একটু আগেও তো জেগে ছিল। বাবুর সঙ্গে খেলতে খেলতে কখন ঘুমিয়ে গেছে।’ বাবু, তাদের দেড় বছরের শিশুটি, যার নাম এখনো ঠিক হয়নি। এ মূহূর্তে ঘুমিয়ে আছে, তা না হলে চিৎকার করে বেশ কয়েকবার তার উপস্থিতি জানান দিত। সিরাজুল ঘরের দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে শিশুকন্যা আর তার পাশে ঘুমন্ত পুত্রকে দেখে নেয়। তারপর এসে বসে রান্নাঘরে বিছানো পাটিতে। ভাতের থালা আর তরকারির বাটি সাজানো সামনে। হাতে একটু পানি দিয়ে খাওয়া শুরু করে সিরাজুল। ফিরোজাও খেতে শুরু করে।
তারপর পুরোনো কথার খেই ধরে জিজ্ঞেস করে, ‘বললে নাতো...’ ‘কী?’ ‘সোবাহান সাহেবরা বলে, কিন্তু তুমি কিছু বলো না কেন?’ সিরাজুল কথার উত্তর না দিয়ে কয়েক গ্রাস ভাত মুখে তোলে। ফিরোজা খেতে খেতে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করে। সিরাজুলই মুখ খোলে, ‘কেমন যেন সংকোচ...’ ‘নিজের টাকা চাবে, তাতে সংকোচের কী? তুমি তো আর চুরি করছ না।’ ‘না তা না... আসলে ঐ মমীনউদ্দিন লোকটা আড়ালে আবডালে বলে বেড়ায়—ব্যাটা ঘটিরা আইসা এই দ্যাশডারে লুইটা নিল।’ ফিরোজা ভাত খাওয়া থামিয়ে নির্ণিমেষ চেয়ে থাকে সিরাজুলের দিকে। আসলে ঠিক সিরাজুলের দিকেও না, ক্রমে ছোট হয়ে আসা চোখের মণি দুটো তখন দেখছে অন্য কিছু। মনে পড়ে তার গ্রামের বাড়ির কথা। আতাগাছটার পাশ দিয়ে যাতায়াতের পথ ছিল। মাটির পাঁচিল ঘেরা অনেকটা জায়গা নিয়ে তাদের ভিটেবাড়ি। মাঝখানের উঠোন ঘিরে তিন দিকে টিনের চৌচালা। পাঁচিলের দরজা বরাবর যে ঘরটা, সেটার ডানপাশে রান্নাঘর। তিন ঘরের একটাতে তার বড় চাচার পরিবার আর তাদের ঘর সেটার সামনেরটা। রান্নাঘরের পাশেরটায় থাকে ছোট চাচা। ধান কাটার পর বাড়িতে কাজের ধুম পড়ে যেত। সেদ্ধ শুকনো করতে করতে কখন বেলা গড়িয়ে যেত, বাড়ির বৌ-ঝিদের খেয়াল থাকত না। পাঁচিলের বাইরের উঠোনে চলত মাড়াই। ফিরোজা তার ভাইদের সঙ্গে উঠে বসে থাকত আতাগাছটায়।
কিষেণ লম্বা লাঠিটা দিয়ে গরুর পেটে গুঁতো দিয়ে দিয়ে খুঁটির চারদিকে ঘোরাত অনবরত। কবেকার সব কথা, তারপর তার একদিন বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হলো তাদের গ্রাম থেকে একটু দূরে গঞ্জমতো জায়গায়। সিরাজুলদের সেখানে কাপড়ের ব্যবসা। বাড়িও সেই দোকানের পেছন দিকে। একটা ছোট্ট আমবাগান আড়াল করে আছে বাড়িটাকে মূল বাজার থেকে। কিছু জমি-জায়গা আছে একটু দূরে। তাও খুব বেশি দূর না, মাইল দুয়েক হবে। বিয়ের ঘটনা মনে হয় এই তো সেদিন। তার গায়ে হলুদ হলো, দুদিন পর বিয়ে। বিয়ের আগের দিনের ছোট্ট একটা ঘটনা, অথচ কেমন করে যেন আজও মনে আছে। বাড়িতে তখন আত্মীয়স্বজন ভরা। সে তারই ফাঁকে বাড়ির পেছন দিকের বাগান পার হয়ে লক্ষ্মী পিসিদের বাড়ি গিয়ে হাজির হয়েছে। পিসি তাকে দেখে তো চোখ ছানাবড়া, ‘এই, তোর না কাল বিয়ে, আর তুই ভরদুপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিস!’ ফিরোজা নিশ্চিন্তে গিয়ে দাওয়ায় বসে, বলে, ‘তোমার কুলের আচার খাওনোর কথা না, কাল বিয়ে হলে খাব কখন?’ ‘দেখেছো পাগলির কাণ্ড! হ্যাঁরে বিয়ে হলে তোর পিসি কি পালিয়ে যাবে।’ তারপর নিজে গিয়ে ঘরের ভেতর থেকে আচার এনে ফিরোজাকে দিয়ে বলে, ‘নে খা। বিয়ে হয়ে গেলে আমি মানুকে দিয়ে তোর বরের দোকানে এক বয়েম আচার পাঠিয়ে দেবখন।’
একটু থেমে আবার বলে, ‘এমন ভাব যেন তোর সাথে আর আমার দেখা হবে না।’ তাই তো হলো, কোথায় রইল লক্ষ্মী পিসি। আর কি কোনো দিন দেখা হবে? কে জানে? যেদিন সিরাজুলের দোকান পোড়াল, সেদিনই তার শ্বশুরবাড়ির সবাই চলে এলো ফিরোজাদের গ্রামে। সিরাজুলের বাজারের বন্ধু নিশিকান্ত, প্রসাদরা মিলে তাদের পৌঁছে দিয়ে গেল। সিরাজুলকে বলে গেল, ‘কটা দিন এখানে থাক, তোদের ঘরবাড়ি আমরা পাহারা দিয়ে রাখব।’ তো রেখেছিল পাহারা দিয়ে। মাঝে সিরাজুলদের পাশের বাড়ির রমাকান্ত কাকা এসে দেখা করে গেছে। সিরাজুলের মাকে বলে গেছে, ‘বৌদি আপনি চিন্তা করবেন না। সিরাজুলের বাপ মরার সময় আমাকে বলে গিয়েছিল, ওদের একটু দেখিস। আমি সে কথা ভুলিনি বৌদি। আমার সাধ্যমতো আমি চেষ্টা করব।’ সবাই ভেবেছিল, গণ্ডগোল একটু কমে গেলে আবার আগের মতো হয়ে যাবে। কিন্তু দিন দিন গোলমাল বাড়াতেই লাগল। ফিরোজা ভেবেই পায় না, কার সঙ্গে কার গোলমাল। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের? কই তাদের গ্রামের সনাতন কাকা, সিরাজুলের বন্ধু নিশিকান্ত, কাউকে তো কোনো দিন পর মনে হয়নি। লক্ষ্মী পিসি তো তার বাপজানকে কোনো দিন দাদা ছাড়া কিছু বলেনি। তাহলে এ কিসের ঝগড়া! কিসের মারামারি! ফিরোজা জানে না, কার ইশারায় এসব কাণ্ড ঘটে।
ফিরোজা এও জানে না, তার মতো কোনো এক দুর্গা কি পার্বতী বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে একই উত্তর খুঁজে বেড়াচ্ছে সীমান্তের ওপারে। যদিও ফিরোজাদের গ্রামে কোনো সমস্যা নেই, তবু চারদিকের খবর শুনে বুক কেঁপে ওঠে ওদের। দলে দলে লোক তাদের গ্রামের ওপর দিয়ে বোঁচকা-বুচকি নিয়ে চলে যাচ্ছে। চলে যাচ্ছে সীমান্তের দিকে। এই স্রোত একসময় তাদেরও নাড়া দেয়। বুঝি এটাই ঠিক, ‘হেথা নয়, হেথা নয় অন্য কোনখানে…।’ প্রথমে তা গুঞ্জনের মধ্যেই ছিল। একদিন সিরাজুলের এক মামা এসে উসকে দিয়ে গেল। ভয়ংকর সব মুসলমান নিধনের গল্প বলে বললেন, ‘এখানে থাকা মোটেও নিরাপদ না। মুসলমানদের জন্য তো তৈরিই হয়েছে পাকিস্তান।’ সিরাজুলদের জমিজমার ভার রমাকান্ত কাকাকে দিয়ে প্রথমে তারাই পাড়ি জমাল। বিক্রি হলে পরে এসে সিরাজুল টাকা নিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে ফিরোজাকেও আসতে হলো। ফিরোজার বাবারা কিছুদিন পর যশোরের এক হিন্দু পরিবারের সঙ্গে বিনিময় করে চলে এলো পাকিস্তানে। সনাতন কাকা, হরি মণ্ডল কত বোঝাল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। মহিম ঠাকুরদা লাঠি ঠুকঠুক করে এসে ফিরোজার বাপকে ডাকে, ‘হ্যাঁরে হামিদ বাপের ভিটে ছেড়ে চললি কী মনে করে? ভয় পাচ্ছিস, আমরা কি মরে গেছি? আমাকে না মেরে তোর কাছে পৌঁছুক দেখি।’
হামিদ মোড়ল মুখ নিচু করে ফেলে, বলে, ‘না গো কাকা বুকের মধ্যে ভয় অনবরত খামচি মারলে থাকি কী করে।’ আসার দিন ফিরোজা গিয়েছিল লক্ষ্মী পিসির সঙ্গে দেখা করতে। কোনো কথা বলতে পারেনি, আঁচলে মুখ চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। পথে যতবার সেই দৃশ্য মনে পড়েছে, ততবারই ফিরোজার চোখ ভিজে উঠেছে। সিরাজুল তাকে সান্ত্বনা দিয়েছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। এমন আতঙ্ক ভরা জীবনের অবসান অপেক্ষা করছে সীমান্তের ওপারে। শান্তির নিশ্চিন্ত নিবাস হবে তাঁদের। ফিরোজার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। খালি থালায় এঁটো আঙুল দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে ভাবছিল এসব। সিরাজুল হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ‘ওরাও বলে তোরা এখানকার না, যা; এরাও বলে উড়ে এসে জুড়ে বসেছিস।’ মুখ তুলে স্বামীর মুখের দিকে তাকায় ফিরোজা। তারপর জিজ্ঞেস করে ‘কোথায় যাবো তাহলে?’ সিরাজুল একটুখানি মুখ তুলে চকিতে ফিরোজার মুখের দিকে তাকায়। তারপর মাথা নামিয়ে মাছের ছোট্ট একটা কাঁটা বের করায় মনোযোগ দেয়। ফিরোজা তাকিয়ে থাকে, কিন্তু কোনো উত্তর আসে না। একসময় খাওয়া শেষ হলে নীরবে উঠে যায় সিরাজুল। সব গোছগাছ করে ঘরে আসে ফিরোজা, তারপরও কোনো উত্তর পায় না।
এক এক করে সব বাতি নিভে আসে, তখনো কোনো উত্তর পায় না। একসময় ঝিঁঝিঁ পোকারা ডাকতে থাকে তীব্র স্বরে। তখনো হয়তো উত্তর আসে না, কেননা তাদের আওয়াজে শোনা যায় না কিছুই।





















 সাজ্জাদ কবীর
সাজ্জাদ কবীর














