গণমাধ্যম ভাবনা
চতুর্থ স্তম্ভে সংকট
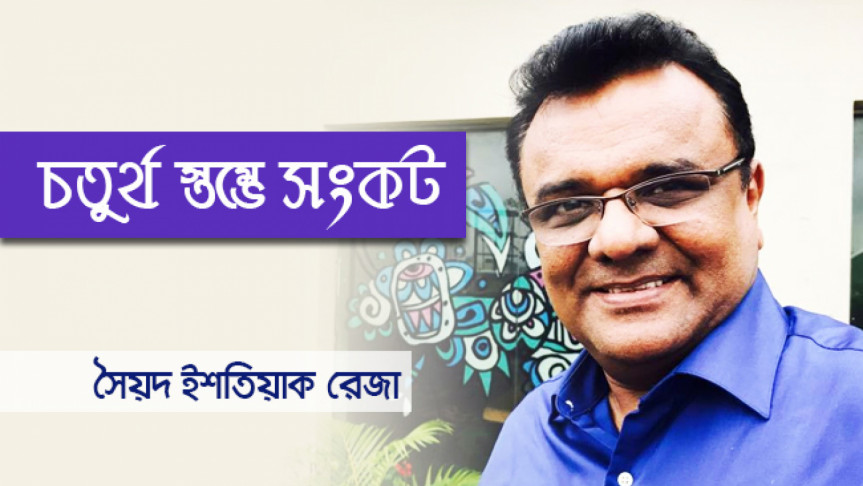
প্রতিটি সমাজেই গণমাধ্যমের বড় ভূমিকা আছে। আধুনিক সমাজ নিজেকে দেখে মিডিয়ার মাধ্যমে। আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে তার গুরুত্ব আমরা অনুধাবন হয়তো করি না সেভাবে। কিন্তু একটা সকাল কি ভাবা যায় পত্রিকা ছাড়া, একটি দিন কি কল্পনায় আসে গণমাধ্যম ছাড়া?
তথ্য, শিক্ষা আর বিনোদনের বাইরেও একটি আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট তৈরিতে ভূমিকা থাকে গণমাধ্যমের। আবার মিডিয়া প্রচারণা যন্ত্রও। কে কীভাবে একে ব্যবহার করে, তার ওপর নির্ভর করে কোন গণমাধ্যমের চরিত্র কী। গত ১৫ বছরের বেশি সময়ে বাংলাদেশের গণমাধ্যমের জমিনে বড় পরিবর্তন এসেছে। এখন দেশে প্রচুর টেলিভিশন চ্যানেল আর রেডিও স্টেশন সক্রিয়। সংবাদ আর অনুষ্ঠানে ঠাসা এগুলোর ফিক্সড পয়েন্ট চার্ট। তবে এসব মাধ্যমের অনুমোদনের ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক বিবেচনা। যারা লাইসেন্স পেয়েছে, তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ই অনুমোদন পেতে একমাত্র উপদান হিসেবে কাজ করেছে।
গণমাধ্যম পেশাজীবীদের জন্য মালিকদের এই পরিচয় বড় বাস্তবতা। সংঘাতময় জটিল রাজনৈতিক সংস্কৃতি, সহিংসতা, দারিদ্র্যসহ নানা সামাজিক সমস্যার ভেতরে কাজ করতে হয় বাংলাদেশের গণমাধ্যমকর্মীদের। তবে তাঁদের জন্য সবচেয়ে বড় বাস্তবতা হলো রাজনৈতিক কারণে সাংবাদিক ইউনিয়ন তথা পুরো সাংবাদিক সমাজের বিভাজন। মানুষের কাছে গণমাধ্যম এখনো অন্যায় আর অনিয়মের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সর্বশেষ ভরসা। আবার চাঞ্চল্যকর হলুদ সাংবাদিকতা, পক্ষপাতদুষ্ট সাংবাদিকতার অভিযোগও অনেক। গণমাধ্যমকর্মীদের মেনেও নিতে হয় এমন অনেক অভিযোগ। আসলে বাস্তবতা এই যে খারাপ সাংবাদিকতা যেমন আছে, তেমনি ভালো সাংবাদিকতার জন্য নিরন্তর সংগ্রামেও লিপ্ত গণমাধ্যমকর্মীরা।
সংকট যদি আমরা ভাবি তবে দেখব, প্রথম সংকট কনটেন্ট বা আধেয় তথা তথ্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ কার বেশি—সাংবাদিকদের নাকি মালিকদের? অবশ্যই মালিকদের। ষাটের দশকে রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যেমন গণমাধ্যম প্রকাশের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন, তেমনি এসেছিলেন কিছু আলোকিত পরিবারও। তাঁরা গণমাধ্যমকে দেখেছেন সমাজের জন্য ভালো কিছু করার প্রত্যয় হিসেবে। সাম্প্রতিককালে গণমাধ্যমে বড় পুঁজির প্রবেশ ঘটেছে। এই পুঁজি এসেছে যেমনি রাজনীতির আহরণ সংস্কৃতি (রেন্ট সিকিং কালচার) থেকে, তেমনি এসেছে জলাভূমি, বনভূমি দখলদার সংস্কৃতি থেকেও। বড় পুঁজি, তাই কোনো কোনো মাধ্যমে সাংবাদিকদের বেতন ও সুবিধাদি ব্যক্তি খাতের অন্যান্য লাভজনক খাতের সঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক। নতুন গণমাধ্যম মালিকানার কাছে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার চেয়ে ক্ষমতা আর প্রভাবের গুরুত্ব অনেক বেশি। তার সম্পদের পাহারা দিতে গণমাধ্যম বড় হাতিয়ার। তাই কোন তথ্য কেমন করে মানুষের কাছে যাবে, তা নির্ধারণে পেশাজীবীদের ভূমিকা ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে।
তাই সাংবাদিকদের সমাজের মাস্তানতন্ত্রকে যেমন বাইরে মোকাবিলা করতে হয়, করতে হয় পেশার ভেতরে ঢুকে যাওয়া কদর্য রাজনীতিকেও। গণমাধ্যম পেশাজীবীদের জন্য নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের ভেতরকার লড়াইটাও অনেক তীব্র।
সুস্থ সাংবাদিকতার প্রাণ হলো দেশের সুশাসন। বর্তমানে রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে যেভাবে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে, তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাংবাদিকতা।
রাজনৈতিক বিরুদ্ধাচরণ বা ভিন্নমতের কারণে নিষেধাজ্ঞা ও জবাই করার দৃষ্টান্তগুলো বহুচর্চিত হতে থাকলে তথ্যের অবাধ প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, মত প্রকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুঃখজনকভাবে অপছন্দের মতকে প্রকাশ্যে বা নেপথ্যে নিয়ন্ত্রণ ও নিষিদ্ধ করার ঐতিহ্য আত্মস্থ করার দিকেই অগ্রসর হচ্ছে সমাজ। তাই একদিকে ভয়ের সংস্কৃতির বিকাশ যেমন ঘটছে, তেমনি নীতি-নৈতিকতাহীন সাংবাদিকতার বিকাশও ঘটছে।
কোনো কোনো গণমাধ্যমে যেমন বড় পুঁজির প্রবেশ ঘটেছে, তাদের অর্থ সংকট নেই। আবার টিকে থাকার জন্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ওপর নির্ভর হয়ে পড়ছে এই জগতের বড় একটি অংশ। বিজ্ঞাপনদাতারাও হয়ে উঠেছে কনটেন্ট কন্ট্রোলার। ক্ষমতার স্বার্থ স্বাধীনতাকে খর্ব করবেই। রাষ্ট্র এবং করপোরেটের চাপ, লেখক-শিল্পীদের কট্টর মতামত, পুলিশের অপব্যবহার, মিডিয়ার আপস—মত প্রকাশের স্বাধীনতার সামনে বিস্তর বাধা। গণতন্ত্রের পক্ষে এগুলো খুব বড় সমস্যা।
সময়টা এমন, সব দল ও মতের নেতারা ধর্মান্ধদের সামনে নতজানু হন। কোনো কোনো সময় তারা রাষ্ট্রের ক্ষমতাকেও সম্পাদক বা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। রাজনৈতিক নেতারা যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন, ক্ষমতায় বা ক্ষমতার বাইরে, বাকস্বাধীনতার টুঁটি টিপে ধরতে সব সময় সচেষ্ট। এ দেশের আইনে বড় বড় ব্যবসায়ীর গণমাধ্যম চালানোয় কোনো বাধা নেই। এর ফলে ধরা যাক, কোনো একটি মাধ্যমে কোনো নেতা বা দলের বিরুদ্ধে কিছু একটা তথ্য গিয়েছে, তা হলে এমনটা সম্ভব যে সেই মালিক ব্যবসায়ীর পেছনে রাষ্ট্রীয় সংস্থা লাগিয়ে দেওয়া হলো। এ ধরনের কাজ মত প্রকাশের স্বাধীনতার খর্ব করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেয়।
বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন ছাড়া মুক্ত ও স্বাধীন গণমাধ্যম চালানো দুঃসাধ্য। রাষ্ট্র এবং রাজনৈতিক দলগুলো সাংবাদিকদের ওপর বলপ্রয়োগ করতে পারে, তাদের দমন করতে পারে অথবা নানাভাবে তাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং করেও। বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন বেসরকারি ব্যবসায়ীরাও। তাই গণমাধ্যমগুলোর বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বিপদ তৈরি হয়। বহু বড় বাণিজ্যিক সংস্থা বিভিন্ন চ্যানেল বা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করেছে, যেখানে তাদের সমালোচনাসূচক কিছু প্রচারিত হয়েছে।
সময় হয়েছে ভাববার যে কেমন আইনি সুরক্ষা চায় বাংলাদেশের গণমাধ্যম। নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ করে নীতি-নৈতিকতার পথে চলার জন্য। তাই শিশু, নারী, ধর্ষণের খবর কীভাবে পরিবেশিত হবে, মানুষের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার ব্যাপারে সংবেদনশীল আচরণ কেমন হবে, ধর্মীয় তথ্যের সংবেদনশীলতাই বা কী হবে এগুলো নির্ধারিত হবে বার্তাকক্ষেই।
পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে লেখক-শিল্পীদের নানা সংগঠন আছে, যারা তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হলে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করে। এ দেশে তেমন সংহতির খুব অভাব। প্রেস কাউন্সিল বা সম্পাদক পরিষদের কোনো ক্ষমতাই নেই। ইউনিয়ন বিভক্ত থাকায় সাংবাদিকের মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিপন্ন বা আক্রান্ত হলে তাকেই আত্মরক্ষার উদ্যোগ নিতে হয়। গণমাধ্যমের অভ্যন্তরীণ সমস্যা আছে, সরকারের দিক থেকে আছে এবং আছে উগ্রবাদ ও ধর্মান্ধতাও। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের কথা বলে সাম্প্রদায়িক নানা ঘটনা ঘটানো হচ্ছে। কিন্তু ধর্মীয় স্পর্শকাতরতার জন্য সেখানে গণমাধ্যমগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না।
তবুও আশার জায়গা এই যে, বাংলাদেশের বৃহত্তর সমাজে সুস্থ গণমাধ্যম প্রত্যাশিত বিষয়। গণমাধ্যমকর্মীরা যেন পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে পারেন, তার জন্য সমাজের বহু মানুষের মাঝে প্রচেষ্টা আছে। তাই গণমাধ্যমের এক অংশ যেমন পুঁজি আর রাজনীতির সঙ্গে আপস করেছে, তেমনি আরেকটি অংশ প্রাতিষ্ঠানিকতা ও পেশাদারিত্বের জন্য লড়ছে। তারা জানে, বহুত্বের পথেই মুক্তি। আর যুগটা এমন যেমন যে তথ্য গোগন করে রাখাও সম্ভব নয়। অনলাইন আর সামাজিক মাধ্যমের কারণে তথ্যপ্রবাহের নতুন দিগন্ত আজ উন্মোচিত।
লেখক : পরিচালক বার্তা, একাত্তর টিভি।





















 সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা
সৈয়দ ইশতিয়াক রেজা

















