বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস
পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য
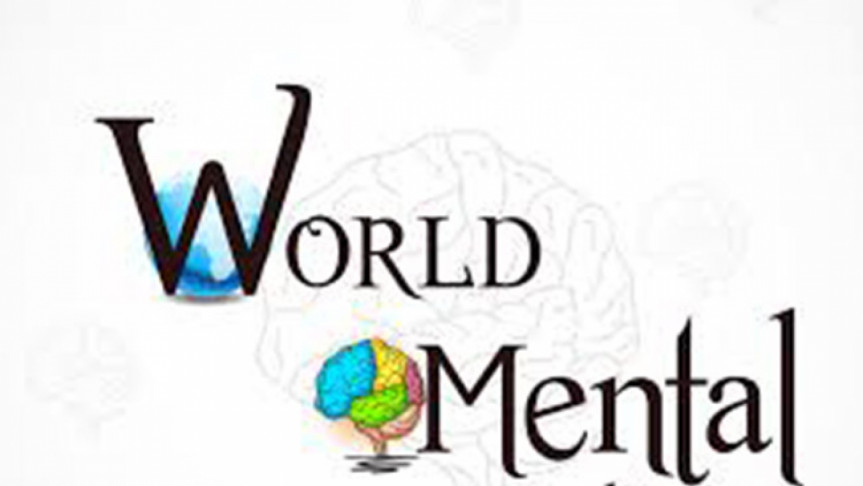
ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন ফর মেন্টাল হেলথ নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ১৯৪৮ সাল থেকে পৃথিবীজুড়ে মানসিক স্বাস্থ্যের মানোন্নয়নে, মানসিক রোগ প্রতিরোধে, চিকিৎসাসেবা জনগণের কাছে সহজলভ্য করতে এবং মানসিক রোগবিষয়ক কুসংস্কার ও বদ্ধমূল নেতিবাচক ধারণা দূরীকরণে কাজ করে যাচ্ছে। এটি পৃথিবীজুড়ে কাজ করা বহু দেশের বহু সংগঠন ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে কাজ করছে। এই উদ্দেশ্যগুলো সাধনে জনসচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এই সংগঠন ১৯৯২ সাল থেকে প্রতিবছর ১০ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালন করে আসছে।
প্রতিবছর এই দিবসের একটি করে প্রতিপাদ্য থাকে। সেই প্রতিপাদ্যের ওপর এই আন্তর্জাতিক সংস্থাটি প্রয়োজনীয় তথ্যের একটি প্যাকেজ পৃথিবীর বহু ভাষায় প্রকাশ করে থাকে। পৃথিবী জোড়া শত শত সংগঠন ও সরকার তখন সেই প্রতিপাদ্যের ওপর সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলাদেশে একদম প্রথম থেকেই, অর্থাৎ ১৯৯২ সাল থেকেই জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট সরকারি পর্যায়ে দিবসটি পালন করে আসছে। এই কর্মসূচির আরেক আয়োজক হচ্ছে ‘বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিস্টস’। এই সংগঠনটি জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যৌথভাবে এই দিবসটি উদযাপন করে আসছে। ১৯৯৮ সাল থেকে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস উযাপন করছে।
‘বাংলাদেশ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি সোসাইটি (বিসিপিএস)’ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সঙ্গে যৌথভাবে এই কর্মসূচি পালন করে থাকে। গত কয়েক বছর ধরে বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের কর্মসূচি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডুকেশনাল অ্যান্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগ, বাংলাদেশ মনোবিজ্ঞান সমিতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগসহ সারা দেশের বহুসংখ্যক সংগঠন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দিবসটি পালন করছে।
এই বছর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য হচ্ছে ‘পরিবর্তনশীল বিশ্বে তরুণদের মানসিক স্বাস্থ্য’। জীবনে সাফল্য অর্জন করতে গেলে, সুখী হতে গেলে অনেকগুলো জিনিস প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য। জাতিসংঘের মতে, ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সীরা হচ্ছেন তরুণ। তরুণদের জীবনে অনেকগুলো পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কৈশোরে তাদের দেহ-মন দ্রুত বাড়ে। হয় প্রচুর হরমোনঘটিত পরিবর্তন। তাদের বিকাশ অনেক সময় অসম হয়। তখন তাদের সেই পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হয়। তরুণরা অনেকেই লেখাপড়ার চাপে থাকেন। অনেকেরই আর্থিক অসংগতি থাকে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তরুণদের সঙ্গে তাঁদের অভিভাবকদের মতের অমিল হয়। তরুণরা দারুণভাবে অভিভাবকদের বিরোধিতা করেন। অভিভাবকরা অনেক সময় জোর-জবরদস্তির পথ বেছে নেন। এতে অশান্তি শুরু হয়।
তরুণরা লেখাপড়ার মধ্যে থাকেন। লেখাপড়া রীতিমতো চাপদায়ী পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে। এ ছাড়া স্কুল-কলেজে অনেক সময় শারীরিকভাবে একটু বেড়ে ওঠা তরুণরা তাদেরই কোন কোন সহাপাঠীকে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে হেনস্তা করে। যেসব কিশোর বা তরুণের শারীরিক গড়ন দুর্বল বা একটু অন্য রকম, যারা জাতিগত বা ধর্মীয়ভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের, তারা অনেক সময় এমন সব পরিস্থিতিতে পড়ে। এ ধরনের দুর্ব্যবহারকে বলে ‘বুলিং’। আধুনিককালে বুলিংও আধুনিক চেহারা নিয়েছে। এখন সামনাসামনি বুলিং ছাড়াও ‘সাইবার বুলিং’ চালু হয়েছে। এ ধরনের বুলিংয়ে কারো ই-মেইল, ফেসবুক, ভাইবার, ইমো ইত্যাদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোর সংকেতবাক্য হ্যাক করে তাকে ভয়-ভীতি দেখানো হয়। তাকে ব্ল্যাকমেইল করে তার থেকে টাকা-পয়সা ও অন্যায় সুবিধা আদায় করা হয়। তার সম্মান ধুলায় লুটিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এই ধরনের বুলিংয়ের ফলও খুব মারাত্মক হয়ে ওঠে। বুলিংয়ের শিকার তরুণদের লেখাপড়া ও সামাজিক খাপ খাওয়ানো মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। পরিণত বয়সেও এই প্রভাব অনেক সময় থেকে যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, যাঁরা বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন, তাঁদের শতকরা ৮৩ ভাগ বলেছেন যে বুলিং তাঁদের আত্মবিশ্বাসের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ১৮টি দেশের এক লাখ তরুণদের ওপর ইউনিসেফ পরিচালিত এক জরিপে দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে যাঁরা বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা পঁচিশ ভাগ তাঁদের শারীরিক গড়নের কারণে, শতকরা পঁচিশ ভাগ তাঁদের লিঙ্গগত পরিচিতির বা যৌন পরিচিতির কারণে এবং শতকরা পঁচিশ ভাগ তাঁদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বা জাতিগত পরিচিতর কারণে বুলিংয়ের শিকার হয়েছেন ।
কৈশোরের একটি পর্যায়ে তরুণরা নিজেদের যৌন পরিচিতি বিষয়ে নিশ্চিত হন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি ও মেয়েরা ছেলেদের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করেন। সমাজে এ ধরনের অনুভূতি ব্যাপকভাবে বিদ্যমান। এভাবে অনুভব করাকে সমাজ সুস্থতা হিসেবেই বিবেচনা করে। কিন্তু মুশকিল হয় যখন এর অন্যথা হয়। কিছু তরুণদের মধ্যে ব্যতিক্রমী কিছু বিষয় খেয়াল করা যায়। কোনো কোনো তরুণ অনুভব করেন যে তাঁদের লৈঙ্গিক (শারীরিক) বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাঁরা সুখী নন। তাঁরা নিজেদের অন্য লিঙ্গের ভাবতে পছন্দ করেন। মনের মধ্যেও এমনটা অনুভব করেন। এতে সমাজে খাপ খাওয়াতে গিয়ে গুরুতর সমস্যায় পড়েন।
এ ছাড়া কিছু ব্যতিক্রমী তরুণ ভিন্ন লিঙ্গের পোশাক পরতে ও তাঁদের মতো কথা বলতে, চলতে পছন্দ করেন। যেমন, ছেলেরা মেয়েদের পোশাক পরতে, সাজতে ও সেভাবে চলতে পছন্দ করেন। মেয়েরা আবার তেমনি ছেলেদের মতো চলতে পছন্দ করেন। উল্লেখ্য, শুধু পোশাক পরাই নয়। এই মেয়েরা নিজেদের ছেলে ভাবতে পছন্দ করেন। কেউ কেউ এমনও বলেন, তিনি ভুলক্রমে একটি মেয়ের দেহ পেয়ে গেছেন। ব্যতিক্রমী ধরনের তরুণদের কেউ কেউ এমনকি অপারেশন করে লিঙ্গ পরিবর্তন করে ফেলতে আগ্রহী থাকেন। ব্যতিক্রমী তরুণদের মধ্যে অনেকেই সমলিঙ্গের, অর্থাৎ ছেলেরা ছেলেদের প্রতি ও মেয়েরা মেয়েদের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোধ করেন। অনেকে এভাবে যৌন ক্রিয়াতেও অভ্যস্ত থাকেন। সমাজ এ ধরনের ব্যতিক্রমগুলোকে মোটেই সহজভাবে নিতে পারে না। ধর্মীয় ও সামাজিক আদর্শের কারণে বহু মানুষ এঁদের প্রতি মারাত্মকভাবে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখান। এতে এ ধরনের মানুষগুলোর মনের মধ্যে মারাত্মক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া পড়ে। এঁদের অনেকে নিজেকে নিজে মানতে পারেন না। অর্থাৎ নিজের আচরণ ও অনুভূতি নিয়ে লজ্জিত থাকেন। কিন্তু বদলাতেও পারেন না। এঁরা অনেকেই বুলিংয়ের শিকার হন। ১২ থেকে ২৪ বছর বয়সী এ ধরনের মানুষগুলোর শতকরা ৫১ ভাগ আত্মহননের কথা বিবেচনা করেন। এঁদের শতকরা ৩০ ভাগ জীবনের কখনো না কখনো অন্তত একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।
পৃথিবীব্যাপী চলছে হিংসা হানাহানি, যুদ্ধ, সংঘাত। চলছে ধর্মীয় ও জাতিগত সহিংসতা। রয়েছে সড়ক ও অন্যান্য ধরনের দুর্ঘটনা। রয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, খড়া, বন্যা, নদীভাঙন। এগুলো তরুণদের বিশেষত কিশোর-কিশোরীদের ভয়ানকভাবে প্রভাবিত করে। সবচেয়ে দুর্বলের কপালে রয়েছে সবচেয়ে খারাপ ধরনের দুর্ভোগ। যখন যুদ্ধ ও সহিংসতা হয়, যখন মানুষের মানবিকতা হারিয়ে যায়, তখন সবচেয়ে বেশি মৃত্যুবরণ করেন, সবচেয়ে বেশি আহত হন, সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন এমন জনগণ যাঁরা রাজনৈতিক হানাহানির সক্রিয় অংশগ্রহণকারী নন। অল্পবয়সী মেয়েরা শিকার হন শারীরিক, মানসিক ও যৌন নিপীড়নের। পৃথিবীতে প্রতি ১০ মিনিটে একজন কিশোরী সহিংসতার কারণে মৃত্যুবরণ করেন। যুদ্ধের কারণে যখন মানুষ শরণার্থী হন, তখন তাঁদের নিরাপত্তাবলয় যায় ভেঙে। নিজস্ব ঘরবাড়ি নেই। নেই পরিচিত সমাজ, পরিচিত প্রতিবেশী। বংশপরম্পরায় বাস করা গ্রাম বা শহর থেকে নির্বাসিত। আশপাশের মানুষগুলো প্রায়ই বৈরী থাকে। অনেক সময় শিশু-কিশোররা বাবা-মায়ের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। শিক্ষিত মানুষগুলো তাঁদের শিক্ষা অনুযায়ী কোনো কাজ পান না। কষ্টকর শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করতে হয়। অনেক সময় পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় অনুদানের, আন্তর্জাতিক সাহায্যের ওপর। সেটিও যেকোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তরুণীরা অনেক সময় যৌন কর্মী হিসেবে কাজ করতে বাধ্য হন। অর্থ নেই, খাদ্য নেই—খুবই অসহায় অবস্থা। এই ট্রমাগুলোর কারণে তরুণরা মানসিক চাপগ্রস্ত হন। অনেকে মানসিক রোগে আক্রান্ত হতে পারেন। তীব্র ট্রমার কারণে অনেক ধরনের মানসিক রোগের পাশাপাশি ‘পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিজঅর্ডার’ নামের দীর্ঘমেয়াদি কষ্টদায়ী মানসিক রোগ হতে দেখা যায়। অল্প বয়সেই মানসিক রোগের প্রকোপ বেশি। প্রতি পাঁচজন তরুণের মধ্যে কোনো না কোনো সময় অন্তত একজনের মানসিক রোগ হতে দেখা যায়। গুরুতর মানসিক রোগের মধ্যে ‘মেজর ডিপ্রেশন’, ‘বাইপোলার মুড ডিজঅর্ডার’ এবং ‘সিজোফ্রেনিয়া’ উল্লেখযোগ্য। তরুণদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা ব্যাপক। যাদের বয়স ১৫-২৯ বছর, তাদের মৃত্যুর দ্বিতীয় মুখ্য কারণ হলো আত্মহত্যা। আত্মহত্যার উপায়গুলোর মধ্যে রয়েছে কীটনাশক বা বিষপান, ফাঁসি নেওয়া ইত্যাদি।
মানসিক রোগ যে নো দেশের জন্যই একটি বড় সমস্যা। দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে, স্বাস্থ্য বাজেটের শতরা চার ভাগও মানসিক রোগের স্বাস্থ্যসেবায় ব্যয় হয় না। তবে এটি হলো আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যান। বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য খাতে এ ধরনের ব্যয় আরো অনেক কম হওয়ার আশঙ্কাই বেশি।
তরুণরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তাঁরা কঠিন সময় পার করছেন। আমাদের করার রয়েছে অনেক কিছু। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বুলিংমুক্ত করার কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। শিক্ষক, অভিভাবক ও জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। সচেতন হতে হবে। মানুষের মধ্যে সহনশীলতা বাড়াতে হবে। যারা আমাদের মতো নয়, যারা ব্যতিক্রমী, তাদের আমাদের অনেকের কাছে অস্বস্তিকর লাগলেও তাদের নিয়ে আমরা কী করতে পারি, তা ভাবতে হবে। খুব বেশি নির্দয় হয়ে ওঠার কোনো মানে হয় না। মনে রাখতে হবে, পৃথিবীর ওপর আমাদের প্রত্যেকের সমান অধিকার রয়েছে। তাহলে তাঁরাও জীবনের সঙ্গে ভালোভাবে খাপ খাওয়াতে পারবেন। দেশে দেশে হিংসা-হানাহানি, যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করতে হবে, যাতে কারো জীবন ধ্বংস না হয়। কারো মধ্যে আত্মহত্যা প্রবণতা দেখা গেলে, কেউ নিজের ক্ষতি নিজে করতে শুরু করলে, কেউ মানসিক চাপগ্রস্ত হলে, কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে দ্রুত চিকিৎসার আওতায় আনতে হবে। এ জন্য সচেতনতার কোনো বিকল্প নেই। এমনভাবে মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে, যাতে তাঁরা নিজেরা মানসিক রোগ প্রাথমিক পর্যায়েই বুঝত পারেন। এমনটা হলে কী করতে হবে, সে বিষয়েও মানুষকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। পরিবারের কী দায়িত্ব হবে, বন্ধুজনের কী দায়িত্ব, সমাজেরই বা কী দায়িত্ব হবে, সেসব বিষয়ে মানুষকে জানাতে হবে। এরপর অসুবিধা বেশি হলে দ্রুত চিকিৎসার আওতায় আসতে হবে। এভাবেই একদিন হয়তো আমরা সবাই পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে শিখব, পরস্পর পরস্পরের অস্তিত্বকে মেনে নিতে শিখব এবং এভাবেই সবাই মিলে সুখী-সমৃদ্ধ আগামী গড়ব।
লেখক : ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ও সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট।





















 মো. জহির উদ্দিন
মো. জহির উদ্দিন

















